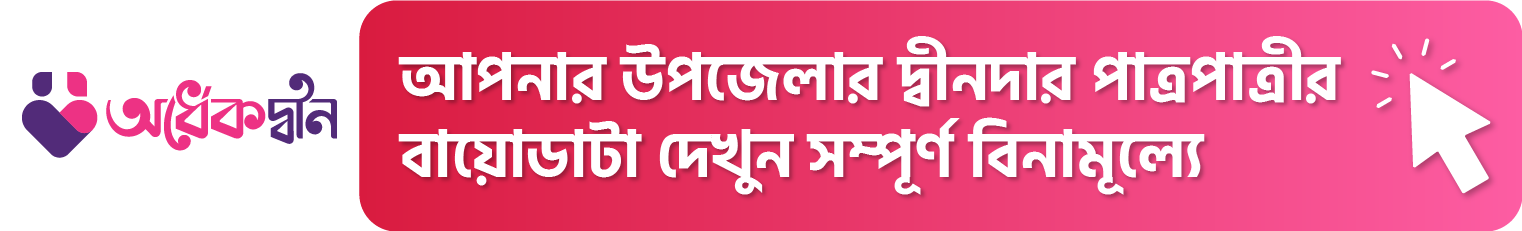মুফতী ইজহারুল ইসলাম কাউসারী
-আপনি নাকি ভাই হাল্লাজিস্ট? ইবনে মনসুর হাল্লাজকে ডিফেন্ড করেন?
– মৃত ব্যক্তির বিচারের দায়িত্ব তো আমার নয়। আল্লাহ তায়ালা বিচার করবেন। এজন্য মৃত ব্যক্তির নিয়ে ডিফেন্ড করার কিছু আছে বলে মনে করি না। এজন্য কারও ব্যক্তি কেন্দ্রিক আলোচনা আমি পছন্দ করি না। তবে ব্যক্তির সাথে যদি কোন মতবাদ যুক্ত থাকে, তাহলে সেই মতবাদের আলোচনা হতে পারে। আমি ব্যক্তিগতভাবে দু’টি কারণে তার পক্ষে বলেছি,
১। অনেক আলিম যেমন তার বিপক্ষে ছিল, আবার অনেকে তার পক্ষেও ছিল। আমাদের আকাবিরদের মধ্যে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ ও হযরত মাওলানা জাফর আহমাদ উসমানী রহ: তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলোর জবাব দিয়েছেন। তাদের জবাবগুলো আমার কাছে শক্তিশালী মনে হয়েছে। যারা বিপক্ষে তাদের দলিলের চেয়ে পক্ষের দলিলগুলো শক্তিশালী হওয়ার কারণে এমতটি গ্রহণ করেছি।
আহলে হাদীসের মান্যবর অনেক আলিমও তার পক্ষে কথা বলেছেন।
২। কাউকে কাফের বা মুরতাদ বলার জন্য অকাট্য দলিল প্রয়োজন। ইবনে মানসুর হাল্লাজকে কাফির বলার কোন অকাট্য দলিল পাইনি।
– তার বিরুদ্ধে তো আলিমদের কুফুরীর ফতোয়া আছে?
– কারও বিরুদ্ধে কুফুরীর ফতোয়া থাকলেই সে কাফের হয় না। ইবনে তাইমিয়া রহ: কে বিখ্যাত আলিম আলা আল-বোখারী রহ: কাফের ফতোয়া দিয়েছিলেন। এমনকি তিনি বলেছিলেন, কেউ যদি তাকে শাইখুল ইসলাম বলে সেও কাফের। আলিমগণ তার এই ফতোয়া পরবর্তীতে গ্রহণ করেননি। ইবনে হাজার আসকালানী রহ: সহ বহু আলিম এর প্রতিবাদ করেন।
– ইবনে মনসুরের হত্যার বিষয়ে তো আলিমদের ঐকমত্য হয়েছিল?
– আশরাফ আলী থানবী রহ: ও জফর আহমাদ উসমানী রহ: বলেছেন, তার হত্যাকান্ড ছিল রাজনৈতিক। সে সময়ের কাজী জোরপূর্বক আলিমদের কাছ থেকে ফতোয়া গ্রহণ করে তাকে হত্যা করে। কাজীর সাথে তার মনমালিন্যের কারণে এমনটি করেছিলেন। এর স্বপক্ষে তারা ঐতিহাসিক প্রমাণও দিয়েছেন। থানবী রহ: এর কিতাবটি বাংলায় বেরিয়েছে। আপনি দেখে নিতে পারেন।
– ইবনে তাইমিয়া রহ: সহ অনেক আলিম তো তাকে কাফির বলেন?
– তাদের কাফের বলার মূল কারণ হল, তারা মনে করতেন, ইবনে মনসুর হাল্লাজ হুলুল ও ইত্তিহাদের আকিদা রাখত। তারা মূলত: এই আকিদার কারণে কাফের বলেছে।
– একই কারণে আপনিও কাফের বলুন।
– না। কারণ হুলুল ও ইত্তিহাদের বিপক্ষে তার স্পষ্ট বক্তব্য আছে। যেমন তিনি বলেছেন,
“আল্লাহ তায়ালা ক্বাদীম বা অনাদির গুণের মাধ্যমে সমস্ত সৃষ্টি থেকে পৃথক হয়েছেন, তেমনি সমস্ত সৃষ্টি নশ্বর গুণের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা থেকে পৃথক হয়েছে ”
এখানে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা মাখলুকের সাথে ইত্তেহাদ বা একীভূত নন, তেমনি তিনি সৃষ্টির মাঝেও প্রবেশ করেন না। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা হুলুল ও ইত্তেহাদ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।
এরপর মনসুর হাল্লাজ বলেন, ” আল্লাহর পরিচয় লাভ করা হলো তাউহীদ। আর আল্লাহর তাউহীদ হলো আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টি থেকে পৃথক বিশ্বাস করা। ”
– তাহলে কি হুলুল ও ইত্তিহাদে অভিযোগ সঠিক নয়?
– আমি মনে করি, না। এছাড়া হুলুল ও ইত্তিহাদের অভিযোগ অনেকের বিরুদ্ধেই করা যায়। যারা আল্লাহ তায়ালাকে কোন দিকে বিশ্বাস করে, তারাও হুলুলের আকিদা রাখে। যারা আল্লাহকে কোন স্থানে বিশ্বাস করে, তারাও হুলুলের আকিদা রাখে। এই অভিযোগের কারণে তাদের ব্যাপারেও কুফুরীর ফতোয়া দেয়া যায়। নিজেদের আকিদা বিশ্বাসে হুলুলে ভরা, আরেকজনকে অভিযুক্ত করার আগে তাদের আকিদার সংশোধনীও জরুরি।
– ইবনে মানসুর যে আনাল হক্ব বলত?
– আনাল হক, আমার জামার নীচে আল্লাহ ছাড়া কিছুই নেই, শুধু এজাতীয় কথার কারণে কাউকে কাফির মুশরিক বলা যায় না। তার উদ্দেশ্য, নিয়ত, অবস্থা ইত্যাদি যাচাইয়ের পরে তাকে কাফির বা মুশরিক বলা যেতে পারে। আবু ইয়াজীদ বোস্তামী রহ: থেকে এধরণের কথা বর্ণিত আছে। তাকে তো আপনারা কাফির বলেন না। আর ইবনে তাইমিয়া রহ: ফানা এর আলোচনায় বলেছেন, অনেকের থেকে অস্বাভাবিক অবস্থায় এধরণের কথা প্রকাশিত হয়েছে। এজাতীয় অস্বাভাবিক কথার কারণে তিনি কাফির বা মুশরিক বলেননি।
– আপনি নাকি ফানার বিষয়ে ইবনে তাইমিয়া রহ: এর নামে মিথ্যা বলেছেন?
– নাউযুবিল্লাহ। আমি ইবনে তাইমিয়া রহ: এর আরবী পড়ে পড়ে শুনিয়েছি। তবে মাঝে মাঝে নিজেদের থেকে দু’একটি উদাহরণ দিয়েছি বোঝার সুবিধার জন্য। ইবনে তাইমিয়া রহ: যেখানে বলেছেন, সুফীদের কেউ কেউ ফানার কারণে আনাল হক বলেছে। আমি আরবীটা পড়েছি। উদাহরণ হিসেবে নিজের থেকে বলেছি, যেমন মনসুর হাল্লাজ। কিছু লোক মনে করেছে, আমি মনসুর হাল্লাজের কথা ইবনে তাইমিয়া রহ: এর কিতাব থেকে বলছি। অথচ আরবীতে তো আমি এধরণের কোন শব্দ কিতাব থেকে পড়িনি। মিথ্যা তো তখন হতো, যখন আমি আরবীতে ইবনে তাইমিয়া রহ: এর বক্তব্য কম-বেশ করতাম। আরবী অনুবাদের সাথে ব্যাখ্যা বা উদাহরণ দেয়ার অধিকার সবারই আছে। সেটা আপনারা ভুল বুঝেছেন। আর ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজেও বহু আগে থেকেই জানতাম যে, ইবনে তাইমিয়া রহ ও ইবনে কাসির রহ: মনসুর হাল্লাজকে যিন্দিক মনে করতেন। আর ওই ভিডিওর আগে এসব বিষয়ে আমি নোটও লিখেছি। সুতরাং নিজেদের ভুল বুঝকে আমার নামে চালিয়ে দেয়াটা আপনাদের অন্যায়। বাকী ফানা ফিল্লাহ বিষয়ে ইবনে তাইমিয়া রহ: ও ইবনুল কাইয়্যিম রহ: যা কিছু বলেছেন, সেটা আমাদের সালাফী ভাইয়েরা হজম করতে পারে না। এজন্য তাদের এক শায়খ এ বিষয়ক আলোচনায় বেশ কারচুপির আশ্রয় নিয়েছেন। পরবর্তীতে কোন এক ভিডিওতে এ বিষয়ে কথা বলব ইনশা আল্লাহ।
-মনসুর হাল্লাজের পক্ষে বলে আপনাদের লাভ কী?
– আমাদের কোন লাভ নেই। আমরা মূলত: হুলুল ও ইত্তিহাদের আকিদার বিরোধী। যারা মনসুর হাল্লাজের বিপক্ষে বলে, তারাও কিন্তু হুলুলের আকিদা রাখে। কেউ আল্লাহ আসমানে বিশ্বাস করে, কেউ আরশে, কেউ উপরের দিকে। এসব কিছুই হুলুল। হুলুলের কারণে যদি হাল্লাজের বিরুদ্ধে কথা ওঠে, তাহলে যারা এসব আকিদা রাখে, তাদের বিরুদ্ধেও আওয়াজ তোলা উচিৎ। দাঁড়িপাল্লা সবার জন্য সমান হোক। যারা এসব আকিদা রাখে তাদেরকে হাল্লাজিস্ট বলা অধিক যুক্তিযুক্ত আমি মনে করি।
প্রশ্ন: ইবনে তাইমিয়া রহ, ইবনে কাসীর রহ, ইবনে হাজার রহ: মনসুর হাল্লাজকে যিন্দিক মনে করার পরও আপনারা মনে করেন না কেন?
উত্তর:
সর্বপ্রথম আপনাকে বিরোধের বাস্তবতা বুঝতে হবে। ইবনে মনসুর হাল্লাজের কুফুরীর বিষয়টি ঐকমত্যপূর্ণ নয়। এটি সব যুগেই মতবিরোধপূর্ণ। বিষয়টি যে মতবিরোধপূর্ণ, এ বিষয়ে যারা তার বিরোধীতা করেছেন, তারাও স্বীকার করেছেন।
আর একটা বিষয় যখন মতবিরোধপূর্ণ হয়, তখন যার কাছে যে দিকটি শক্তিশালী মনে হবে, সে সেটি গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে কারও গবেষণা অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে না।
ইবনে মনুসর হাল্লাজের বিষয়টি মতবিরোধপূর্ণ হওয়ার কিছু দলিল।
১। খতীব বাগদাদী রহ: বলেন,
قال الخطيب البغدادي: والصوفية مختلفون فيه، فأكثرهم نفى أن يكون الحلاج منهم، وأبى أن يعده فيهم، وقبله من متقدميهم أبو العباس بن عطاء البغدادي، ومحمد بن خفيف الشيرازي، وإبراهيم بن محمد النصراباذي النيسابوري، وصححوا له حاله، ودونوا كلامه، حتى قال ابن خفيف: الحسين بن منصور عالم رباني.
وقال أبو عبد الرحمن السلمي – واسمه محمد بن الحسين – سمعت إبراهيم بن محمد النصراباذي وعوتب في شيء حكي عن الحلاج في الروح فقال للذي عاتبه: إن كان بعد النبيين والصديقين موحد فهو الحلاج.
قال أبو عبد الرحمن: وسمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت الشبلي يقول: كنت أنا والحسين بن منصور شيئا واحدا إلا أنه أظهر وكتمت.
وقد روي عن الشبلي من وجه آخر أنه قال، وقد رأى الحلاج مصلوبا: ألم أنهك عن العالمين؟
قال الخطيب: والذين نفوه من الصوفية نسبوه إلى الشعبذة في فعله، وإلى الزندقة في عقيدته وعقده.
অর্থ: সূফীগণ তার বিষয়ে মতবিরোধ করেছেন। অধিকাংশ সূফী মনে করেন, হাল্লাজ তাদের দলভুক্ত নয়। তারা তাকে সূফীদের মধ্যে গণ্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। আবার সূফীদের কেউ কেউ তাকে প্রথম সারির সূফী মনে করেন। যেমনটি মনে করতেন, আবুল আব্বাস ইবনে আতা আল-বাগদাদী। মুহাম্মাদ ইবনে খাফীফ আশ-শিরাজী, ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মাদ নাসরাবাজী নাইসাপুরী। তারা তার অবস্থানকে সঠিক মনে করতেন। তার বক্তব্যগুলো সংকলন করেছেন। এমনকি মুহাম্মাদ ইবনে খাফীফ বলেন, হাল্লাজ একজন বুজুর্গ আলিম।
আবু আব্দুর রহমান সুলামী (তার নাম মুহাম্মাদ ইবনে হুসাইন) বলেন,
ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মাদ নাসরাবাজী রুহ সম্পর্কে হাল্লাজ থেকে কিছু বিষয় বর্ণনা করেন। তখন জনৈক ব্যক্তি তাকে তিরষ্কার করে। তখন তিনি বলেন, নবী ও সিদ্দিকগণের পরে যদি কেউ একত্ববাদী হয়, তাহলে সে হল হাল্লাজ।
আবু আব্দুর রহমান সুলামী বলেন, আমি মানসুর বিন আব্দুল্লাহকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি শিবলী রহ: কে বলতে শুনেছি, আমি ও হুসাইন ইবনে মানসুর হাল্লাজ একই অবস্থার উপর ছিলাম। তবে সে প্রকাশ করেছে কিন্তু আমি গোপন করেছি।
শিবলী থেকে আরও বর্ণনা আছে, হাল্লাজকে শুলিতে দেখে তিনি বলেন, আমি কি মানুষকে জানাতে তোমাকে নিষেধ করিনি?
খতীব বলেন, সূফীদের যারা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, তারা তার কাজকর্মকে ভেল্কিবাজী ও তার আকিদা-বিশ্বাসকে ধর্মদ্রোহিতা মনে করেন।
(আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া)
এখানে খতীব বাগদাদী রহ: স্পষ্টভাষায় মতবিরোধের কথা তুলেছেন। এখানে তিনি যারা হাল্লাজের পক্ষ অবলম্বন করেছেন, তাদের কয়েকজনের নামও উল্লেখ করেছেন। তারা সকলেই মুহাদ্দিস ছিলেন। হাল্লাজের সম-সাময়িক ছিলেন। সিয়ারু আ’লামিন নুবালাতে তাদের বিস্তারিত জীবনী রয়েছে। আমরা পরবর্তী তাদের সম্পর্কেও আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।
খতীব রহ: এর বক্তব্য থেকে মতবিরোধের বিষয়টি স্পষ্ট।
২। ইবনে কাসীর রহ: বলেন,
لم يزل الناس منذ قتل الحلاج مختلفين في أمره
অর্থ: হাল্লাজের হত্যার পর থেকে এখনও পর্যন্ত মানুষ তার বিষয়ে মতবিরোধ করছে।
(আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া)
এরপর তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমদের মত এবং তার পক্ষের মত নিয়ে আলোচনা করেছেন।
ইবনে কাসীর রহ: এ বক্তব্য উল্লেখের মূল উদ্দেশ্য হল, বিষয়টির অবস্থান তুলে ধরা। হাল্লাজের হত্যার পর থেকেই তার বিষয়ে দু’টি মত চলে আসছে। ইবনে কাসীর রহ: তার বিপক্ষে হলেও মতবিরোধের কথা স্বীকার করেছেন।
৩। ইবনে হাজার আসকালানী রহ: ও মতবিরোধের বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন,
وأخبار الحلاج كثيرة والناس مختلفون فيه
অর্থ: হাল্লাজের বিষয়ে অনেক বর্ণনা রয়েছে। মানুষ তার সম্বন্ধে মতভেদ করেছে।
(লিজানুল মিজান)
ইবনে কাসীর ও ইবনে হাজার রহ: বলেন, অধিকাংশ আলিমের মতে সে জিন্দিক। কিন্তু তারা বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন যে, তার বিষয়ে মতবিরোধপূর্ণ অবস্থান রয়েছে আলিমগণের।
৪। ইমাম ইবনুল আসীর রহ: ও মতবিরোধের বিষয়টি উল্লেখ করে বলেছেন,
وبالجملة فإن الناس اختلفوا فيه اختلافهم في المسيح عليه السلام، فمن قائل إنه حل فيه جزء إلهي ويدعي فيه الربوبية، ومن قائل إنه ولي الله تعالى وأن الذي يظهر منه من جملة كرامات الصالحين، ومن قائل أنه ممخرق ومستغش وشاعر كذاب ومتكهن والجن تطيعه فتأتيه بالفاكهة بغير أوانها
]অর্থ: মোটকথা, মানুষ হাল্লাজের বিষয়ে মতবিরোধ করেছে। যেমন হযরত ইসা আ: এর বিষয়ে মানুষ মতবিরোধ করেছিল। কেউ বলে, তার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা অনুপ্রবেশ করেছে। এজন্য তারা তাকে খোদা মনে করত। কেউ বলে, তিনি একজন আল্লাহর ওলী। তার থেকে প্রকাশিত বিষয়গুলো অন্যান্য বুজুর্গের মত তার কারামত হিসেবে গণ্য হবে। কেউ বলে, সে উদভ্রান্ত ও বিকৃত মস্তিষ্কের। মিথ্যুক কবি। গণক। তার কাছে জ্বিন এসে ভিন্ন মৌসুমের ফল দিয়ে যেত।
(আল-কামিল)
ইবনুল আসির রহ: এর বক্তব্যের কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে মনে করি না। এজন্য যারা হাল্লাজের বিষয়ে আলোচনা করবেন, তাদেকে প্রথমে স্বীকার করতে হবে যে বিষয়টি আহলে সুন্নতের আলিমগণের মধ্যে মতবিরোধপূর্ণ। তার পক্ষে-বিপক্ষে বড় বড় আলিম রয়েছেন।
উদাহরণ হিসেবে আহলে সুন্নতের বিখ্যাত কিছু আলিমের নাম এখানে উল্লেখ করছি, যারা তার পক্ষে কথা বলেছেন অথবা কাফির বলেননি,
১। আবুল আব্বাস ইবনে আতা আল-বাগদাদী রহ:
২। মুহাম্মাদ ইবনে খাফীফ আশ-শিরাজী রহ:
৩। ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মাদ নাসরাবাজী নাইসাপুরী রহ:
৪। ইমাম কুশাইরী রহ:
৫। আবু নসর তুসী রহ:
৬। ইবনে আকীল হাম্বালী রহ:
৭। ইমাম গাজালী রহ:
৮। আব্দুল কাদির জিলানী রহ:
৯। আব্দুল ওহাব শা’রানী রহ
১০। কাজী শাওকানী রহ:
১১। নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান রহ
এক দিকে যেমন ইবনে তাইমিয়া রহ, ইবনে কাসীর রহ, ইবনে হাজার আসকালানী আছেন, অন্য দিকে ইমাম কুশাইরী, গাজালী, আব্দুল কাদির জিলানী, ইবনে আকীল, কাজী শাওকানী আছেন। সুতরাং প্রত্যেকের আলোচনার মধ্যে সতর্কতা কাম্য। কোন একদল আলিমের গবেষণাকে মূল ধরে অন্যদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে নিজের আমলনামা কাল না করি। মতবিরোধকে মতবিরোধের স্তরে রাখি।
প্রশ্ন: ইবনে মানসুর হাল্লাজকে কোন বড় আলিম কি সমর্থন করেছেন?
উত্তর:
আমরা পূর্বের আলোচনায় বিখ্যাত আলিমগণের নাম উল্লেখ করেছি। এছাড়াও আরও বহু আলিম আছেন, যারা তাকে কাফির বা যিন্দিক বলেননি। হুসাইন ইবনে মানসুর হাল্লাজকে তার সম-সাময়িক বড় বড় কয়েকজন মুহাদ্দিস সমর্থন করেছেন।
১। আবুল কাসিম নাসরাবাজী (মৃত:৩৬৭ হি:)
ইমাম জাহাবী রহ: তার সম্পর্কে বলেছেন,
الإمام المحدث القدوة الواعظ شيخ الصوفية
অর্থ: ইমাম, মুহাদ্দিস, আমাদের আদর্শ, বক্তা, সূফীগণের শায়খ।
ইমাম হাকিম, আবু আব্দুর রহমান সুলামী, আবুল আ’লা ওয়াসেতি, আবু আলী দাক্কাক প্রমুখ মুহাদ্দিস তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।
তিনি হুসাইন ইবনে মানসুর হাল্লাজ সম্পর্কে বলেন,
إن كان بعد النبيين والصديقين موحد فهو الحلاج
নবী ও সিদ্দিকগণের পরে যদি কেউ একত্ববাদী হয়, তাহলে সে হল হাল্লাজ।
(আল-বিদায়া)
২। আবুল আব্বাস ইবনে আতা রহ (মৃত: ৩০৯ হি:)
তিনিও একজন মুহাদ্দিস ছিলেন। ইউসুফ ইবনে মুসা আল-কাত্তান ও ফজল ইবনে জিয়াদ প্রমুখ মুহাদ্দিস থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।
হাল্লাজের পক্ষ অবলম্বনের কারণে তিনি বিপদের মুখে পড়েন। তৎকালীন উজির হামেদ তাকে ডাকে। উজির তাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি হাল্লাজ সম্পর্কে কী বলো? তিনি বলেন,
তুমি তা দিয়ে কী করবে? তুমি মানুষের মাল লুন্ঠন আর রক্তপাত নিয়ে ব্যস্ত থাকো।
উজির হামেদ তাকে শাস্তির আদেশ করে। তখন তার দাঁত উপড়ে ফেলান হয়। তখন তিনি উজীর হামিদের বিরুদ্ধে বদ-দুয়া করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তোমার দুই হাত আর দুই পা কেটে দিক। পরবর্তীতে তার এই দু’য়া কবুল হয়।
আবুল আব্বাস ইবনে আতা রহ: উক্ত ঘটনার ১৪ দিন পর ইন্তিকাল করেন।
ইমাম জাহাবী পুরো বিষয়টা সিয়ারে তুলে ধরেছেন,
لكنه راج عليه حال الحلاج ، وصححه ، فقال السلمي : امتحن بسبب الحلاج ، وطلبه حامد الوزير وقال : ما الذي تقول في الحلاج ؟ فقال : ما لك ولذاك ؟ عليك بما ندبت له من أخذ الأموال ، وسفك الدماء . فأمر به ، ففكت أسنانه ، فصاح : قطع الله يديك ورجليك . ومات بعد أربعة عشر يوما ، ولكن أجيب دعاؤه ، فقطعت أربعة حامد . قال السلمي : سمعتأبا عمرو بن حمدان يذكر هذا .
যারা হাল্লাজের বিরুদ্ধে তৎকালীন আলিমদের ইজমার দাবী করেন, তাদের এই দাবী সম্পূর্ণ সঠিক নয়। আবুল আব্বাস ইবনে আতা রহ: উক্ত ঘটনা এর বাস্তব প্রমাণ। তার মতো বড় মাপের মুহাদ্দিস হাল্লাজের পক্ষ অবলম্বন করে নির্যাতনের মুখে পড়ে ইন্তিকাল করেন। সুতরাং ইজমার দাবী কীভাবে সঠিক হয়?
৩। মুহাম্মাদ ইবনে খাফীফ শিরাজী রহ (মৃত: ৩৭১ হি:)
তিনিও বড় মাপের মুহাদ্দিস ছিলেন। তার সম্পর্কে ইমাম জাহাবী রহ: লিখেছেন,
الشيخ الإمام العارف الفقيه القدوة ، ذو الفنون أبو عبد الله محمد بن خفيف بن اسفكشار الضبي الفارسي الشيرازي ، شيخ الصوفية .
অর্থ: শায়খ, ইমাম, আরিফ, ফকীহ, আমাদের আদর্শ, বহু শাস্ত্রের পন্ডিত আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন খাফীফ বিন ইসফিকশার জাব্বী ফারসী শিরাজী। তিনি সূফীগণের শায়খ।
তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আবুল ফজল খোজায়ী, হাসান ইবনে হাফস উন্দুলুসী, কাজী আবু বকর বাকিল্লানী।
তিনি ইবনে মানসুর হাল্লাজের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তার কাছ থেকে তাসাউফের জ্ঞান হাসিল করেন। ইবনে মানসুর বন্দী থাকা অবস্থায় তার সাথে সাক্ষাৎ করে বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞেস করেন। খতীব বাগদাদী রহ: তাকে হাল্লাজের সমর্থক হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
৪। আবু বকর শিবলী রহ: (৩৩৪ হি:)
তিনি বিখ্যাত সূফী, মালেকী মাজহাবের বড় আলিম ছিলেন। ইমাম জাহাবী তার সম্পর্কে বলেছেন,
وكان فقيها عارفا بمذهب مالك ، وكتب الحديث عن طائفة
অর্থ: তিনি ফকীহ ছিলেন। মালেকী মাজহাবের আলিম ছিলেন। একদল মুহাদ্দিস থেকে তিনি হাদীস লিখেছেন।
তিনিও হাল্লাজের পক্ষে ছিলেন। তিনি বলেন,
আমি ও হুসাইন ইবনে মানসুর হাল্লাজ একই অবস্থার উপর ছিলাম। তবে সে প্রকাশ করেছে কিন্তু আমি গোপন করেছি।
(আল-বিদায়া)
৫। ইমাম আবুল কাসিম কুশাইরী রহ:
ইমাম জাহাবী রহ: তার সম্পর্কে বলেন,
الإمام الزاهد ، القدوة ، الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيري ، الخراساني ، النيسابوري ، الشافعي ، الصوفي ، المفسر ، صاحب ” الرسالة ” .
অর্থ: ইমাম, দুনিয়াত্যাগী(জাহিদ), আদর্শ, উস্তাদ আবুল কাসিম আব্দুল কারিম বিন হাওয়াজিন বিন আব্দুল মালিক বিন ত্বালহা কুশাইরী খোরাসানী নাইসাপুরী। শাফেয়ী। সূফী। মুফাসসির। রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা এর লেখক।
ইবনে খাল্লিকান রহ: তার সম্পর্কে বলেন,
كان أبو القاسم علامة في الفقه والتفسير والحديث والأصول والأدب والشعر والكتابة
অর্থ: আবুল কাসিম কুশাইরী রহ: ফিকহ, তাফসীর, হাদীস, উসুল, আরবী সাহিত্য, কাব্য ও লেখনীতে আল্লামা ছিলেন।
(সিয়ারু আ’লামিন নুবালা)
আবুল কাসিম কুশাইরী রহ: বড় মাপের মুহাদ্দিস ছিলেন।
খতীব বাগদাদী রহ: তার সম্পর্কে বলেন,
كتبنا عنه ، وكان ثقة
অর্থ: আমরা তার কাছ থেকে হাদিস লিখেছি। তিনি বিশ্বস্ত (সিকা) ছিলেন।
(সিয়ারু আ’লামিন নুবালা)
তিনি তার আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়া-তে ইবনে মানসুর হাল্লাজের আকিদা বিশ্বাস বর্ণনা করেছেন।
তিনি লিখেছেন,
ألزم الكل الحدث لأن القدم له . فالذى بالجسم ظهوره فالعرض يلزمه . و الذى بالأداة اجتماعه . فقواها تمسكه . و الذى يؤلفه وقت يفرقه وقت .
و الذى يقيمه غيره فالضرورة تمسه . و الذى الوهم يظفر به فالتصوير يرتقى إليه . و من آواه محل أدركه أين . و من كان له جنس طالبه مكيّف .
إنه سبحانه لا يظله فوق . و لا يقله تحت . و لا يقابله حد . و لا يزاحمه عند . و لا يأخذه خلف .
و لا يحده أمام . و لم يظهه قبل و يفنه بعد . و لم يجمعه كل و لم يوجده كان . و لم يفقده ليس .
وصفه : لا صفة له . و فعله : لا عله له . و كونه : لا أمد له . تنزه عن أحوال خلقه . ليس له من خلقه مزاج . و لا فى فعله علاج . باينهم بقدمه . كما باينوه بحدوثهم .
إن قلت : متى فقد سبق الوجود كونه . و إن قلت : هو فالهاء و الواو خلقه . و إن قلت : أين فقد تقدم المكان وجوده .
فالحروف آياته ووجوده إثباته و معرفته توحيده وتوحيده تمييزه من خلقه .
ما تصور فى الأوهام فهو بخلافه . كيف يحل به ما منه بدأه ؟ أو يعود إليه ما هو أنشأه ؟
لا تماقله العيون . و لا تقابله الظنون . قربه كرامته . و بعده إهانته . علوّه من توقل . و مجيئه من غير تنقل .
هو : الأول و الآخر و الظاهر و الباطن . القريب البعيد الذى ليس كمثله شىء و هو السميع البصير .
অর্থ: হুসাইন ইবনে মনসুর হাল্লাজ বলেন, সব কিছুকে উদ্ভুত মনে করো। কারণ অবিনশ্বরতা একমাত্র আল্লাহর জন্য। তাই শরীরের মাধ্যমে যার প্রকাশ, নশ্বরতাও তার সাথে সংশ্লিষ্ট। উপকরণ দিয়ে যে একীভূত সেগুলোর শক্তি তাকে ধরে রাখে। সময় যাকে একত্র করে, তাকে আবার সময়-ই বিচ্ছিন্ন করে দেয়। যাকে অন্য কেউ স্থাপন করে, তার সাথে প্রয়োজন সংযুক্ত হয়। যাকে কল্পনা করা যায়, তাকে আঁকাও যায়। যাকে কোন স্থান ধারণ করে, তাকে বলা যায় ‘কোথায়’। যার কোন সমজাতীয়তা আছে, তার অনুসন্ধানী তাকে বলতে পারে, তিনি ‘কেমন’।
মহান আল্লাহ তায়ালাকে না কোন উঁচু স্থান ছায়া দেয়, না কোন নিচু স্থান বহন করে। কোন দিক তার সম্মুখীন হয় না, কোন স্থান তাকে সীমাবদ্ধ করতে পারে না, কোন সম্মুখ বা পশ্চাৎ তাকে আবদ্ধ করতে পারে না। ‘পূর্ববর্তিতা’ তার উন্মেষ ঘটায়নি, ‘পরবর্তীতা’ তাকে নি:শেষ করবে না। ‘সব’ তাকে একত্রিত করে না। ‘ছিলেন’ যেমন তাকে অস্তিত্ববান করেনি তেমনি ‘নেই’ তাকে অস্তিত্বহীন করবে না।
তার গুণাবলীর কোন ধরণ নেই। তার কর্মের কোন উপলক্ষ্য নেই। তার অস্তিত্বের সমাপ্তি নেই। তিনি তার সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যাবলী থেকে পবিত্র। তাদের সাথে তাঁর কোন সংমিশ্রণ নেই; তার কর্মে কোন মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। তিনি যেমন তার নিত্যতায় সৃষ্টি থেকে পৃথক, তেমনি সৃষ্টিও তাদের উদ্ভুদতায় তার থেকে পৃথক।
যদি প্রশ্ন করা হয়, তিনি কখন থেকে আছেন? বলা হবে, সময়ের অস্তিত্বের পূর্ব থেকেই তিনি আছেন। যদি বলা হয়, ‘হুয়া’ (তিনি), এই শব্দের ‘হা’এবং ‘ওয়াও’ আল্লাহর সৃষ্টি। যদি প্রশ্ন করা হয়, তিনি কোথায়? উত্তর দেয়া হবে, স্থান সৃষ্টির পূর্ব থেকেই তিনি আছেন। (অর্থাৎ সময় ও স্থানের সীমাবদ্ধতা থেকে আল্লাহ তায়ালা মুক্ত)।
অক্ষরসমূহ আল্লাহর নিদর্শন। আল্লাহর বিদ্যমাণতাই আল্লাহর অস্তিত্ব। আল্লাহর পরিচয় লাভ করা হলো তাউহীদ। আর আল্লাহর তাউহীদ হলো আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টি থেকে পৃথক বিশ্বাস করা।
তোমার ভাবনায় যা অঙ্কিত হয়, তিনি তার বিপরীত। এমন বস্তু তার মাঝে কীভাবে প্রবিষ্ট হবে, যা তার থেকে প্রকাশিত হয়নি? অথবা তিনি যার উদ্ভব ঘটিয়েছেন, তা কীভাবে তার কাছে ফিরে মিলবে? চর্মচক্ষু দিয়ে তাকে দেখা যায় না, ভাবনা তাকে বেষ্টন করতে পারে না। তার নৈকট্যের অর্থ সম্মানদান আর দূরত্বের অর্থ লাঞ্ছনাদান। তার উচ্চতা কোন আরোহন ব্যতীত আর তার আগমন কোন স্থানান্তর ব্যতীত।
তিনি সর্বপ্রথম যার কোন শুরু নেই। তিনি সর্বশেষ, যার কোন শেষ নেই। তিনি প্রকাশ্য ও গোপন, নিকটবর্তী ও দূরবর্তী কোন কিছুই তার মতো নয়। তিনি সব কিছু শোনেন। সব কিছু দেখেন।
(আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়া, অনুবাদ সংগৃহীত)
ইমাম আবুল কাসিম কুশাইরী রহ: উক্ত বক্তব্যের সনদ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,
أَخْبَرَنَا الشيخ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ السلمي رحمه اللَّه تعالي , قَالَ: سمعت مُحَمَّد بْن مُحَمَّد بْن غالب , قَالَ: سمعت أبا نصر أَحْمَد بْن سَعِيد الإسفنجاني , يَقُول: قَالَ الْحُسَيْن بْن مَنْصُور
অর্থ: আমার কাছে শায়খ আবু আব্দুর রহমান সুলামী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি মুহাম্মাদ বিন গালিবকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আবু নসর আহমাদ ইবনে সাইদ ইসফানজানীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, হুসাইন ইবনে মানসুর বলেন।
এটি উক্ত আকিদার পুরো সনদ। যা ইমাম কুশাইরী রহ: আর ‘আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়া’-তে উল্লেখ করেছেন।সুবহানাল্লাহ। কতো স্বচ্ছ আকিদা-বিশ্বাস। তথাকথিত অনেক সহীহ আকিদার দাবিদারদের সাদৃশ্যবাদী, দেহবাদী আকিদা থেকে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত। যেই হুলুলের অভিযোগ আনা হয়েছে, সেগুলো থেকেও তিনি আল্লাহ তায়ালাকে মুক্ত বিশ্বাস করতেন। আল্লাহ তায়ালাকে স্থান ও দিক থেকে মুক্ত বিশ্বাস করতেন। আল্লাহ তায়ালাকে কোন সৃষ্টির মাঝে বিশ্বাস করে তিনি হুলুলের আকিদা রাখতেন না। অনেকে তো মুখে দাবী করে তারা হুলুলের বিরোধী, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, তারা আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টির মাঝে বিশ্বাস করে। যা স্পষ্ট হুলুল। যেমন, কেউ বিশ্বাস করে আল্লাহ আসমানে আছেন। কেউ বিশ্বাস করে আরশে। কেউ বিশ্বাস করে উপরের দিকে। এসব হুলুলের আকিদার কারণে একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, এদের আকিদার চেয়ে ইবনে মানসুর হাল্লাজের আকিদা বিশ্বাস অনেক ভাল ছিল।
উপরে আমরা বিখ্যাত কয়েকজন মুহাদ্দিসের মতামত তুলে ধরেছি। কিছু ভাই প্রচার করে থাকেন, হাল্লাজ যেমন যিন্দিক, তার পক্ষে কেউ কথা বললে সেও যিন্দিক। নাউযুবিল্লাহ। আশা করি, তারা এধরণের অতিরঞ্জনমূলক তাকফিরি চিন্তা-চেতনা ফিরে আসবে। নতুবা ইসলামের অনেক বড় বড় ইমামকে যিন্দিক বলতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে এধরণের বিকৃত ও উগ্র মানসিকতা থেকে রক্ষা করুন।
ইবনে মানসুর হাল্লাজকে কি শুধু আনাল হক্ব বলার জন্য কাফির বলা যাবে না?
উত্তর:
না। কেউ যদি বাস্তবে মু’মিন হয়, তাহলে তার থেকে কোন কুফুর প্রকাশিত হলে সেই কুফুরের বাস্তবতা খুজে বের করতে হবে। সে যদি স্বাভাবিক অবস্থায়, সুস্থ্য-মস্তিষ্কে উক্ত কুফুরী কথা বলে এবং তার থেকে কুফুরীটা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়, তাহলে তার সম্পর্কে কুফুরীর কথা বলার সুযোগ আছে। তবে এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল, সে ঐ কুফুরীর উপর অটল-অবিচল থাকতে হবে। সে যদি অস্বাভাবিক অবস্থায় বলে অথবা তার থেকে তওবা প্রমাণিত হয় তাহলে কুফুরী সাব্যস্ত হবে না।
আনাল হক, যদিও কুফুরী শব্দ কিন্তু দু’টি কারণে এই শব্দের কারণে ইবনে মানসুর হাল্লাজকে কাফির বলা হবে না।
১। সে অস্বাভাবিক অবস্থায় এটি বলেছে।
২। তার থেকে এর বিপরীত বক্তব্য সনদসহ বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবুল কাসিম কুশাইরী রহ: তার আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়াতে তার আকিদা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ইবনে মানসুর হাল্লাজের তওবার কথাও অনেকে লিখেছেন। কাজী ইয়াজ রহ: তার আশ-শিফা-তে উল্লেখ করেছেন, তৎকালীন আলিমগণ হাল্লাজকে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সে বাহ্যিকভাবে শরীয়ত অনুসরণ করা সত্ত্বেও তার ‘আনাল হক’, হুলুলু ও খোদা দাবীর কারণে আলিমগণ তাকে হত্যার ফয়সালা করে। এ ব্যাপারে তারা হাল্লাজের তওবা কবুল করেনি।
হাল্লাজের তওবা কবুল না করার কারণ ছিল, তার সে তওবা করছিল, আবার তার থেকে এধরণের কথা প্রকাশিত হচ্ছিল। হাল্লাজের তওবা কবুল না করা সম্পর্কে নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান রহ: লিখেছেন,
و اقول ان ثبت انه تاب ، ثم رجع ثم اناب ثم قتل و لم يقبلوا توبته، فهذا فعل لا يتاتي الاقدام عليه الا ممن لم يدرك مدارك السنة الصحيحة علي وجهها، عفا الله عنا و عنهم اجمعين، و التائب من الذنب كمن لا ذنب له، و ان تكرر منه ذنب فالتوبة تمحو الحوبة و ان كثرت النوبة
অর্থ: আমি বলব, যদি প্রমাণিত হয় যে, হাল্লাজ তওবা করেছিল, এরপর আবার সে একই কথা বলেছে, আবার তওবা করেছে; কিন্তু এরপরও তাকে হত্যা করেছে এবং তার তওবা কবুল করেনি, তাহলে তো তার এই হত্যা রাসূল স: এর সহীহ সুন্নতের অনুসারী কোন ব্যক্তির কাজ হতে পারে না। আল্লাহ আমাদের এবং তাদের সবাইকে ক্ষমা করুন। হাদীসে তো এসেছে, তওবাকারী এমন যেন তার কোন গোনাহ নেই। যদিও সে একই অপরাধ বারবার করে। এরপরও তওবা তার অপরাধকে মুছে ফেলে। বারবার একই অপরাধ করলেও।
(আত-তাজুল মুকাল্লাল, পৃ:৩৮২)
কিছু কিছু আলিম মনে করেছেন, ইবনে মানসুর হাল্লাজ হুলুল ও ইত্তিহাদের আকিদার উপর মৃত্যুবরণ করেছে। এজন্য তারা তাকে কাফির বলেছেন। যেমন, ইবনে তাইমিয়া রহ: মনে করতেন, সে হুলুলের আকিদা পোষণ করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। কিন্তু শুধু আনাল হক বা এজাতীয় বক্তব্যের কারণে তিনি সূফীগণকে কাফের মনে করতেন না।
এবিষয়ে ইবনে তাইমিয়া রহ: এর বক্তব্যগুলি নিচে উল্লেখ করছি।
সূফীদের মুখ নি:সৃত বিভিন্ন ধরনের উক্তি বিশ্লেষণ করে ইবনে তাইমিয়া রহ. বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ইবনে তাইমিয়া রহ. লিখেছেন,সূফীদের বিভিন্ন সূক্ষ্ম ও ইঙ্গিতপূর্ণ কথা থাকে।
আল্লামা ইবনে তাইমিয়া বলেন-
وَاعْلَمْ أَنَّ لَفْظَ ” الصُّوفِيَّةِ ” وَعُلُومَهُمْ تَخْتَلِفُ فَيُطْلِقُونَ أَلْفَاظَهُمْ عَلَى مَوْضُوعَاتٍ لَهُمْ وَمَرْمُوزَاتٍ وَإِشَارَاتٍ تَجْرِي فِيمَا بَيْنَهُمْ فَمَنْ لَمْ يُدَاخِلْهُمْ عَلَى التَّحْقِيقِ وَنَازَلَ مَا هُمْ عَلَيْهِ رَجَعَ عَنْهُمْ وَهُوَ خَاسِئٌ وَحَسِيرٌ
“জেনে রেখ, তাছাউফ এবং তার ইলম বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। সূফীদের কথায় তাছাউফ সংক্রান্ত বিভিন্ন ইঙ্গিত থাকে। কখনও কখনও তারা শব্দকে ব্যাপক রাখেন, তাদের পরিভাষার উপর বিভিন্ন ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলেন, তারা বিভিন্ন সূক্ষ্ম বিষয়ের আলোচনা করে থাকেন, যার মর্ম কেবল তারাই অনুধাবন করেন। প্রকৃতপক্ষে যে তাদের সংস্পর্শে অবলম্বন না করে এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে ভালভাবে অবগত না হয়ে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করবে, তবে সে অপদস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে”
[মাজমুউল ফাতাওয়া, খ-৫, পৃষ্ঠা-৭৯]
ফানা, হালাত ও মাকামের ব্যাখ্যাঃ
الْفَنَاءَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ ” : نَوْعٌ لِلْكَامِلِينَ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ ؛ وَنَوْعٌ لِلْقَاصِدِينَ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ ؛ وَنَوْعٌ لِلْمُنَافِقِينَ الْمُلْحِدِينَ الْمُشَبِّهِينَ . ( فَأَمَّا الْأَوَّلُ ) فَهُوَ ” الْفَنَاءُ عَنْ إرَادَةِ مَا سِوَى اللَّهِ ” بِحَيْثُ لَا يُحِبُّ إلَّا اللَّهَ . وَلَا يَعْبُدُ إلَّا إيَّاهُ وَلَا يَتَوَكَّلُ إلَّا عَلَيْهِ وَلَا يَطْلُبُ غَيْرَهُ ؛ وَهُوَ الْمَعْنَى الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُقْصَدَ بِقَوْلِ الشَّيْخِ أَبِي يَزِيدَ حَيْثُ قَالَ : أُرِيدُ أَنْ لَا أُرِيدَ إلَّا مَا يُرِيدُ . أَيْ الْمُرَادُ الْمَحْبُوبُ الْمَرْضِيُّ ؛ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْإِرَادَةِ الدِّينِيَّةِ وَكَمَالُ الْعَبْدِ أَنْ لَا يُرِيدَ وَلَا يُحِبَّ وَلَا يَرْضَى إلَّا مَا أَرَادَهُ اللَّهُ وَرَضِيَهُ وَأَحَبَّهُ وَهُوَ مَا أَمَرَ بِهِ أَمْرَ إيجَابٍ أَوْ اسْتِحْبَابٍ ؛ وَلَا يُحِبُّ إلَّا مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ كَالْمَلَائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ . وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ فِي قَوْلِهِ : { إلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ } قَالُوا : هُوَ السَّلِيمُ مِمَّا سِوَى اللَّهِ أَوْ مِمَّا سِوَى عِبَادَةِ اللَّهِ . أَوْ مِمَّا سِوَى إرَادَةِ اللَّهِ . أَوْ مِمَّا سِوَى مَحَبَّةِ اللَّهِ فَالْمَعْنَى وَاحِدٌ وَهَذَا الْمَعْنَى إنْ سُمِّيَ فَنَاءً أَوْ لَمْ يُسَمَّ هُوَ أَوَّلُ الْإِسْلَامِ وَآخِرُهُ. وَبَاطِنُ الدِّينِ وَظَاهِرُهُ .
“ফানা তিন প্রকার। প্রথম প্রকার নবী ও কামেল ওলীদের ফানা। দ্বিতীয় প্রকার হল, ক্বাসেদীন তথা আল্লাহর ওলী ও সৎকর্মশীলদের ফানা। তৃতীয় প্রকার ফানা হল, মুনাফেক ও ধর্মদ্রোহী সাদৃশ্যদানকারীদের ফানা।
প্রথম প্রকারের ফানা হল, গাইরুল্লাহ তথা আল্লাহ ব্যতীত অন্য সব কিছু থেকে নিজের ইচ্ছাকে মিটিয়ে দেয়া অর্থাৎ বান্দা একমাত্র আল্লাহকেই মহব্বত করবে এবং একমাত্র তারই ইবাদত করবে, তার উপরই তাওয়াক্কুল করবে এবং তিনি ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকবে না। শায়েখ আবু ইয়াযীদ বুস্তামী (রহঃ) এর উক্তির উদ্দেশ্য এটিই। তিনি বলেন-“আমি কামনা করি যে, তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছুর ইচ্ছা করব না” অর্থাৎ তাঁর প্রিয় ও সন্তুষ্টপূর্ণ ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। আর দ্বীনি বিষয়ে যে কোন ইচ্ছার ক্ষেত্রে এটিই কাম্য। বান্দা তখনই কামেল হবে, যখন সে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছুর ইচ্ছা করবে না, আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত কোন কিছুতে সন্তুষ্ট হবে না এবং আল্লাহর মহব্বত ব্যতীত কোন কিছুকে মহব্বত করবে না। আল্লাহ তায়ালা যা আদেশ করেছেন, তা হয়ত আবশ্যকীয় কিংবা মুস্তাহাব পর্যায়ের। আল্লাহ যাকে মহব্বত করেন তাকে ব্যতীত অন্য কাউকে মহব্বত করবে না, যেমন ফেরেশতা, নবীগন ও সৎকর্মশীলগণ। পবিত্র কুরআনের নিম্নরে আয়াতের তাফসীরে তারা এটি উদ্দেশ্য নিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-
إلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (সেদিন কারও সম্পদ ও সন্তান কোন উপকারে আসবে না। তবে যে ব্যক্তি পরিচ্ছন্ন হৃদয়ে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে)
সূফীগণ বলেছেন- আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকল কিছু থেকে মুক্ত হৃদয় অথবা আল্লাহর ইবাদত ব্যতীত অন্য সকল কিছু থেকে মুক্ত, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত সকল কিছু থেকে মুক্ত অথবা আল্লাহর মহব্বত ব্যতীত সকল কিছু থেকে মুক্ত হৃদয়ে যে উপস্থিত হবে। এ সকল অর্থের উদ্দেশ্য এক। আর একে ফানা বলা হয়। এখন কেউ একে ফানা বলুক চাই না বলুক, এটিই মূলতঃ ইসলামের শুরু, এটিই শেষ, এটি দ্বীনের বাহ্যিক (জাহের) এবং এটিই দ্বীনের বাতেন (অভ্যন্তর)।
[মাজমুঊল ফাতাওয়া, খ–১০, পৃষ্ঠা-২১৯]
আল্লামা ইবনে তাইমিয়া “ফানার” দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন-
وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي : فَهُوَ ” الْفَنَاءُ عَنْ شُهُودِ السِّوَى ” . وَهَذَا يَحْصُلُ لِكَثِيرِ مِنْ السَّالِكِينَ ؛ فَإِنَّهُمْ لِفَرْطِ انْجِذَابِ قُلُوبِهِمْ إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَعِبَادَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ وَضَعْفِ قُلُوبِهِمْ عَنْ أَنْ تَشْهَدَ غَيْرَ مَا تَعْبُدُ وَتَرَى غَيْرَ مَا تَقْصِدُ ؛ لَا يَخْطُرُ بِقُلُوبِهِمْ غَيْرُ اللَّهِ ؛ بَلْ وَلَا يَشْعُرُونَ ؛ كَمَا قِيلَ فِي قَوْلِهِ : { وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا } قَالُوا : فَارِغًا مَنْ كُلِّ شَيْءٍ إلَّا مِنْ ذِكْرِ مُوسَى . وَهَذَا كَثِيرٌ يَعْرِضُ لِمَنْ فَقَمَهُ أَمْرٌ مِنْ الْأُمُورِ إمَّا حُبٌّ وَإِمَّا خَوْفٌ . وَإِمَّا رَجَاءٌ يُبْقِي قَلْبَهُ مُنْصَرِفًا عَنْ كُلِّ شَيْءٍ إلَّا عَمَّا قَدْ أَحَبَّهُ أَوْ خَافَهُ أَوْ طَلَبَهُ ؛ بِحَيْثُ يَكُونُ عِنْدَ اسْتِغْرَاقِهِ فِي ذَلِكَ لَا يَشْعُرُ بِغَيْرِهِ . فَإِذَا قَوِيَ عَلَى صَاحِبِ الْفَنَاءِ هَذَا فَإِنَّهُ يَغِيبُ بِمَوْجُودِهِ عَنْ وُجُودِهِ وَبِمَشْهُودِهِ عَنْ شُهُودِهِ وَبِمَذْكُورِهِ عَنْ ذِكْرِهِ وَبِمَعْرُوفِهِ عَنْ مَعْرِفَتِهِ حَتَّى يَفْنَى مَنْ لَمْ يَكُنْ وَهِيَ الْمَخْلُوقَاتُ الْمُعَبَّدَةُ مِمَّنْ سِوَاهُ وَيَبْقَى مَنْ لَمْ يَزُلْ وَهُوَ الرَّبُّ تَعَالَى . وَالْمُرَادُ فَنَاؤُهَا فِي شُهُودِ الْعَبْدِ وَذِكْرِهِ وَفَنَاؤُهُ عَنْ أَنْ يُدْرِكَهَا أَوْ يَشْهَدَهَا . وَإِذَا قَوِيَ هَذَا ضَعُفَ الْمُحِبُّ حَتَّى اضْطَرَبَ فِي تَمْيِيزِهِ فَقَدْ يَظُنُّ أَنَّهُ هُوَ مَحْبُوبُهُ كَمَا يُذْكَرُ : أَنَّ رَجُلًا أَلْقَى نَفْسَهُ فِي الْيَمِّ فَأَلْقَى مُحِبُّهُ نَفْسَهُ خَلْفَهُ فَقَالَ : أَنَا وَقَعْتُ فَمَا أَوْقَعَكَ خَلْفِي قَالَ : غِبْتُ بِكَ عَنِّي فَظَنَنْتُ أَنَّكَ أَنِي
“দ্বিতীয় প্রকার হল, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর দর্শন ও চিন্তা থেকে ফানা হওয়া। এটি অনেক সালেকেরই অর্জিত হয়ে থাকে। কেননা তারা আল্লাহর যিকিরের প্রতি অধিক আসক্তি, অধিক ইবাদত ও মহব্বত এবং অন্তরের মুজাহাদার মাধ্যমে এমন স্তরে উন্নীত হন যে, তাদের অন্তর মা’বুদ ব্যতীত অন্য কিছুকে প্রত্যক্ষ করে না, মা’বুদ ব্যতীত অন্য কারও প্রতি তাদের ক্বলব ধাবিত হয় না। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছু তাদের কল্পনায়ও আসে না বরং তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছু অনুভব করতে পারেন না। যেমন হযরত মুসা (আঃ) এর মা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,
“সকালে মূসা জননীর অন্তর অস্থির হয়ে পড়ল। যদি আমি তাঁর হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিতাম, তবে তিনি মূসা জনিত অস্থিরতা প্রকাশ করেই দিতেন। [সূরা ক্বাসাস-১০]
সূফীগণ বলেছেন- তাঁর হৃদয় মুসা (আঃ) এর স্মরণ ব্যতীত অন্য সব কিছু থেকে মুক্ত হয়ে গেছে। এটি অনেক ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। যেমন কেউ অধিক ভয়, মহব্বত কিংবা অধিক আশায় নিপতিত হলে তার অন্তর অন্য সব কিছু থেকে খালি হয়ে যায় এবং তার অন্তর ভয়, মহব্বত কিংবা আশা ব্যতীত অন্য সব কিছু থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় সে তার উদ্দিষ্ট বিষয়ে এতটা নিমগ্ন থাকে যে, অন্য কিছুর অস্তিত্বই অনুভব করতে পারে না। “ফানার” অধিকারীর উপর যখন এ অবস্থা প্রবল হয়, তখন সে তার অস্তিত্ব ভুলে যায়, নিজের ধ্যান থেকে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হয়, নিজের কথা ভুলে আল্লাহকে স্মরণ করে এমনকি অস্তিত্বহীন সকল কিছু তাঁর নিকট ফানা হয়ে যায়, অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য যা কিছুর ইবাদত করা সব কিছু অস্তিত্বহীন মনে হয় এবং এককভাবে আল্লাহ তায়ালাই তাঁর অন্তরে বিদ্যমান থাকে। সুতরাং মূল উদ্দেশ্য হল, বান্দার ধ্যান থেকে এবং বান্দার স্মরণ থেকে মাখলুকাত ফানা হওয়া এবং বান্দা এ সমস্ত জিনিসের অস্তিত্ব অনুভব কিংবা ধ্যান থেকে ফানা হওয়া। এ অবস্থা যখন প্রবল হয়, তখন প্রেমিক দূর্বল হয়ে পড়ে এমনকি তাঁর বিশ্লেষণ ক্ষমতার মাঝে ত্রুটি দেখা যায়, তখন সে নিজেকেই তার প্রেমাস্পদ মনে করতে শুরু করে। যেমন, বলা হয়, এক ব্যক্তি নিজেকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলে তার প্রেমিকও তার পিছে পিছে ঝাঁপ দিয়েছে। তখন সে তার প্রেমিককে জিজ্ঞেস করল যে, আমি নিজে পড়েছি, তোমাকে কে নিক্ষেপ করল? সে বলল- তোমার ধ্যানে আমি আমার নিজের অস্তিত্ব ভুলে গেছি। আমি মনে করেছি তুমিই আমি।”
[মাজমুউল ফাতাওয়া, খ–১০, পৃষ্ঠা-২১৯]
ইবনে তাইমিয়া বলেন-
وَفِي هَذَا الْفَنَاءِ قَدْ يَقُولُ : أَنَا الْحَقُّ أَوْ سُبْحَانِي أَوْ مَا فِي الْجُبَّةِ إلَّا اللَّهُ إذَا فَنِيَ بِمَشْهُودِهِ عَنْ شُهُودِهِ وَبِمَوْجُودِهِ عَنْ وُجُودِهِ . وَبِمَذْكُورِهِ عَنْ ذِكْرِهِ وَبِمَعْرُوفِهِ عَنْ عِرْفَانِهِ . كَمَا يَحْكُونَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ مُسْتَغْرِقًا فِي مَحَبَّةِ آخَرَ فَوَقَعَ الْمَحْبُوبُ فِي الْيَمِّ فَأَلْقَى الْآخَرُ نَفْسَهُ خَلْفَهُ فَقَالَ مَا الَّذِي أَوْقَعَك خَلْفِي ؟ فَقَالَ : غِبْت بِك عَنِّي فَظَنَنْت أَنَّك أَنِّي . وَفِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ يَقَعُ السُّكْرُ الَّذِي يُسْقِطُ التَّمْيِيزَ مَعَ وُجُودِ حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ كَمَا يَحْصُلُ بِسُكْرِ الْخَمْرِ وَسُكْرِ عَشِيقِ الصُّوَرِ . وَكَذَلِكَ قَدْ يَحْصُلُ الْفَنَاءُ بِحَالِ خَوْفٍ أَوْ رَجَاءٍ كَمَا يَحْصُلُ بِحَالِ حُبٍّ فَيَغِيبُ الْقَلْبُ عَنْ شُهُودِ بَعْضِ الْحَقَائِقِ وَيَصْدُرُ مِنْهُ قَوْلٌ أَوْ عَمَلٌ مِنْ جِنْسِ أُمُورِ السُّكَارَى وَهِيَ شَطَحَاتُ بَعْضِ الْمَشَايِخِ : كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ : أَنْصِبُ خَيْمَتِي عَلَى جَهَنَّمَ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الْمُخَالِفَةِ لِلشَّرْعِ ؛ وَقَدْ يَكُونُ صَاحِبُهَا غَيْرَ مَأْثُومٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَيُشْبِهُ هَذَا الْبَابُ أَمْرَ خُفَرَاءِ الْعَدُوِّ وَمَنْ يُعِينُ كَافِرًا أَوْ ظَالِمًا بِحَالِ وَيَزْعُمُ أَنَّهُ مَغْلُوبٌ عَلَيْهِ . وَيَحْكُمُ عَلَى هَؤُلَاءِ أَنَّ أَحَدَهُمْ إذَا زَالَ عَقْلُهُ بِسَبَبِ غَيْرِ مُحَرَّمٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَصْدُرُ عَنْهُمْ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الْمُحَرَّمَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ سَبَبُ زَوَالِ الْعَقْلِ وَالْغَلَبَةِ أَمْرًا مُحَرَّمًا . وَهَذَا كَمَا قُلْنَا فِي عُقَلَاءِ الْمَجَانِينِ والمولهين الَّذِينَ صَارَ ذَلِكَ لَهُمْ مَقَامًا دَائِمًا كَمَا أَنَّهُ يَعْرِضُ لِهَؤُلَاءِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ ذَلِكَ فِي مَنْ زَالَ عَقْلُهُ حَتَّى تَرَكَ شَيْئًا مِنْ الْوَاجِبَاتِ . إنْ كَانَ زَوَالُهُ بِسَبَبِ غَيْرِ مُحَرَّمٍ مِثْلِ الْإِغْمَاءِ بِالْمَرَضِ أَوْ أُسْقِيَ مُكْرَهًا شَيْئًا يُزِيلُ عَقْلَهُ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ وَإِنْ زَالَ بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْوَالِ الْمُحَرَّمَةِ أَثِمَ بِتَرْكِ الْوَاجِبِ وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ فِي فِعْلِ الْمُحَرَّمِ . وَكَمَا أَنَّهُ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فَلَا يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِهِمْ وَلَا حَمْلُ كَلَامِهِمْ وَفِعَالِهِمْ عَلَى الصِّحَّةِ بَلْ هُمْ فِي الْخَاصَّةِ مِثْلُ الْغَافِلِ وَالْمَجْنُونِ فِي التَّكَالِيفِ
“এ ফানার কারণে অনেক ক্ষেত্রে সূফীগণ বলেছেন, আমি হক্ব (আল্লাহ), আমার সত্ত্বা সুমহান, অথবা আমার জামার নিচে আল্লাহ ব্যতীত আর কিছুই ন্য়। যখন তারা নিজের ধ্যান থেকে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হয়, নিজের অস্তিত্ব থেকে আল্লাহর অস্তিত্বে নিমজ্জিত হয়, নিজের স্মরণ থেকে আল্লাহর স্মরণে অবগাহন করে এবং নিজের মা’রেফাত থেকে আল্লাহর মা’রেফাতে ডুব দেয় তখন এ ধরণের পরিস্থিতির স্বীকার হয়। যেমন, ঘটনা বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে, এক ব্যক্তি অন্য কারও মহব্বতে নিমজ্জিত ছিল। কোন একদিন প্রেমাস্পদ সাগরে পড়ে গেলে প্রেমিকও তার পিছে পিছে নিজেকে সাগরে নিক্ষেপ করল। প্রেমাস্পদ জিজ্ঞেস করল, তোমাকে কে ফেলল? তখন সে বলল, আমি তোমার মাঝে হারিয়ে গেছি, আমি মনে করেছি, তুমিই আমি। এ অবস্থায় মানুষের মাঝে মাতাল অবস্থার সৃষ্টি হয়, যা তার বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতা দূর করে দেয়, কিন্তু ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে থাকে, যেমন মদ্যপ ব্যক্তি মদের স্বাদ এবং গাইরুল্লাহর প্রেমিক তার প্রেমের স্বাদ আস্বাদন করে। কখনও ভয় ও আশার কারণে “ফানা” এর অবস্থা সৃষ্টি হয়, যেমন মহব্বতের কারণেও ফানার সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় অন্তর কিছু কিছু হাকীকত বুঝতে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং তার থেকে এমন কিছু কাজ বা কথা প্রকাশ পায়, যা মাতালদের থেকে পাওয়া যায়।
ইবনে তাইমিয়া বলেন-
“قد يقع بعض من غلب عليه الحال في نوع من ا لحلول والاتحاد .. لماورد عليه ماغيب عقله أولإناه عما سوى محبوبه, ولم يكن ذلك بذنب منه كان معذورًا غير معاقب عليه مادام غيرعاقل… وهذا كما يحكى : أن رجلين كان أحدهما يحب الآخر فوقع المحبوب في اليم , فألقى الآخر نفسه خلفه فقال: أناوقعت, فما الذي أوقعك ؟ فقال: غبت بك عني, فظننت أنك أني.
فهذه الحال تعتري كثيرً امن أهل المحبة والإرادة في جانب الحق, وفي غيرجانبه… فإنه يغيب بمحبوبه عن حبه وعن نفسه , وبمذكوره عن ذكره… فلا يشعر حينئذ بالتميز ولابوجوده , فقد يقول في هذه الحال : أنا الحق أوسبحاني أومافي الجبة إلا الله ونحوذلك …
“কিছু মাজযুবের উপর যখন তাদের হালত প্রবল হয়ে যায়, তাদের থেকে এমন কিছু কথা প্রকাশ পায় যা “হুলুল” (অনুপ্রবেশ) ও ইত্তেহাদ (সত্ত্বাগত একাত্মতা) এর অন্তর্ভূক্ত। তার উপর আরোপিত বিষয়ের কারণে তার আক্বল চলে যায়, অথবা তাঁর মাহবুবের প্রতি প্রবল আসক্তির কারণে। এটি তার পক্ষ থেকে কোন গোনাহর কারণে নয়। এক্ষেত্রে তিনি মা’জুর এবং যতক্ষণ তিনি আক্বলহীন থাকবেন ততক্ষণ কোন শাস্তির যোগ্য হবেন না। তাদের অবস্থা ঐ ব্যক্তির ঘটনার মত যার সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, দু’ব্যক্তি একে অপরকে মহব্বত করত। প্রেমাস্পদ সাগরে পড়ে গেলে প্রেমিকও সাগরে পড়ে যায়। তখন প্রেমাস্পদ বলল, আমি পড়ে গেছি, তোমাকে কে ফেলল? প্রেমিক বলল- আমি তোমার মাঝে হারিয়ে গেছি, আমি ধারণা করেছি, আমি তুমিই।
…এ সমস্ত অবস্থা মহব্বত ও ইরাদার অধিকারী অনেককে হকের পথে পরিচালিত করে, অনেককে তা অন্য দিকে পরিচালিত করে। কেননা সে তার প্রেমাস্পদের মাঝে হারিয়ে যায় এমনিক নিজের প্রেম ও অস্তিত্ব সম্পর্কে ভুলে যায়, যিকিরের মাধ্যমে সে আল্লাহর ইশকের মাঝে হারিয়ে যায়, তখন তার কোন পার্থক্য জ্ঞান থাকে না এবং সে নিজের অস্তিত্ব বুঝতে পারে না। এ অবস্থায় কখনও তারা বলে থাকে যে, আমি হক্ব, আমার সত্ত্বা মহান, অথবা আমার জামার নিচে আল্লাহ ব্যতীত আর কিছ্ইু নয় ইত্যাদি।
[মাজমুউল ফাতাওয়া, খ–২, পৃষ্ঠা-৩৯৬]
ইবনে তাইমিয়া . এর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, সূফীদের এজাতীয় বক্তব্যের কারণে বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই তাদেরকে কাফের বলা হবে না।
প্রশ্ন: জারাহ-তা’দীলের আলিমগণ তো ইবনে মানসুরের জারাহ করেছেন। যেমন ইবনে হাজার আসকালানী রহ, ইমাম জাহাবী রহ, ইমাম ইবনে কাসীর রহ। তাদের জারাহ গ্রহণ করে তাকে কাফের বলছেন না কেন?
উত্তর:
প্রথমেই জারাহ তা’দীল সম্পর্কে আপনার ধারণা স্পষ্ট করে নিতে হবে। জারাহ-তা’দীল মূলত: রাসূল স: এর হাদীস সংরক্ষণের জন্য। কাউকে কাফির বা ফাসিক প্রমাণের জন্য নয়। প্রথমত: ইবনে মানসুর হাল্লাজ থেকে কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি। সুতরাং হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে তার জারাহ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। জারাহ-তা’দীলের কিতাবে তাকে স্থান দেয়ারও কোন বিশেষ প্রয়োজন চোখে পড়ে না। কেউ হয়ত বলবে অনেক মিথ্যুক রাবীর জীবনীও তো আছে। হ্যাঁ। আছে, কিন্তু ইবনে মানসুর তো কোন হাদীসের রাবী নয় যে তাকে জারাহ-তা’দীলের কিতাবে স্থান দিতে হবে। দ্বিতীয়ত: সে যদি বাস্তবেই যিন্দিক হতো, তাহলে তাকে জারাহ এর কিতাবে স্থান দেয়া কীভাবে যৌক্তিক হয়?
দ্বিতীয়ত: জারাহ-তা’দীল সম্পর্কে কিছু মৌলিক কথা সবার হ্নদয়ে গেথে নেয়া উচিৎ। শায়খ শরীফ হাতিম আল-আউনী হাফিজাহুল্লাহ তার ‘আত-তাখরীজ ও দিরায়াতুল আসানিদ’ কিতাবের শেষে বিষয়গুলি উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন,
وينبغي أن يُعلم أن الجرح والتعديل في الأصل هو غيبة ، ولولا ضرورة هذه الغيبة وأن مفسدتها أقلُّ من مفسدة عدم الغيبة ، لما رضي العلماء بالجرح أبداً ، والضرورة تُقدر بقدرها ، فيجب عليّ أن لا أتجاوز موطن الضرورة ، ومن المؤسف أن بعض طلبة العلم الذي قد يسمع-مثلاً- أن شريك بن عبدالله القاضي فيه ضعف ، فإذا ذكره فإنه يذكره بسخرية ، ولو كان حيّاً لما استطاع أن يواجهه بهذه الطريقة ، مع أن شريك بن عبدالله القاضي كان عالماً من علماء السنّة ، آمراً بالمعروف ، ناهياً عن المنكر ، وكان من أشدِّ الناس في قمع أهل البدع ، وفلان من الناس قد يكون عابداً من العباد أو زاهداً من الزهاد ، ضُعّف لسوء حفظه ، فيجب عليك أن تنتبه لألفاظك وعباراتك مع هؤلاء . وهذا يُبيّن ضرورة مراجعة كتب التراجم المطوّلة ، حتى تتبيّن حال الرواة ، وتُنزّل الناس منازلهم .
لمّا كان ابن أبي حاتم يُحدّث بكتابه (الجرح والتعديل) ، أتاه أحد الزهاد فقال له :”يا أبا محمد لعلك تتكلم في أناس وضعوا رحالهم في الجنة من مائتي سنة” ، فأوقف ابن أبي حاتم الدرس ، وجعل يبكي ، مع علمه بوجوب هذا الأمر وأهميته ، إذ لولاه لذهب كثير من السنّة ، وضاع كثير من الدين .
ثم اعلم أن حكمك على الراوي خطيرٌ جداً ، من أجل ذلك يقول ابن دقيق العيد :” أعراض المسلمين حفرةٌ من حفر النار ، وقف على شفيرها صنفان من الناس المُحدِّثون والحكام” ، والمقصود أن الذي يتكلم في الحديث على شفير جهنم ، إلا أن يوفقه الله -عز وجل- ؛ وذلك لأن تضعيف راوٍ واحد ، قد يكون ثقة ، معناه أنك حكمت على جميع أحاديثه بأنها ليست سنةً ، وليست ديناً ، وليست وحياً من رب العالمين ،ولانوراً يُهتدى به . وحكمك على راوٍ بأنه ثقةٌ ، معناه أن أحاديثه يجب أن تلتزم بها ، وأنها وحي وحقٌ وخير يجب أن تعتقده وتعمل به ، وكذلك الحكم على الحديث خطيرٌ جداً .
অর্থ: সবার জেনে রাখা উচিৎ, জারাহ-তা’দীল মূলত: গীবত (পরনিন্দা)। যদি এই গীবতের প্রয়োজন না থাকত এবং গীবত না করার ক্ষতি যদি গীবত করার চেয়ে কম হতো, তাহলে আলিমগণ কখনও কারও জারাহ(সমালোচনা) করতেন না। মনে রাখতে হবে, জরুরতের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। আমাদের জন্য আবশ্যক হল, আমরা যেন এ প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম না করি। দু:খজনক বিষয় হল, কিছু তালিবে ইলম এর ক্ষেত্রে দেখা যায়, যদি সে শোনে যে, কাজী শরীক ইবনে আব্দুল্লাহ দুর্বল ছিলেন। এরপর যখন সে তার আলোচনা করে, তাকে নিয়ে উপহাস ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। অথচ কাজী শরীক যদি জীবিত থাকতেন, তার সামনে কখনও এমনটি করতে পারত না। আর কাজী শরীক ইবনে আব্দুল্লাহ আহলে সুন্নতের বরেণ্য আলিম ছিলেন। সৎকাজে আদেশ, অসৎকাজে নিষেধে অগ্রণী ভূমিকা রাখতেন। বিদয়াতীর বিরুদ্ধে তিনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন।
কোন এক ব্যক্তি অনেক বড় আবিদ ছিলেন, অনেক বড় দুনিয়াত্যাগী (জাহিদ) ছিলেন, কিন্তু স্মৃতিশক্তির দিক থেকে তিনি দুর্বল, এধরণের ব্যক্তিদের সম্পর্কে শব্দ চয়নে তোমাকে অবশ্যই যারপরনাই সতর্ক হতে হবে। বিষয়টি জারাহ-তা’দীলের বড় বড় কিতাবে তাদের জীবনী অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তাকে আরও প্রকট করে দিয়েছে। এর মাধ্যমে তুমি তাদের বিস্তারিত জীবনী জানতে পারবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার সঠিক অবস্থানে রাখতে পারবে।
একদিন ইবনু আবি হাতিম রহ: তার ‘আল-জারহু ওয়াত-তা’দীল’ কিতাব বর্ণনা করছিলেন। ইতোমধ্যে এক জাহিদ (দুনিয়াত্যাগী বুজুর্গ) এসে বলল, হে আবু হাতিম, তুমি হয়ত এমন ব্যক্তিদের সমালোচনা করছ, যারা দু’শ বছর আগে জান্নাতে তাদের পা রেখেছে।
তার কথা শুনে ইবনু আবি হাতিম রহ: তার দরস বন্ধ করে দিলেন। এরপর কাঁদতে শুরু করলেন। অথচ ইবনে আবি হাতিম রহ: জারাহ তা’দীলের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব জানতেন। কারণ জারাহ তা’দীল না থাকলে অনেক হাদিস হারিয়ে যেত, দ্বীনের অনেক কিছু নষ্ট হতো।
তুমি মনে রেখো, কোন রাবীর ব্যাপারে তোমার হুকুম প্রদান একটা ভয়াবহ বিষয়। এজন্য ইমাম ইবনে দাকীক আল-ইদ বলেন, “মুসলমানদের ইজ্জত-সম্মান জাহান্নামের গর্তসমূহের একটি। এই গর্তের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে দু’শ্রেণির লোক। মুহাদ্দিস ও বিচারকগণ।”
এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যে হাদীস নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করে সে জাহান্নামের গর্তের কিনারায়। তবে আল্লাহ যাকে তৌফিক দিয়েছেন, সে এর ব্যতিক্রম।
কোন একজন রাবী বাস্তবে বিশ্বস্ত হতে পারে, কিন্তু তুমি যদি তাকে জয়ীফ (দুর্বল) সাব্যস্ত করো, তাহলে তার বর্ণিত সমস্ত হাদিসকে তুমি দুর্বল সাব্যস্ত করে দিলে। তার হাদীসগুলোকে দ্বীন ও সুন্নাতের গন্ডি থেকে বের করে দিলে। তোমার হুকুমের কারণে এখন এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী নয়, অনুসরণযোগ্য হিদায়াত ও নূর নয়। কোন একজন রাবীর ব্যাপারে তুমি যদি হুকুম দাও, সে বিশ্বস্ত (সিকা), তাহলে তার বর্ণিত সমস্ত হাদীস গ্রহণ করা জরুরি হয়ে পড়ে। এগুলোর ব্যাপারে তখন বিশ্বাস করতে হয় যে, এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী। এগুলো সত্য। এর মাঝে কল্যাণ নিহিত আছে। এর প্রতি ইমান রাখা এবং আমল করা জরুরি হয়ে পড়ে। একইভাবে কোন একটা হাদীসের উপর সহীহ-জয়ীফের হুকুম লাগানও অত্যন্ত মারাত্মক বিষয়।
(আত-তাখরীজ ও দিরায়াতুল আসানিদ, অনুবাদ সমাপ্ত)
এই দীর্ঘ আলোচনা থেকে আমাদের সামনে কয়েকটা বিষয় স্পষ্ট হয়েছে।
১। জারাহ-তা’দীলে কাউকে মিথ্যুক, ফাসিক বা অন্য কোন সমালোচনা করার কারণে এটি প্রমাণ করে না যে, তিনি আজীবন ঐ অবস্থায় ছিলেন। তার মৃত্যুও ঐ অবস্থার উপর হয়েছে। অনেক রাবী এমন আছে, যারা জারাহ-তা’দীলে মারাত্মক সমালোচিত, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের জান্নাতের ফয়সালা করে দিয়েছেন। ইমাম ইবনু আবি হাতিমের ঘটনাটি এক্ষেত্রে আমাদের জন্য শিক্ষণীয়।
২। জারাহ-তা’দীল প্রয়োজন অনুপাতে ব্যবহার করা হবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত এর ব্যবহার সঠিক নয়।
৩। কোন রাবীকে নিয়ে উপহাস বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার অনুমতি ইসলাম দেয় না। কারণ জারাহ-তা’দীলে তার শেষ পরিণতি বলা সম্ভব নয়। হাদীস সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কেবল তার বাহ্যিক অবস্থার উপর হুকুম দেয়া হবে হাদীসের প্রয়োজনে। সর্বদা একই অবস্থায় ছিলেন বা তার শেষ পরিণতি তুলে ধরার জন্য জারাহ-তা’দীল নয়।
এবার আসি ইবনে মানসুরের তাকফিরের বিষয়ে।
১। কোন ব্যক্তির তাকফিরের জন্য অকাট্য দলিলের প্রয়োজন। আর ইবনে হাজার আসকালানী বা অন্যরা যেই বর্ণনাগুলো পেশ করেছেন, এগুলো সব খবরে ওয়াহিদ। আর খবরে ওয়াহিদ কারও তাকফিরের জন্য যথেষ্ট নয়। কোন এক ব্যক্তির একক বর্ণনা বা কথার ভিত্তিতে শরীয়ত কাউকে তাকফিরের অনুমতি দেয় না। কারও মুসলমান হওয়ার বিষয়টা যদি নিশ্চিত হয়, তাহলে শুধু খবরে ওয়াহিদের উপর ভিত্তি করে তাকে তাকফির করার সুযোগ নেই।
২। এই সব খবরে ওয়াহিদের সনদগুলো ব্যাপকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ প্রয়োজন। একাজটি না করা হলে বাহ্যিক বর্ণনার উপর ভিত্তি করা হুকুম দেয়া সঠিক হবে না।
৩। এসব বক্তব্যের সঠিক ব্যাখ্যা বা তা’বীল করা সম্ভব। এজন্য কাজী শাওকানী ৪০ বছর পরে তাকফির থেকে রুজু করেন। তার মতে, কারও বক্তব্য যদি বাহ্যিকভাবে শরীয়ত বিরোধী হয় এবৎ ঐ ব্যক্তি বাস্তবে মু’মিন হয়ে থাকে, তাহলে যথা সম্ভাব তার বক্তব্যের ব্যাখ্যা বা তা’বীল করা উচিৎ।
৪। কাজী ইয়াজ রহ: ইবনে মানসুর হাল্লাজের হত্যার বিষয়ে লিখেছেন, “তৎকালীন কাযী আবূ উমর মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ আল-মালেকী (রহ.) হাল্লাজের হত্যার ফতোয়া দেন। আলিমরা তখন ইবনে মানসুরের তওবা কবুল করেননি। ”
তওবা কবুল না করে তাকে হত্যার ফয়সালা দেয়ার একটি যৌক্তিক কারণ এও হতে পারে যে, ইবনে মানসুর মানুষের ফেতনার কারণ হচ্ছিলেন, সেদিকে লক্ষ রেখে তারা ফতোয়া দিতে পারেন। কিন্তু ইবনে মানসুর হাল্লাজ যদি তওবা করে থাকেন, তাহলে তওবার পরেও তাকে কাফির বা যিন্দিক বলার সুযোগ থাকে না। তবে তওবার পরেও ফেতনা বন্ধের উদ্দেশ্যে কাজী কাউকে হত্যা করতে পারেন। তখন এটি তা’জীর হিসেবে গণ্য হবে। কাফির হওয়ার কারণে হত্যার দন্ডবিধি হিসেবে গণ্য হবে না।
মানুষ যত বড় অপরাধই করুক, তার তওবা কবুল করা উচিৎ। তওবা কবুল না করার কারণে ইবনে মানসুরের হত্যার ফতোয়াদানকারীদের কঠোর সমালোচনা করেছেন বরেণ্য আহলে হাদিস আলিম নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান তার আত-তাজুল মুকাল্লালে। আমরা পূর্বে তার বক্তব্য উল্লেখ করেছি।
৫। তার শেষ পরিণতি কী হয়েছিল এটা আল্লাহ ছাড়া কারও বলা সম্ভব নয়। আমরা শুধু ধারণা রাখতে পারি। যারা কাফির বলছেন, তারাও ধারণার উপর বলছেন। আবার যারা তাকে কাফির বলছেন না, তারাও ধারণার উপর বলছেন। তবে ইবনুল কাইয়্যিম রহ: তার ‘আর-রুহ’ কিতাবে ইবনে মানসুর হাল্লাজের ভালো অবস্থার ব্যাপারে একটি স্বপ্ন বর্ণনা করেছে। উক্ত স্বপ্ন যদি সত্য হয়, তাহলে তার শেষ পরিণতি ভালো হওয়ার দিকটা শক্তিশালী হয়।
৬। আলিমগণ তাকফিরের ব্যাপারে যারপরনাই সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। তাদের এই সতর্কতা শুধু মৌখিক নয়। এটি বাস্তব ও প্রয়োগিক। তাকফির বিষয়ে আলিমগণের কিছু বক্তব্য এখানে উল্লেখ করছি।
তাকফির বিষয়ে আলিমগণের বক্তব্য:
১. আল্লামা মোল্লা আলী কারী রহঃ শরহে ফিক্বহুল আকবারে বলেন,
কুফরী সম্পর্কিত বিষয়ে, যখন কোন বিষয়ে ৯৯ ভাগ সম্ভাবনা থাকে কুফরীর, আর এক ভাগ সম্ভাবনা থাকে, কুফরী না হওয়ার; তাহলে মুফতী ও বিচারকের জন্য উচিত হল কুফরী না হওয়ার উপর আমল করা। কেননা ভুলের কারণে এক হাজার কাফের বেচে থাকার চেয়ে ভুলে একজন মুসলমান ধ্বংস হওয়া জঘন্য। (শরহু ফিক্বহিল আকবার-১৯৯)
২. আল্লামা ইবনে নুজাইম রহ. আল-বাহরুর রায়েকে লিখেছেন,
إذا كان في المسالة وجوه توجب التكفير، ووجه واحد يمنع التكفير، فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير
অর্থাৎ কারও মাঝে যদি কাফের হওয়ার অনেকগুলো কারণ পাওয়া যায়, আর কাফের না হওয়ার মাত্র একটি কারণ পাওয়া যায়, তবে মুফতি কাফের না হওয়ার একটি কারণকে প্রাধান্য দিবে এবং কাফের না হওয়ার ফতোয়া দিবে। (আল-বাহরুর রায়েক, খ.৫, পৃ.১৩৪)
৩. কাযি শাওকানী রহ. বলেন,
اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار
অর্থাৎ কোন মুসলমান ইসলাম থেকে বের হয়ে কাফের হওয়ার ব্যাপারে ফয়সালা দিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার কুফুরীটা সূর্য থেকেও স্পষ্ট হয়। (আস সাইলুল জাররার, খ.৪, পৃ.৫৭৮)
অর্থাৎ সূর্যের আলোর চেয়ে কুফুরীটা স্পষ্ট হলে কেবল তাকে কাফের বলা যাবে। নতুবা কাউকে কাফের বলার দু:সাহস দেখাবে না।
৪. ইমাম বাকিল্লানি রহ. বলেন,
ولا يكفر بقول ولا رأي إلا إذا أجمع المسلمون على أنه لايوجد إلا من كافر، ويقوم دليل على ذلك، فيكفر
কারও মতামত বা বক্তব্যের আলোকে কাউকে কাফের বলা যাবে না। তবে মুসলমানরা যে বিষয়ের একমত হয়েছেন এটি কুফুরী ছাড়া কিছুই নয় এবং কুফুরীর সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, কেবল তখনই কাউকে কাফের বলা যাবে। (ফাতাওয়াস সুবকি, খ.২, পৃ.৫৭৮)
শেষ কথা হল, যারা ইবনে মানসুরকে তাকফির করেছেন, তাদের গবেষণা যেমন সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা আছে, একইভাবে যারা কাফের বলেননি, তাদের বক্তব্যও সঠিক হতে পারে। এক্ষেত্রে দলিলের আলোকে যার কাছে যে বিষয়টি শক্তিশালী হবে, সে সেটা গ্রহণ করবে। আমরা কাউকে তাকফির করার যেমন দাওয়াত দেই না, তেমনি যারা তাকফির করেননি তাদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, তাদের আকিদা-বিশ্বাসকে প্রশ্নবিদ্ধ করার প্রচেষ্টাকেও সঠিক মনে করি না। ব্যক্তির বিচারের দায়িত্ব আমাদের নয়। আল্লাহর। তিনি বিচার করবেন। তবে আমরা হুলুল ও ইত্তিহাদের আকিদাকে কখনও সমর্থন করি না। এমনকি এখনও যারা আল্লাহর ক্ষেত্রে হুলুলের আকিদা রাখে আমরা তাদের বিরোধীতা করি।
প্রশ্ন: আপনি কি আমাদেরকে হাল্লাজের আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে আনাল হক্ব বলার দাওয়াত দিচ্ছেন?
উত্তর:
নাউযুবিল্লাহ। আমাদের আলোচনা থেকে কেউ যদি একথা বুঝে থাকে, তাহলে অবশ্যই বলব, তার বুঝ ভুল। কয়েকটি কারণে আমরা হাল্লাজ সম্পর্কে আলোচনা করেছি,
১। মানসুর হাল্লাজের পক্ষে বললেই কিছু লোক ঐ ব্যক্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে শুরু করে। তার আকিদা-বিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন তোলে। অনেকে হাল্লাজের মতো এ ব্যক্তিকে যিন্দিক মনে করে। হাল্লাজের আলোচনা করতে গিয়েই আমরাও এধরণের বহু লোককে পেয়েছি। শুধু হাল্লাজকে কাফের মনে না করার কারণে তাকফির করছে। এমনকি অমুসলিমদের সালাম ব্যবহার করেছে। এসব ভাইদের এই সীমালঙ্ঘন, ভয়ঙ্কর তাকফিরি চিন্তা-চেতনার বাস্তবতা তুলে ধরা হল এই আলোচনার মূল উদ্দেশ্য।
২। হাল্লাজের তাকফিরের বিষয়টি ঐকমত্যপূর্ণ নয়। সব যুগেই আলিমরা এ বিষয়ে মতবিরোধ করেছেন। আহলে সুন্নতের বহু বরেণ্য আলিম তার তাকফিরের বিরোধী ছিলেন।
৩। হাল্লাজের তাকফির কোন অকাট্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে নয়। কিছু খবরে ওয়াহিদ আছে। আর খবরে ওয়াহিদ তাকফিরের জন্য যথেষ্ট নয়। আর এসব বক্তব্য এটা প্রমাণ করে না যে, তিনি আমৃত্যু এসব বিষয়ের উপর অটল-অবিচল ছিলেন। বরং তার তওবার কথা বলেছেন কাজী ইয়াজ রহ:। কিন্তু আলিমরা তার তওবা গ্রহণ না করে তাকে হত্যার ফতোয়া দেয়।
৪। আহলে সুন্নতের সকলেই হুলুল ও ইত্তিহাদের আকিদার বিরোধী। এমনকি হাল্লাজ নিজেও এই কুফুরী আকিদার বিরোধী ছিলেন। নিজে হুলুল ও ইত্তিহাদের আকিদার বিরোধী হওয়ার পরও বহু আলিম হাল্লাজকে তাকফির করেননি। সুতরাং একথা বলা আদৌ উচিৎ নয় যে, হাল্লাজের পক্ষে বললেই সে সর্বেশ্বরবাদী।
৫। হাল্লাজ অনেক বড় ওলী-বুজুর্গ ছিলেন, এসব প্রমাণ করা কিংবা এজাতীয় বিষয়ের প্রতি দাওয়াত দেয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তার বাস্তব অবস্থা আল্লাহ তায়ালা ভালো জানেন।
৬। শরীয়ত বিরোধী কোন বিষয়ে কেউ আমাদের অনুসরণীয় নয়। সুতরাং যেসব সূফী ও মাশায়িখগণ অস্বাভাবিক অবস্থায় আনাল হক বা এজাতীয় কথা বলেছেন তাদেরকে আমরা মা’জুর মনে করি। আমরা কাউকে এই দাওয়াত দেই না যে, এসব সূফী ও মাশায়িখগণের অনুসরণ করতে হবে। ইবাদত করতে করতে সবাইকে ওই স্তরে যেতে হবে। বরং আমরা মানুষকে মৌলিক কুরআন সুন্নাহের আহ্বান করি। এরপরও কারও থেকে অস্বাভাবিক কিছু প্রকাশ পেলে তার অবস্থা যাচাই না করে তাকফির করি না।
৭। তাকফিরের বিষয়ে আহলে সুন্নতের আলিমগণ সীমাহীন সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। কিন্তু বর্তমানে কিছু উগ্রপন্থী দল তাকফিরকে তাদের মূল আদর্শ বানিয়েছে। সাধারণ মানুষকে তারা তাকফিরের দিকে দাওয়াত দিয়ে থাকে। এদের প্রচারণা সত্ত্বেও আমরা আহলে সুন্নতের মূল মানহাজকে সামনে রেখে তাকফিরের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করি।
৮। দলিলের কারণে যারা হাল্লাজকে কাফির বা যিন্দিক বলেছেন, আমরা সেসব আলিমের মতকেও শ্রদ্ধা করি। তবে তাদের মতের চেয়ে কাফির না বলার মতকে আমরা অগ্রগণ্য (রাজেহ) মনে করি।
৯। হাল্লাজের হত্যাকান্ড ছিল রাজনৈতিক। উজীর হামিদের সাথে মনমালিন্যের কারণে সে জোরপূর্বক আলিমদের থেকে হাল্লাজের হত্যার ফতোয়া গ্রহণ করে। এ বিষয়ে ইবনে খল্লিকান রহ: এর বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। এছাড়া হাল্লাজের সম-সাময়িক অনেক মুহাদ্দিস তাকে সমর্থন করেছেন।
১০। হাল্লাজ সম্পর্কে অনেক বর্ণনা সনদের দিক থেকে দুর্বল। এসব বর্ণনার সনদ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন আল্লামা জফর আহমাদ উসমানী রহ: তার সিরাতে মনসুর হাল্লাজে।
বিষয়গুলি স্পষ্ট করার জন্যই এ আলোচনা। কাউকে আনাল হক্ব বলার দাওয়াত দেয়ার জন্য নয়।
হাল্লাজের তাকফিরিদের সবচেয়ে শক্তিশালী দলিল হল, তার কুফুরীর বিষয়ে তৎকালীন আলিমদের ইজমা হয়েছিল। সুতরাং তার ব্যাপারে আর কোন আলোচনার প্রয়োজন নেই।
অথচ আমার মনে হয়, এটি সবচেয়ে দুর্বল আর্গুমেন্ট। ইবনুল আসিরের আল-কামিল, ইবনে খল্লিকানের ওফায়াতুল আ’য়ান, ইবনে কাসীরের আল-বিদায়া-তে তার হত্যা বিষয়ক ফতোয়ার ঘটনা পড়লে যে কেউ বিস্মিত হবে। ইন্নালিল্লাহ।
এক ব্যক্তি চিৎকার করে যাচ্ছে, আমি আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত করি না। আমি আহলে সুন্নতের আকিদার উপর। আমার রক্ত সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করো। আমার রক্ত তোমাদের জন্য হারাম। আল্লাহকে ভয় করো।
আরেকদল লোক উজীর হামিদের চাপাচাপিতে হত্যার ফতোয়ায় স্বাক্ষর করছে। সবশেষে একে নাম দেয়া হল, আলিমদের ইজমা। ইন্নালিল্লাহ। আল্লাহ সবাইকে মাফ করুন।
প্রশ্ন: মনসুর হাল্লাজ তার হত্যার সময়ে বলেছিল, আমি ৩০ দিন পরে ফিরে আসব। মৃত্যুর পর ফিরে আসার বিষয়টি কি হিন্দুদের পুন:জন্মে বিশ্বাস নয়? শুধু একারণেই তো তাকে কাফির বলা উচিৎ। কী বলেন?
উত্তর:
উত্তরের আগে উক্ত বর্ণনাটি দেখে নেয়া যাক। ইবনে হাজার আসকালানী রহ: সহীহ সনদে বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন,
قال أبو عمر بن حيويه لما اخرج حسين الحلاج ليقتل مضيت في جملة الناس ولم أزل أزاحم الناس حتى رأيته فقال لأصحابه لا يهولنكم هذا فإني عائد اليكم بعد ثلاثين يوما ثم قتل
আবু উমার বিন হীওয়াইহ বলেন:
“আল-হুসাইন আল-হাল্লাজকে যখন হত্যার জন্য বের করা হয়। আমি মানুষদের জমায়েতের মাঝে চলতে থাকি এবং তাদের মাঝে ঠেলাঠেলি করতে থাকি। অবশেষে আমি তাকে দেখতে পাই। সে তার সঙ্গীদের বলে: “তোমরা এতে ত্রস্ত হয়ো না! আমি অবশ্যই ত্রিশ দিন পর তোমাদের কাছে ফিরে আসব।” অতঃপর তাকে হত্যা করা হয়।”
(লিসানুল মীযান)
এবার আসুন পুন:জন্ম সম্পর্কে একটু ধারণা নেয়া যাক। হিন্দুদের নিকট পুন:জন্ম হল, জীবের মৃত্যুর পর আত্মা পুনরায় নতুন দেহ ধারণ করে। গীতায় রয়েছে- “যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে সেই রূপে আত্মা জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করে অন্য নতুন শরীর পরিগ্রহ করে”
পুন:জন্মের মূল বিষয়ই হল, আত্মার নতুন দেহ ধারণ করা। হিন্দুরা মনে করে মৃত ব্যক্তির দেহ থেকে আত্মা বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন দেহ ধারণ করে। নতুন দেহ ধারণ করে সে নতুন শিশু হিসেবে আবার পৃথিবীতে আগমন করে। হিন্দুরা মনে করে মানবাত্মা তার ভোগের আকাঙ্খা পূরণের জন্য বার বার পৃথিবীতে আসতে চায়। একারণে পুন:জন্মের মাধ্যমে সে তার এই আকাঙ্খা নিবারণ করে। মোটকথা, হিন্দুদের পুন:জন্ম বলতে নতুন দেহের মাধ্যমে পুনরায় জন্মগ্রহণ বোঝায়।
এবার হাল্লাজের বক্তব্যে আসা যাক। আমার জিজ্ঞাসা হল, আপনি হাল্লাজের বক্তব্যের কোন অংশ থেকে পুন:জন্মের কথা বুঝলেন? পৃথিবীতে ফিরে আসা বলতেই কি পুন:জন্ম বোঝায়? এখানে হাল্লাজের কথায় সমস্যা নাকি আপনার আকিদা-বিশ্বাসে সমস্যা? আপনি কি পৃথিবীতে ফিরে আসা বলতে শুধু পুন:জন্ম বুঝেন? এছাড়া আর কোনভাবে মানুষ পৃথিবীতে আসতে পারে না?
আমাদের এই আলোচনায় আকিদার গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় জড়িত। মৃত ব্যক্তি কি মৃত্যুর পর জীবিত হতে পারে? মৃত্যুর পর জীবিত হয়ে দুনিয়াতে স্বাভাবিকভাবে জীবন-যাপন করতে পারে? অথবা বারজাখে থাকা অবস্থায় স্বাভাবিক আকৃতিতে পৃথিবীতে এসে মানুষের সাথে দেখা সাক্ষাৎ, কথাবার্তা বলতে পারে?
আমাদের কিছু ভাই এগুলোকে কুফুরী মনে করেন। এর মূল কারণ হল, তারা সঠিকভাবে ইসলামী আকিদা-বিশ্বাস জানে না । এরা সম্পূর্ণ বস্তুবাদী চিন্তায় নিমজ্জিত। তথাকথিত কিছু আলিমকেও দেখবেন যারা এজাতীয় বিষয়কে চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই কুফুরী বলে দেয়। আল্লাহ সবাইকে হেদায়াত দান করুন।
এক্ষেত্রে ইসলামি আকিদা হল, জীবন-মৃত্যুর মালিক হলেন আল্লাহ তায়ালা। তিনি যাকে ইচ্ছা জীবন দান করেন, যাকে ইচ্ছা মৃত্যু দেন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতে পারেন। বারজাখ বা কবর জগতের কোন ব্যক্তি আল্লাহর ইচ্ছায় ও ক্ষমতায় জীবিতদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ও কথা বলতে পারে। কেউ যদি বিশ্বাস করে, এগুলো আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতায় হয়, তাহলে এজাতীয় বিশ্বাসে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু কেউ যদি মনে করে, ব্যক্তি নিজস্ব ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্ষমতায় পুনরায় জীবিত হয় বা বারজাখ থেকে দুনিয়াতে আসতে পারে, তাহলে এটি শিরক হবে। সমস্ত মুসলিম এই আকিদা রাখে যে, এজাতীয় অস্বাভাবিক বিষয় আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতায় হয়ে থাকে। এটি ইসলামী আকিদার একটি মৌলিক বিষয়। কারামত বা অস্বাভাবিক ঘটনা আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতায় হয়ে থাকে, এই বিশ্বাস রাখা। যে কোন ধরণের স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক বিষয়ে এই আকিদা রাখা জরুরি।
পুনরায় জীবিত হওয়া বা বারজাখ থেকে দুনিয়াতে আগমনের এই আকিদার সাথে পুন:জন্মের কোন সম্পর্ক নেই। পুন:জন্ম অবশ্যই ইসলাম বিরোধী কুফুরী আকিদা। ইসলামী আকিদার সাথে পুন:জন্মের মৌলিক পার্থক্য হল,
১। মুসলমানরা একই ব্যক্তির দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণে বিশ্নাস করে না।
২। রুহ ভিন্ন দেহে প্রবেশের আকিদা রাখে না। আল্লাহ যাকে যেই দেহ দিয়ে তৈরি করেছেন, সে কিয়ামত পর্যন্ত ঐ দেহের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবে। এক দেহ ছেড়ে অন্য দেহে প্রবেশের আকিদা রাখে না।
৩। হিন্দুরা পুন:জন্মকে আত্মার স্বাভাবিক বিষয় মনে করে। কিন্তু মুসলমানরা বিশ্বাস করে, মৃত ব্যক্তি পুনরায় জীবিত হওয়া বা বারজাখ থেকে পৃথিবীতে আগমনের বিষয়টি আল্লাহর ক্ষমতা ও ইচ্ছাধীন।
শিরক সমাচার শিরোনামেে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।
এবার পুনরায় জীবিত হওয়া বা বারজাখ থেকে দুনিয়াতে আগমনের দলিল আলোচনা করা যাক।
১। আল্লাহর ইচ্ছায় হযরত ইসা আ: মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতেন। বিষয়টি পবিত্র কুরআনে রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,
وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللّهِ وَأُبْرِئُ الأكْمَهَ والأَبْرَصَ وَأُحْيِـي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
আর বণী ইসরাঈলদের জন্যে রসূল হিসেবে তাকে মনোনীত করবেন। তিনি বললেন নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছি নিদর্শনসমূহ নিয়ে। আমি তোমাদের জন্য মাটির দ্বারা পাখীর আকৃতি তৈরী করে দেই। তারপর তাতে যখন ফুৎকার প্রদান করি, তখন তা উড়ন্ত পাখীতে পরিণত হয়ে যায় আল্লাহর হুকুমে। আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং শ্বেত কুষ্ঠ রোগীকে। আর আমি জীবিত করে দেই মৃতকে আল্লাহর হুকুমে। আর আমি তোমাদেরকে বলে দেই যা তোমরা খেয়ে আস এবং যা তোমরা ঘরে রেখে আস। এতে প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। [ সুরা ইমরান ৩:৪৯ ]
ইসা আ: যাদেরকে জীবিত করতেন, তারা পৃথিবীতে বহু দিন বসবাস করেছে। অনেকের সন্তানাদি হয়েছে। ইসা আ: শুধু সদ্য মৃতকে জীবিত করতেন না, বহু বছর আগে মৃত ব্যক্তিকে তিনি জীবিত করতেন। তাফসীর গ্রন্থগুলোতে বিস্তারিত রয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা বিশ্বাস করি, তাদের দুনিয়াতে ফিরে আসার সাথে পুন:জন্মের কোন সম্পর্ক নেই।
.
২। আসহাবে কাহাফের প্রসিদ্ধ ঘটনা পবিত্র কুরআনে রয়েছে।
৩। হযরত উজাইর আ: ও তার গাধার ঘটনা পবিত্র কুরআনে রয়েছে।
৪। হযরত ইব্রাহীম আ: মৃত পাখিদেরকে ডাক দিলে তারা জীবিত হয়ে উড়ে আসে। এটি পবিত্র কুরআনে রয়েছে।
৫। হযরত মুসা আ: এর সময়ে গাভী জবাই করে গোশত স্পর্শ করানোর মাধ্যমে মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে কথা বলে। এটিও কুরআনে রয়েছে।
এসব ঘটনার কোনটির সাথেই পুন:জন্মের কোন সম্পর্ক নেই। বরং যারা আল্লাহর ইচ্ছায় পুনরায় জীবিত হওয়া বা বারজাখ থেকে দুনিয়ায় আগমনকে কুফুরী-শিরকী বা পুন:জন্ম মনে করে, তাদের আকিদা-বিশ্বাস সংশোধন করা জরুরি।
বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ. মৃত্যুর পরে জীবন লাভের উপর পৃথক একটি কিতাব লিখেছেন। এখানে তিনি সনদসহ ৬৪ টি ঘটনা ও বর্ণনা এনেছেন। তার বিখ্যাত কিতাবের নাম হল, মান আশা বা’দাল মাউত (মৃত্যুপর পরে যারা জীবন লাভ করেছে)। এই কিতাব থেকে ইবনে কাসীর রহ, ইমাম বাইহাকি রহ, ইমাম সূয়ূতী রহ, ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী রহ. তাদের কিতাবে বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করেছেন।
আমরা এখানে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করছি।
ইবনে কাসীর রহ. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে আবিদ দুনিয়ার সূত্রে ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ. নিজ সনদে বর্ণনা করেন, রবীয়া ইবনে কুলসুম জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন, উক্ত ব্যক্তির এক বৃদ্ধা প্রতিবেশী ছিল। তিনি অন্ধ ও কিছুটা বধির ছিলেন। হাটা-চলা করতে পারতেন না। তার একটি মাত্র ছেলে ছিল। ছেলেটি তার দেখা-শোনা করতো। ছেলেটি মৃত্যুবরণ করল। আমরা এসে বৃদ্ধাকে বললাম, মুসীবতে আল্লাহর উপর সবর করুন। তিনি বললেন, কী হয়েছে? আমার ছেলে কি মারা গেছে? হে আমার মাওলা, আমার উপর রহম করো। আমার থেকে আমার ছেলেকে নিও না। আমি অন্ধ, বধির ও অচল। আমার দুনিয়াতে আর কেউ নেই। মাওলা, আমার উপর রহম করুন।
আমি বললাম, বৃদ্ধার স্মৃতিভ্রম হয়েছে। এই বলে আমি বাজারে গেলাম। আমি তার কাফনের কাপড় ক্রয় করে নিয়ে এলাম। ফিরে এসে দেখি সে জীবিত হয়ে বসে আছে।
১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ.৬, পৃ.১৫৪।
২.দালাইলুন নুবুওয়া, খ.৬, পৃ.৫০-৫১
ইবনে কাসীর রহ. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে নীচের ঘটনাটি লিখেছেন। ঘটনাটি ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ. মান আশা বা’দাল মাউত কিতাবে উল্লেখ করেছেন,
এক দল লোক ইয়ামান থেকে আল্লাহর পথে বের হল। পথিমধ্যে তাদের একজনের গাধা মৃত্যুবরণ করল। তার সহযাত্রীরা তাকে অন্য গাধার উপর আরোহরণের অনুরোধ জানাল। কিন্তু সে অস্বীকার করল। সে উঠে উজু করল। নামায আদায় করে দুয়া করল,
” হে আল্লাহ, আমি দাফিনা শহর থেকে আপনার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়েছি। আমি একমাত্র আপনার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এসেছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি মৃতকে জীবিত করেন। আপনি কররবাসীকে পুনরায় জীবন দান করবেন। সুতরাং আমাকে কারও অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী করবেন না। আমি আপনার কাছে দুয়া করছি, আপনি আমার গাধা জীবিত করে দিন। এরপর সে গাধার কাছে গেল। গাধাকে উঠার জন্য একটি আঘাত করল। গাধাটি দাড়িয়ে কান ঝাড়তে শুরু করল। সে পুনরায় গাধায় তার সফরের পাথেয় উঠিয়ে যাত্রা করল। কিছুদূর গিয়ে তার সঙ্গীদের সাথে মিলিত হল। তারা তাকে জিজ্ঞাসা করল, এটা কীভাবে হল?
সে বলল, আল্লাহ তায়ালা আমার গাধা জীবিত করে দিয়েছেন। ইমাম শা’বী বলেন, আমি সেই গাধাটি কান্নাসা নামক বাজারে বিক্রি হতে দেখেছি।
সূত্র: আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ.৬, পৃ.১৫৪
২. মান আশা বা’দাল মাউত, বর্ণনা নং ২৯।
৩. দালাইলুন নুবুওয়াহ, খ.৬, পৃ.৪৯
এধরনের একটি ঘটনা ইবনে তাইমিয়া রহ. তার মাজমুয়াতুল ফাতাওয়া-তে লিখেছেন। ইবনে তাইমিয়া রহ. লেখেন,
ورجل من النخع كان له حمار فمات في الطريق فقال له أصحابه : هلم نتوزع متاعك على رحالنا، فقال لهم : أمهلوني هنيئة ، ثم توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين ودعا الله تعالى فأحيا حماره فحمل عليه متعاه .
অর্থ: নাখ’ এর অধিবাসী এক ব্যক্তির একটি গাধা ছিল। যাত্রাপথে গাধাটি মৃত্যুবরণ করে। তার সহযাত্রীরা বলল, আমরা তোমার মাল-সামানা ও পাথেয় আমাদের গাধাগুলোতে বন্টন করে নেই। সে তাদেরকে বলল। আমাকে কিছুক্ষণ সময় দাও। এরপর সে উত্তমরূপে ওজু করল। দু’রাকাত নামায আদায় করে আল্লাহর কাছে দুয়া করল। আল্লাহ তায়ালা তার গাধা জীবিত করে দিলেন। এরপর সে গাধার উপর তার পাথেয় উঠালো।
মাজমুউল ফাতাওয়া, খ.১১, ২৮১।
একই ধরনের একটি ঘটনা ইমাম শা’বী থেকে ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তার আল-ইসাবা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি হযরত উমর রা. এর সময় সংগঠিত হয়। এক্ষেত্রে শাইবান নামক এক ব্যক্তির গাধা মৃত্যুবরণ করলে পরবর্তীতে সে নামায আদায় করে দুয়া করে। আল্লাহ তায়ালা তার গাধাটি জীবিত করে দেন।
[আল-ইসাবা, খ.৩, পৃ.২২৭, বর্ণনা নং ৩৯৮৮]
এছাড়া মে’রাজের রাতে বাইতুল মুকাদ্দাসে নবীগণের সাথে রাসূল স: এর সাক্ষাৎ মূলত: জীবিত ব্যক্তির সাথে বারজাখের লোকদের সাক্ষাতের উদাহরণ। এমনকি বারজাখের রুহের মাধ্যমেও দুনিয়াতে অনেক ঘটনা ঘটা সম্ভব। এ বিষয়ে ইবনুল কাইয়্যিম রহ: তার ‘আর-রুহ’ কিতাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কিতাবটি তিনি ইবনে তাইমিয়া রহ: এর ইন্তিকালের পরে লিখেছেন। ইবনুল কাইয়্যিম রহ: লিখেছেন,
ومما ينبغي أن يعلم أن ما ذكرنا من شأن الروح يختلف بحسب حال الأرواح من القوة والضعف والكبر والصغر، فللروح العظيمة الكبيرة من ذلك ما ليس لمن هو دونها. وأنت ترى أحكام الأرواح في الدنيا كيف تتفاوت أعظم تفاوت بحسب تفارق الأرواح في كيفياتها وقواها وإبطائها وإسراعها والمعاونة لها، فللروح المطلقة من أسر البدن وعلائقه وعوائقه من التصرف والقوة والنفاذ والهمة وسرعة الصعود إلى الله والتعلق بالله ما ليس للروح المهينة المحبوسة في علائق البدن وعوائقه، فإذا كان هذا وهي محبوسة في بدنها فكيف إذا تجردت وفارقته واجتمعت فيها قواها وكانت في أصل شأنها روحا علية زكية كبيرة ذات همة عالية، فهذه لها بعد مفارقة البدن شأن آخر وفعل آخر. وقد تواترت الرؤيا في أصناف بني آدم على فعل الأرواح بعد موتها ما لا تقدر على مثله حال اتصالها بالبدن من هزيمة الجيوش الكثيرة بالواحد والاثنين والعدد القليل ونحو ذلك، وكم قد رئي النبي (صلى الله عليه وسلم) ومعه أبو بكر وعمر في النوم قد هزمت أرواحهم عساكر الكفر والظلم فإذا بجيوشهم مغلوبة مكسورة مع كثرة عَدَدهم وعُدَدهم وضعف المؤمنين وقلتهم
অর্থ: জেনে রাখা উচিৎ যে, পূর্বে আমরা রুহের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। রুহের বিভিন্ন অবস্থা যেমন, শক্তি, ছোট-বড় হওয়া বা অন্যান্য অবস্থার প্রেক্ষিতে রুহের কার্যক্রম ভিন্ন ভিন্ন হয়। তুমি দেখে থাকবে, দুনিয়াতে রুহের অবস্থার কারণে কার্যক্রমের মাঝেও ব্যাপক তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। রুহের শক্তি ও অবস্থার করণে এর গতি, কার্যক্রম, চলাচল ও প্রতিক্রিয়ার মাঝে পার্থক্য দেখা যায়। দেহের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত মর্যাদাসম্পন্ন রুহের ব্যাপক কার্যক্রম, শক্তি, গতিশীলতা, হিম্মত ও আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়ার ক্ষমতা থাকে, যেটা দেহের বন্ধনে আবদ্ধ বন্দী রুহের থাকে না। দেহের বন্ধনে আবদ্ধ থাকার পরও রুহের অনেক অপ্রাকৃতিক কার্যক্রম দেখা যায়, সুতরাং এটি দেহের বন্ধ মুক্ত হয়ে এর পরিপূর্ণ শক্তি ও প্রকৃত বাস্তবতায় যখন ফিরে যায়; পবিত্র ও অধিক শক্তিসম্পন্ন এসব রুহের কার্যক্রম তাহলে কেমন হবে? দেহের বন্ধনে আবদ্ধ রুহের কার্যক্রম থেকে দেহের বন্ধ মুক্ত রুহের কার্যক্রম ভিন্ন।
রুহের কার্যক্রম সম্পর্কে এতো অধিক বর্ণনা রয়েছে যে, এগুলো অস্বীকারের উপায় নেই। মৃত্যুর পরে রুহের কার্যক্রম সম্পর্কে অসংখ্য স্বপ্ন বর্ণিত হয়েছে। মৃত্যুর পরে রুহের মাধ্যমে এমন সব ঘটনা ঘটেছে, যেটি জীবিত থাকা অবস্থায় সম্ভব নয়। যেমন, একজন, দু’জন অথবা সামান্য কিছু লোক বিশাল সেনাবাহিনীকে পরাজিত করা। অসংখ্য লোক রাসূল স. কে স্বপ্নে দেখেছে, তার সাথে হযরত আবু বকর ও হযরত উমর রা. রয়েছেন। তাদের রুহ কাফেরদের সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে দিয়েছে। কাফেরদের পরাজিত ছিন্ন-ভিন্ন সেনাদের লাশ ছড়িয়ে থাকে। অথচ তাদের সংখ্যা মুসলমানদের তুলনায় বহুগুণ বেশি ছিল। মুসলমানরা সংখ্যা ও শক্তিতে ছিল খুবই নগন্য ।
কিতাবুর রুহ, পৃ.১০২-১০৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বয়রুত থেকে প্রকাশিত।
এখানে তিনি রুহের বিভিন্ন কাযর্ক্রমের কথা উল্লেখ করেছেন। রুহ যুদ্ধ করে কাফেরদের পরাজিত করেছে। রাসূল স, হযরত আবু বকর ও হযরত উমর রা. এর কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি স্পষ্ট করেছেন, মৃত্যুর পরে রুহের মাধ্যমে এমন সব কাজ বা ঘটনা ঘটা সম্ভব যা তার জীবিত থাকা অবস্থায় সম্ভব নয়। এর উদাহরণও তিনি দিয়েছেন।
ইবনুল কাইয়্যিম রহ. লিখেছেন,
وما يراه الناس من أرواح الموتى ومجيئهم إليهم من المكان البعيد أمر يعلمه عامة الناس ولا يشكون فيه
অর্থ: “মানুষ অনেক সময় মৃত ব্যক্তির রুহ দেখে থাকে এবং দূর থেকে তাদের রুহ মানুষের কাছে আগমন করার বিষয়টি সাধারণ মানুষও জানে। এ ব্যাপারে তারা সন্দেহ করে না।”
এ বিষয়ে আলোচনা দীর্ঘায়িত করব না। উপরের আলোচনা ও দলিল থেকে একথা বলার কোন সুযোগ থাকে না যে, মৃত ব্যক্তির পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসার পুন:জন্মের সম্পর্ক রয়েছে। একজন মুসলিম পুন:জন্মে বিশ্বাস করা ছাড়াই একথা বিশ্বাস করে যে, ইসা আ: যাদেরকে জীবিত করেছিলেন, তারা বারজাখ থেকে দুনিয়াতে এসেছে। দুনিয়াতে বসবাস করেছে। এটি আল্লাহর ইচ্ছায় ও ক্ষমতায় হয়েছে। এর সাথে পুন:জন্মের কোন সম্পর্ক নেই।
এবার আসি হাল্লাজের উক্ত বক্তব্যের বিশ্নেষণে,
১। হাল্লাজের উক্ত বক্তব্যের সাথে পুন:জন্মের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। কিছু ভাই মূলত: যে কোনভাবে হাল্লাজকে কাফের বলতে চাচ্ছে। এজন্য যে বক্তব্যের সাথে কুফুরীর কোন সম্পর্ক নেই, সেগুলোকে জোরপূর্বক কুফুরী বানানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এটা তো মারাত্মক অন্যায়। যা সে বলেনি, তার নামে তা চাপিয়ে দেয়া তো এক ধরণের অন্যায়। এরপর সেই অপবাদের উপর ভিত্তি করে তাকফির করা আরও বড় অন্যায়। নাউযুবিল্লাহ। আল্লাহ এসব ভাইদের এধরণের অন্যায় মানসিকতা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন।
২। উক্ত বক্তব্যে তার দুনিয়াতে পুনরায় ফিরে আসার কথা রয়েছে। সে হয়ত ইলহামের মাধ্যমে বিষয়টি জেনেছে। এতে শরীয়ত বিরোধী কোন কিছু নেই। আল্লাহ তায়ালা যদি তাকে ৩০ বছর পরে আবার জীবিত করেন, তাহলে এতে আকিদাগত কী সমস্যা? এধরণের ঘটনা অসংখ্য ঘটেছে। পবিত্র কুরআন থেকে আমরা বেশ কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করেছি। আর বাস্তবে যদি তিনি ফিরে নাও আসেন, তাহলেও তো কোন অসুবিধা নেই। তার ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। কারও ইলহাম বা ধারণা ভুল প্রমাণিত হওয়াতে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন অসুবিধা দেখি না। আল্লাহর উপর ভরসা করে অনেক মুসলমান ভবিষ্যতের অনেক কিছুই বলে। তাতে ভুল প্রমাণিত হলে অসুবিধা কী? সূরা কাহাফের ঘটনায় রাসূল স: ধারণা করেছিলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী আসবে। ওহী আসলে তিনি প্রশ্নের উত্তর দিবেন। কিন্তু সময়মত আল্লাহর পক্ষ ওহী আসেনি। এটা তো কোন সমস্যা নয়।
আল্লাহর উপর ভরসা করে, ইলহামের মাধ্যমে কেউ যদি কিছু বলে, আর বাস্তবে যদি সেটা না ঘটে, তাহলে এতে অন্যায়ের কিছু নেই। আর একারণে তার তাকফির করার চিন্তা করাটাও মারাত্মক অন্যায়।
৩। কিছু ভাই আরেকটা জঘন্য কাজ করার চেষ্টা করেছেন। তারা বলতে চেয়েছেন, তার একথাটি যেহেতু কুফুরী, আর সে মৃত্যুর আগে এটি বলেছে; এজন্য সে কাফির অবস্থায় মারা গেছে। নাউযুবিল্লাহ। প্রথমত: একথাটি স্বাভাবিকভাবে কুফুরী হলো কী করে? আপনারা তো পুন:জন্মের আকিদার অপবাদ দিয়ে কুফুরী বানিয়েছেন। হাল্লাজের কথা স্বাভাবিক হলেও আপনারা জোর করে একে কুফুরী বানিয়েছেন। নতুবা মৌলিকভাবে কথাটি কুফুরী নয়। একথাকে পুন:জন্মের সাথে মিলিয়ে যে অন্যায় করেছেন, এজন্য আপনাদের তওবা করা উচিৎ।
৪। এছাড়া হাল্লাজ মৃত্যুর আগে শুধু একথাই বলেনি; তার মৃত্যুর আগের আরও কিছু কথা ইবনে কাসীরে রয়েছে। তাকে যখন বেত্রাঘাত করা হচ্ছিল, তখনও সে প্রত্যেকটা আঘাতে আহাদ আহাদ বলছিল।
ইবনে কাসীর রহ: লিখেছেন,
قال أبو عبد الرحمن: سمعت عبد الله بن علي يقول: سمعت عيسى القصار يقول: آخر كلمة تكلم بها الحلاج حين قتل أن قال: حسب الواحد إفراد الواحد له.
অর্থ: আবু আব্দুর রহমান সুলামী বলেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন আলীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি ইসা আল-কাসসারকে বলতে শুনেছি, হত্যার সময় হাল্লাজ সর্বশেষ যে কথাটি বলেছিল তা হল, এক আল্লাহর আল্লাহর জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে একজন ব্যক্তি তাকে এক হিসেবে মেনে নিবে।
হাল্লাজের সর্বশেষ বক্তব্যটিও তাউহীদ ও এককত্বের সাক্ষী দিচ্ছে। সুতরাং একথা বলা কীভাবে জায়েজ হয় যে, সে কাফির অবস্থায় মারা গেছে? আর ৩০ বছর পর ফিরে আসব, একথাকে শেষ কথা বানিয়ে তাকে তাকফির করা বৈধ হয় কীভাবে? কেউ যদি এই পণ করে বসে যে, হাল্লাজকে যেকোনভাবে তাকফির করতেই হবে, এমনকি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে হলেও, তবে সেই কেবল একটা স্বাভাবিক কথাকে পুন:জন্মের সাথে মিলাতে পারে। আল্লাহ সবাইকে হেদায়াত দান করুন। সব ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অনুসরণের তৌফিক দান করুন।
প্রশ্ন: ‘আমি খোদা’ বলেও যদি হাল্লাজ নির্দোষ হয়, তাহলে দেওয়ানবাগীর কী অপরাধ?
উত্তর:
একজন সাধারণ মানুষ এধরণের প্রশ্ন করতেই পারেন। আলিমদের নিকট বিষয়টা জটিল নয়। সহজ। কারও যদি উসুলুত তাকফির বা তাকফিরের নীতিমালা সম্পর্কে ধারণা থাকে, তাহলে তার কাছে বিষয়টি জটিল মনে হওয়ার কথা নয়।
শুরুতে তাকফিরের কিছু মৌলিক নীতিমালা দেখে নেয়া যাক।
কুরআন সুন্নাহর অকাট্য মূলনীতি ও দলিলের আলোকে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনটা কূফুরী, কোনটা শিরকী সেটা বলা কঠিন কাজ নয়। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কাফের বা মুশরিক বলা খুবই মারাত্মক একটি বিষয়। নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তাকফির করার ক্ষেত্রে কয়েকটি মূলনীতি অবশ্যই মনে রাখতে হবেl
শরীয়তের মূলনীতি হলো, কেউ যদি মুসলিম হয়, তাহলে তাকে মুসলিম মনে করতে হবে। কেউ যদি আদেল বা ন্যায় পরায়ণ হয়, তাহলে যথাসাধ্য তাকে আদেল মনে করতে হবে। মূল বিষয় হলো, মুসলমানকে সাধারণ অবস্থায় মুসলমান বিশ্বাস করা। উদাহরণ হিসেবে ধরুন, একজন লোক নিয়মিত নামাজ পড়ে। রোজা রাখে। আবার সে মাজারেও যায়। এই লোক সম্পর্কে সাধারণ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, সে মুসলিম। যদিও মাজারে গিয়ে তার শিরক করার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু শুধু এই সম্ভাবনার কারণে তাকে মুশরিক মনে করা যাবে না। বরং তাকে তার মূল ইসলামের উপর বিশ্বাস করতে হবে।
এজন্য মূল বিষয় হলো, কেউ মুসলিম হিসেবে পরিচিত হলে তাকে সাধারণ অবস্থায় মুসলিমই মনে করতে হবে। ধারণা কিংবা অনুমানের উপর নির্ভর করে এক্ষেত্রে ফয়সালা করা জায়েজ নয়।
কারও মধ্যে যদি বাস্তবেই শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রমাণিত শিরক বা কুফুরী পাওয়া যায়, এরপরও নির্দিষ্ট এই ব্যক্তিকে সরাসরি কাফের বা মুশরিক বলা যাবে না, যতক্ষণ না তার মধ্যে তাকফীরের শর্তসমূহ পাওয়া যাবে। সাধারণ মানুষ কখনও নির্দিষ্ট কোন মুসলমানকে শুধু তার কাজ বা ধারণার কারণে কাফের বা মুশরিক বলবে না।
কারও মধ্যে শিরক বা কুফুরী পাওয়া গেলেও তাকে বেশ কয়েকটি কারণে সরাসরি কাফের বা মুশরিক বলা যায় না। যেমন,
১. সে এ বিষয়ে অজ্ঞ বা জাহিল হওয়া। সে জানেই না যে, এটা কূফুরী বা শিরকী কাজ।
২. স্বেচ্ছায় কুফুরী বা শিরকীতে লিপ্ত না হওয়া। কূফুরী বি শিরকী কাজে যদি তার ইচ্ছা না পাওয়া যায়, তাহলে তাকে সরাসরি মুশরিক বলা যাবে না। যেমন, কেউ যদি শিরকী কাজের জন্য বাধ্য হয়, তাহলে তাকে মুশরিক ফতোয়া দেয়া যাবে না।
অত্যধিক আনন্দ, ভয় বা পেরেশানির আতিশয্যে কেউ যদি কুফুরী-শিরকী কাজ করে তাহলেও তাকে মুশরিক বলা যায় না। মোটকথা, তার পূর্ণ ইচ্ছা না থাকলে তার উপর কুফুরী-শিরকীর ফতোয়া প্রযোজ্য হবে না।
৩. তাবীল কারী না হওয়া। অর্থাত একটা বিষয় কুফুর বা শিরক, কিন্তু যে এটা করছে তার কিছু সন্দেহের কারণে সে এটাকে শিরক মনে করছে না। অথবা সে শরীয়তের দলিল সঠিকভাবে না বোঝার কারণে শিরককে ইমান মনে করছে, তাহলে এক্ষেত্রেও সরাসরি তাকে কাফের বা মুশরিক বলা যাবে না।
জীবিত কারও মধ্যে যদি শরয়ী দৃষ্টিতে প্রমাণিত শিরক বা কুফুরী পাওয়া যায়, তাহলে তার উপর আগে হুজ্জত কায়েম করতে হবে। অর্থাত তাকে নিশ্চিত করতে হবে যে, এটি কুফুর। তার কোন সন্দেহ, অজ্ঞতা, বা তাবীল থাকলে সেটাও দূর করতে হবে। এগুলো করার পর যদি তার মধ্যে স্বেচ্ছায় ওই শিরকী বা কুফুরী কাজটি পাওয়া যায়, তখন কোন যোগ্য মুফতী তার ব্যাপারে কাফের বা মুশরিক হওয়ার ফয়সালা দিবে।
প্রথমত: হাল্লাজের ক্ষেত্রে তাকফিরের উক্ত মূলনীতিগুলো রক্ষা করা হয়নি। এর বেশ কয়েকটি কারণ আছে,
১। হাল্লাজ সর্বদা এক আল্লাহর ইবাদতের কথা বলেছে। এমনকি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাউহীদের কথা বলেছে। যখন তার বিরুদ্ধে ফতোয়া দেয়া হচ্ছিল তখনও সে দাবী করেছে, সে আহলে সুন্নতের আকিদার উপর।
তাকফিরের সময় তার এই বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য না করা মারাত্মক অন্যায় হয়েছে।
২। আবেগের আতিশয্যে তার মুখ থেকে কিছু কুফুরী শব্দ বের হয়েছে। এখানেও তাকফিরের মূলনীতি রক্ষা করা হয়নি। সুস্থ্য ও স্বাভাবিক অবস্থায় কুফুরী শব্দ বললে তাকফির করা হল শরয়ী বিধান। কিন্তু হাল্লাজের ক্ষেত্রে তার অবস্থা যাচায় করা হয়নি।
৩। যখন তাকফির করা হচ্ছে সে সময় পর্যন্ত ঐ কুফুরীর উপর অটল থাকতে হবে। হাল্লাজের ক্ষেত্রে মারাত্মকভাবে এই মূলনীতি লঙ্ঘন করা হয়েছে। যখন হত্যার ফতোয়া দেয়া হচ্ছিল বা তাকে হত্যা করা হচ্ছিল তখনও সে তাউহীদের কথা বলেছে। এখানে ফতোয়ার সময় কুফুরীর উপর অটল-অবিচলতা পাওয়া যায়নি।
৪। কুফুরীর ফতোয়াটি শুধু কুফুরীর উপর ভিত্তি করে দেয়া হবে। কারও চাপে নয়। কিন্তু হাল্লাজের ফতোয়াটি ছিল উজির হামিদের চাপে। কাজী আবু উমর প্রথমে ফতোয়াটি লিখতে অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু উজির হামিদ নিজে কাগজ-দোয়াত এগিয়ে দেয়। ফতোয়া লিখতে অস্বীকৃতি জানানোর পরও জোর করে ফতোয়া আদায় করাটা শরীয়তে বৈধ নয়। আর এ ফতোয়া কখনও শরয়ী ফতোয়া হিসেবে বিবেচিত হবে না। শরয়ী নীতিমালা উপেক্ষা করা দেয়া এই ফতোয়ার উপর যারা দস্তখত করেছে, তারা মূলত: শরীয়তে অবৈধ ফতোয়ার উপর দস্তখত করেছে। একারণে তাদের দস্তখতগুলোও গ্রহণযোগ্য হবে না।
৫। কারও থেকে কোন কুফুরী প্রকাশ পেলে তার উপর হুজ্জত কায়েম করা হবে। শরীয়তের অকাট্য দলিল প্রমাণ উপস্থিত করে তাকে কুফুরী থেকে ফিরে আসার আহ্বান করা হবে। কুফুরী থেকে ফেরার জন্য এবং এটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য সময় ও সুযোগ দেয়া হবে। হাল্লাজের ক্ষেত্রে এর কোনটিই হয়নি।
এবার আসি দেয়ানবাগীর কুফুরীর বিষয়ে। দেওয়ানবাগীর কুফুরী কথার বিষয়ে তো কারও দ্বিমত নেই। ব্যক্তি দেয়ানবাগীকে কাফির বলার জন্য তাকফিরের নীতিগুলো প্রয়োগ করতে হবে। যদি উপরের নীতিমালার আলোকে সে সুস্থ্য-স্বাভাবিক অবস্থায় কথাগুলো বলে থাকে এবং ঐ কথার উপর অটল থাকে, তাহলে তার উপর হুজ্জত কায়েম করতে হবে। তার বক্তব্যটা যে কুফুরী, কুরআন-সুন্নাহের অকাট্য দলিল দ্বারা তার সামনে কুফুরী তুলে ধরতে হবে। এরপরও যদি সে ঐ কুফুরীর উপর অটল থাকে, তাহলে তাকে সরাসরি কাফির হিসেবে ফয়সালা দেয়া হবে। এই নীতিমালা শুধু দেয়ানবাগী নয়, যে কোন ব্যক্তির জন্যই প্রযোজ্য।
শরীয়তের নীতিমালা ঠিক রেখে কাউকে তাকফির করা হলে, আমরা কখনও এধরণের তাকফিরের বিরোধী নয়। ওমুক কথা বা কাজ কুফুরী বলাটা সহজ। কিন্তু ওই কথা বা কাজের কারণে অমুক ব্যক্তি কাফির, এটা বলা কঠিন। ব্যক্তিকে কাফের বলার আগে তাকফিরের নীতিমালাগুলো সামনে রাখতে হবে। সে দেওয়ানবাগী হোক বা অন্য কেউ হোক। সবার জন্য শরীয়তের উসুল ও নীতিমালা এক।
 আহলে হক্ব বাংলা মিডিয়া সার্ভিস Ahle Haq Media
আহলে হক্ব বাংলা মিডিয়া সার্ভিস Ahle Haq Media