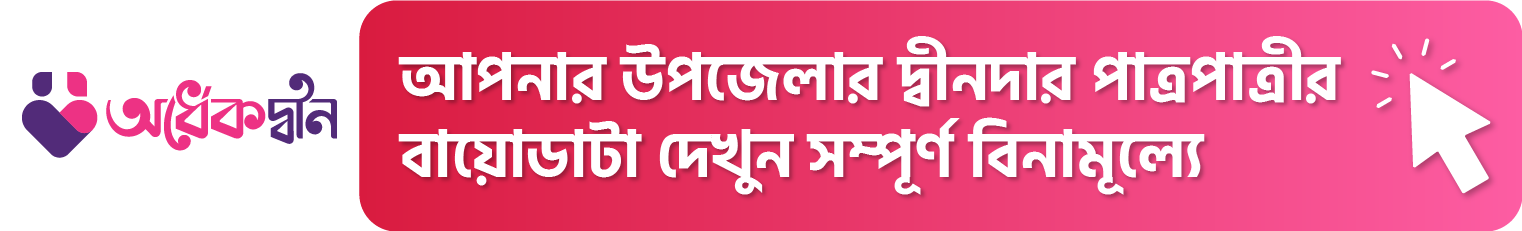মূল: ওয়াজেহ রশিদ হাসানি নদবি
ভাষান্তর: মুফতী আজীজুর রহমান হাসান ফরায়েজী
সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ও বিশ্বজায়নবাদ
উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে হেজাজ, ইরাক ও সিরিয়াকে নিয়ে ইউরোপ যে সাম্রাজ্যবাদী ছক এঁকেছিল, পরবর্তী সময়ে তা আরববিশ্বের রাজনীতির মানচিত্রে বড় সুদূরপ্রভাবী ফল বয়ে আনে। এসব চক্রান্ত বাস্তবায়নে ফ্রান্স ও ব্রিটেন অগ্রভাগে ছিল। পুরো ইউরোপে তখন এ দুটি দেশই ছিল পরাশক্তি; এরপর রাশিয়া, জার্মানি ও আমেরিকাও এই সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার অংশিদার হয়।
পশ্চিমের এই সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিশ্বজায়নবাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তারা মানবতা, রাজনীতি ও ধর্মের নামে ইহুদিদের প্রতি সমবেদনা ও সাহায্যের চেতনা তৈরি করে। ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো নিজেদের দেশে থাকা ইহুদিদের উদারমনে ফিলিস্তিন পাঠাতে থাকে এবং ফিলিস্তিনে ইহুদিদের বসতি স্থাপনের জন্য সবধরনের উপকরণ সরবরাহ করতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) পর ফিলিস্তিন উসমানি খেলাফত থেকে বের হয়ে গেলে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো নিজেদের দূতাবাস ও রাষ্ট্রদূতদের সাহায্যে সেখানে ভূমি ক্রয় করে ইহুদিদের হাতে তুলে দিতে থাকে।
তুর্কি উত্তরাধিকার নিয়ে ভাগ-বাটোয়ারা
প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুর্কিদের অংশগ্রহণ এবং জার্মানিকে সাহায্য করার ফল তাদের ভুগতে হয়েছে। আগে থেকেই তারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৈন্যতার শিকার ছিল। তাদের বলা হতো ইউরোপের ‘রুগ্ন পুরুষ’। তুর্কিদের হাতে বারবার পরাজিত ও লাঞ্ছিত হওয়া ইউরোপের খৃস্টান রাষ্ট্রগুলো এ দুর্বলতার সুযোগে তাদের অধীন অঞ্চলগুলোতে বিদ্রোহ ঘটিয়ে নিজেদের অধীনে নেওয়ার পথ তৈরি করে। তুর্কিদের সম্ভাব্য উত্তরাধিকার বণ্টন করার জন্য একটি প্ল্যান তৈরি হয়, বৃটেনের এক পত্রিকায় তা প্রকাশ পায়। এতে রাশিয়া, ব্রিটেন ও ফ্রান্স শরিক ছিল। এটি ছিল প্রতিশোধ গ্রহণের একটি উত্তম সুযোগ। সুতরাং এটি নিয়ে গোপন আলাপ-আলোচনা, সাক্ষাত ও যুদ্ধ-পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে পরিকল্পনার জন্য চুক্তি করা হলো। যদিও তখনো বিশ্বজায়নিস্ট সংগঠনটির কোথাও স্থিতি ছিল না এবং তাদের পথপ্রদর্শকেরা জার্মানিতে আটকে ছিল, কিন্তু অপরদিকে হাইম ওয়াইজম্যান ব্রিটেনে নিজের প্রভাব ও দৃঢ়তার জোরে এর বিক্ষিপ্ত কাতারকে সঙ্ঘবদ্ধ করে একে একটি শক্তিশালী নেতৃত্ব দান করে।
ব্রিটিশদের চক্রান্ত
ব্রিটেন তিনটি পৃথক, বরং বিপরীতমুখী পথ ও পদক্ষেপ গ্রহণ করে সিরিয়া ও ইরাকে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি ধরে রাখতে সচেষ্ট ছিল। প্রথম পদক্ষেপ ছিল, সে উসমানি খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলনের জন্য হেজাজের গভর্নর শরিফ হুসাইন ইবনে আলির সাথে আলোচনা করে। তাকে প্রতিশ্রুতি দিল যে, উসমানি সাম্রাজ্য বেদখল হয়ে যাওয়ার পর আরব উপদ্বীপ, সিরিয়া ও ইরাকের অধিকাংশ অঞ্চল তার নেতৃত্বে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা অর্জন করবে।
ব্রিটেন এ ক্ষেত্রে অস্পষ্ট ও ধোঁয়াশা পথ অবলম্বন করে। ফলে সিদ্ধান্ত হলো, বিদ্রোহের ঘোষণা এখনই তাৎক্ষণিকভাবে দিয়ে দেওয়া হবে, বাকি ব্যাপারগুলো যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর পরস্পর আলোচনা ও সন্তুষ্টিক্রমে ঠিক করা হবে। সুতরাং এই চুক্তি মোতাবেক শরিফ হুসাইন ১০ জুন ১৯১৬ হেজাজে বিদ্রোহের ঘোষণা দিয়ে দেয় এবং প্রকাশ্যেই ব্রিটেনের মিত্র হয়ে যায়।
সাইকস-পিকু চুক্তি
অন্যদিকে ব্রিটেন ইরাক ও সিরিয়ার ভবিষ্যত নিয়ে ফ্রান্সের সাথে আলোচনা শুরু করে। (পরবর্তী সময়ে এই আলোচনায় রাশিয়াও যুক্ত হয়) মে ১৯১৬ সাইকস-পিকু চুক্তি([1]) হয়। যেখানে সিদ্ধান্ত হয়, ইরাকের অধিকাংশ অংশ, পূর্ব-জর্দান ও ফিলিস্তিনের হাইফা অঞ্চল ব্রিটেন পাবে। লেবানন ও সিরিয়া ফ্রান্সের ভাগে আসবে। ফিলিস্তিনের ওপর যেহেতু বিভিন্ন ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের দৃষ্টি ছিল, তাই একাধিক দাবিদারদের থেকে বাঁচার জন্য সিদ্ধান্ত হয়, এই অঞ্চলটিকে কোনো এক দেশের কাছে না দিয়ে তাকে আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে রেখে দেওয়া হবে।
ব্রিটেন এখানে যে চাল চেলেছে তা হলো, সে ফিলিস্তিনের ভবিষ্যত নিয়ে বিশ্বজায়নিস্ট সংগঠনের সাথে গোপনে আলোচনা করে। সে মূলত আমেরিকায় ইহুদিদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ব্যবহার করে আমেরিকাকে নিজের পক্ষে যুদ্ধে শামিল করতে চাচ্ছিল।
ক্রুসেড যুদ্ধের ভূত এখনো নামেনি মাথা থেকে
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ও উসমানি সাম্রাজ্যের পতনের পর ব্রিটিশ সেনাবাহিনী আরব বাহিনীর সহায়তায় ১১ ডিসেম্বর ১০১৭ কুদস শহরে প্রবেশ করে। ব্রিটিশ বাহিনীর সেনাপতি ছিল জেনারেল এলেনবি আর আরব বাহিনী বাদশা ১ম ফয়সালের নেতৃত্বাধীন ছিল। বিজয়ের পর ব্রিটিশ বাহিনীর সেনাপ্রধান আনন্দ উদযাপন করতে গিয়ে বলল, ক্রুসেডের আজ সমাপ্তি ঘটল! যেন ফিলিস্তিনের ওপর তাদের আক্রমণ ক্রুসেড যুদ্ধের সর্বশেষ পেরেক ছিল। তার এই বাক্য থেকে একটি ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যায়, ইউরোপিয়ানদের মাথায় ক্রুসেড যুদ্ধের ভূত আটশ বছর চলে যাওয়ার পরও ঠিক সেভাবেই সওয়ার হয়ে আছে, যেভাবে একাদশ শতাব্দীতে ছিল। ৯/১১-এর ঘটনার সময় বুশের মুখ থেকে যে বাক্যটি অজান্তে বেরিয়ে গিয়েছিল, তা থেকেও বোঝা যায়—ইউরোপের ওপর ক্রুসেড যুদ্ধের ছায়া এখনো বহাল। এখানে একটি কথা মাথায় রাখা দরকার, ৯ম লুইস ১২৭০ সালে মৃত্যুর সময় যে অসিয়ত লিখিয়ে গিয়েছিল, তার মাঝে এ-ও ছিল—আরবদের মধ্যখানে এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হোক, যা তাদের একতাবদ্ধ হওয়া থেকে বাধা দিয়ে রাখবে এবং তাদের মাঝে গোলযোগ ও বিভেদ সৃষ্টি করে রাখবে।
বালফুর ঘোষণা
১৯১৭ সালে উসমানি খেলাফতের প্রতিনিধির পক্ষ থেকে কুদস শহর জেনারেল এলেনবির হাতে হস্তান্তর করার পূর্বে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বালফুর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে জায়নিস্ট নেতা লর্ড রথচাইল্ডের উদ্দেশ্যে একটি রাজনৈতিক পত্র পাঠান, যা ‘বালফুর ঘোষণা’ নামে প্রসিদ্ধ। সেই পত্রে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, মহামান্য ব্রিটিশ রাজার সরকার (His Majesty) পূর্ণ সহানুভূতি ও দায়িত্বশীলতার সাথে ফিলিস্তিন ভূমিতে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ভাবছে। তার রাষ্ট্র এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সবধরনের সম্ভাব্য চেষ্টা করবে।
প্রকাশ থাকে যে, এই ঘোষণার সময় ফিলিস্তিন ব্রিটেনের অধীন ছিল না।
ব্রিটেনের দখলদারি
সেপ্টেম্বর ১৯১৮ ব্রিটিশ সেনাবাহিনী উত্তর ফিলিস্তিন দখল করে নেয়। এরপর অক্টোবর পর্যন্ত তারা পূর্ব-জর্দান, সিরিয়া ও লেবাননও দখল করে ফেলে। তখন থেকেই ব্রিটেন নিয়মতান্ত্রিকভাবে ফিলিস্তিন ভূমিকে ইহুদিদের হাতে তুলে দেওয়া শুরু করে। ব্রিটেন ফ্রান্সকেও এ কথার ওপর রাজি করিয়ে ফেলে যে, সাইকস-পিকু চুক্তিতে ফিলিস্তিনকে আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে রাখার যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, সে যেন তা থেকে সরে আসে।
১০ জানুয়ারি ১৯২০ ব্রিটেনের শক্তিশালী মিত্রগুলোর ঐকমত্যে ফিলিস্তিনকে ব্রিটিশ ম্যান্ডেটে দিয়ে দেওয়া হয়। এরপর সেপ্টেম্বর ১৯২২ জাতিসঙ্ঘও এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন দেয়।
ব্রিটেনের চরিত্র
বালফুর ঘোষণাকে বাস্তবায়ন করার জন্য ব্রিটেন ফিলিস্তিনে তাদের ত্রিশ বছরের শাসনামলে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের হিজরত ও আগমনের জন্য সব দরজা খুলে দিয়েছে এবং ইহুদি মুহাজিরদের জন্য সবধরনের সম্ভাব্য সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। ফলে ১৯১৫ সালে যে ইহুদিদের সংখ্যা আট শতাংশ অর্থাৎ পঞ্চান্ন হাজার ছিল, সেটা ১৯৪৮ পর্যন্ত এসে একত্রিশ শতাংশ অর্থাৎ ছয়শ পঞ্চাশ হাজার হয়ে গেছে। ব্রিটেন তার শাসনামলে ফিলিস্তিনিদের জীবনযাত্রা সংকীর্ণ করে দেয়। তাদের জন্য জীবিকার পথও বন্ধ করে দেয়। ফেতনা-ফাসাদ উস্কে দেয়। বংশীয় ও দলীয় মতভেদগুলো বাড়িয়ে দেয় এবং ফিলিস্তিনিদের নিজেদের মধ্যে ব্যস্ত রাখার জন্য ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ও প্রচেষ্টা করে। হাইকমিশনকে—যার মাঝে অধিকাংশই ছিল ইহুদি—লাগামহীন ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হয়।
পিল কমিশন
ফিলিস্তিনের মহাবিপ্লবের (১৯৩৬-১৯৩৯) পর ব্রিটেন পিল কমিশন গঠন করে; যে কমিশন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে ফিলিস্তিনকে ইহুদি ও আরবীয় দুটি রাষ্ট্রে ভাগ করে দিতে এবং কুদস ও হাইফা শহরকে ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের অধীনে বহাল রাখার ব্যাপারে সুপারিশ করে, কিন্তু ইহুদি ও আরব—উভয়ে এই প্রস্তাবনা মেনে নিতে অস্বীকার করে দেয়।
ইহুদিদের অপপ্রচার ও মার্কিন হস্তক্ষেপের সূচনা
ইহুদিরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরিস্থিতি থেকে অনেক বেশি ফায়দা কামিয়েছে। তারা পৃথিবীবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভ করার জন্য জার্মানিতে যা ঘটেছে, সেগুলোকে রঙচঙ চড়িয়ে বৃহদাকারে প্রচার করে এবং এ বিষয়ে ব্যাপক অপপ্রচার চালায় যে, তাদের জন্য পৃথিবীতে কোথাও শান্তির জায়গা নেই। তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়—ফিলিস্তিনে তাদের জন্য জাতীয় বাসভূমি প্রতিষ্ঠা। তারা এমন অপপ্রচারও চালায় যে, ইহুদিদের সাহায্য করা খৃস্টানদের ধর্মীয় কর্তব্য ও মানবিক সহানুভূতির দাবি। পাশাপাশি তারা উদীয়মান আন্তর্জাতিক শক্তি আমেরিকাকে নিজেদের পক্ষে নেওয়ার প্রচেষ্টাও জোরদার করে। বিশেষ করে ১৯৪২ সালে বিল্টমোর (Biltemore) চুক্তির পর তারা তাদের নিশানা পুরোপুরি আমেরিকার দিকে ঘুরিয়ে নেয় এবং ব্রিটেনের হোয়াইট পেপারকে (মে ১৯৩৯) প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে ডেমোক্রেট ও রিপাবলিকান—উভয় পার্টির সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করে। সুতরাং ৩১ আগস্ট ১৯৪৫ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ইটলির কাছে আবেদন করে, যেন এক লাখ ইহুদিকে ফিলিস্তিনে পাঠানো হয়।
ইঙ্গ-মার্কিন কমিটি
তৎকালীন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্যাভেন ১৪ নভেম্বর ১৯৪৫ একটি বিবৃতি প্রকাশ করে, যেখানে ফিলিস্তিন-সমস্যা সমাধানের জন্য একটি ইঙ্গ-মার্কিন কমিটি গঠন ও তার প্রস্তাবনাগুলো বাস্তবায়নের আহ্বান করা হয়েছিল। এভাবে আমেরিকা সরাসরি ফিলিস্তিন-ইস্যুতে ঢুকে পড়ে। এই কমিটি ১৯৪৬ সালে ফিলিস্তিনের জমিগুলো হস্তান্তর ও ইহুদিদের হাতে সেগুলো বিক্রয় করার স্বাধীনতা দিয়ে এক লাখ ইহুদিকে ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপনের সুপারিশ করে। ১৯৩৯-১৯৪৫ সালে বিরানব্বই হাজার ইহুদি ফিলিস্তিনে হিজরত করে। এরপর ১৯৪৬-১৯৪৮ সালে একষট্টি হাজার ইহুদি বিভিন্ন দেশ থেকে হিজরত করে ফিলিস্তিনে এসে বসতি স্থাপন করে, দুইশ সত্তর হাজার এক্টর জমি লাভ করে এবং তেহাত্তরটি নতুন কলোনী গড়ে তুলে।
ইহুদিদের জন্য জাতীয় বাসভূমি প্রতিষ্ঠা
এপ্রিল ১৯৪৭ ইহুদিদের জন্য জাতীয় বাসভূমি প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার পূর্ণ করার পর ব্রিটেন আরব-ইহুদি ঝগড়াকে জাতিসঙ্ঘের আদালতে পাঠিয়ে দিয়ে নিজের আঁচল ঝেড়ে ফেলে এবং ফিলিস্তিনের ওপর ত্রিশ বছর পর্যন্ত শাসন চালানো সত্ত্বেও আরবদের ব্যাপারে নিজের দায়িত্ব থেকে চোখ বন্ধ করে ফেলে। অথচ ম্যান্ডেটের দফা অনুসারে তার এ বিষয়ে ভাবা উচিত ছিল যে, তার নিয়ন্ত্রণাধীন ফিলিস্তিনের প্রকৃত বাসিন্দাদের যেন কোনো ধরনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষতি না হয়।
ফিলিস্তিন-সমস্যা সমাধানের নিষ্ফল প্রচেষ্টা
মে ১৯৪৭ জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ UNSCOP (U.N Special committee on palestine) নামে একটি কমিটি বিশেষ করে ফিলিস্তিন-সমস্যা সমাধানের জন্য গঠন করে, যেন এই কমিটি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে দ্রুততম সময়ে তাদের রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্ট ৩১ আগস্ট প্রস্তুত হয়। যার প্রহসনমূলক প্রস্তাবনাগুলো ছিল নিম্নরূপ—
- ফিলিস্তিনে ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের সমাপ্তি টেনে দেওয়া হবে।
- ফিলিস্তিনকে আরব ও ইহুদি—দুই স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্রের মাঝে ভাগ করে দিয়ে কুদস শহরকে সম্মিলিত অধিকারে দিয়ে দেওয়া হবে।
এরপর আরববিশ্ব সূফর কনফারেন্স (৬ ডিসেম্বর ১৯৪৭) ও আলিয়া কনফারেন্স (৭-১৫ অক্টোবর ১৯৪৭) থেকে আন্তর্জাতিক কমিটির সুপারিশগুলোর বিরোধিতা এবং লোকবল ও অস্ত্র দিয়ে ফিলিস্তিনিদের সহযোগিতা এবং সেনাবাহিনীকে সুশৃঙ্খলকরণ ও সেনা আগ্রাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।
ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা
২৯ নভেম্বর ১৯৪৮ জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ তার ইতিহাসের সবচেয়ে কালো রেজুলেশন নম্বর ১৮১ জারি করে—যা আমেরিকার চাপ আর রাশিয়ার জোরদার সহযোগিতার ফলে দুই তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে মঞ্জুর করে নেওয়া হয়—যেখানে ফিলিস্তিনকে দুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্রে বিভক্ত করে দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। সাধারণ পরিষদের এই শিষ্টাচারবহির্ভূত ও মানবতাবিরোধী সিদ্ধান্তের কারণে ইসরায়েল ফিলিস্তিনের পঞ্চান্ন শতাংশ ভাগ পেয়ে যায়। এর আগে তারা ১১ শতাংশের বেশির মালিক ছিল না।
বিভাজনের এই সিদ্ধান্ত ফিলিস্তিনের প্রত্যেক আরবিভাষী ও মুসলিমের জন্য একটি বজ্রসদৃশ ও অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠার মতো দুর্ঘটনা ছিল, যা আলোচনা-সমঝোতার মাধ্যমে ফিলিস্তিন-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সব আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করে দেয়। সমগ্র মুসলিমবিশ্বে এর কঠিন প্রতিবাদ হয়। প্রত্যেক দেশের জনসাধারণ নিজ নিজ রাষ্ট্রের কাছে এই অন্যায় বিভাজন থামানোর জন্য দাবি জানায় এবং ফিলিস্তিনকে ইহুদিদের কবল থেকে স্বাধীন করার জন্য সশস্ত্র অভিযান চালানোরও আওয়াজ তোলা হয়, কিন্তু সবই ছিল নিষ্ফল ও বৃথা।
১৪ মে ১৯৪৮ ব্রিটেনের সশস্ত্র সেনাবাহিনী ফিলিস্তিন ছেড়ে যাওয়ার পর মধ্যরাতে ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের সমাপ্তি হয়ে যায়। আর সেদিনই ইহুদিরাষ্ট্রের কওমি কাউন্সিল তেলআবিবে ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়ে দেয়।
ফিলিস্তিনের গণহত্যা ও মুসলিমবিশ্বের অবস্থান
ফিলিস্তিনিরা অক্টোবর ১৯৪৮ গাজার কনফারেন্সে ফিলিস্তিনের সাধারণ সরকার গঠনের ঘোষণা দিয়ে দেয়। কিন্তু সেসব আরবরাষ্ট্রগুলো—যাদের কাছে শক্তি ছিল, সেনাবাহিনী ছিল—ফিলিস্তিন ভূমিতে তাদের কোনো প্রভাবই ফেলতে পারেনি। কারণ, তারা ইউরোপিয়ান রাষ্ট্রগুলোর উপদেষ্টা ও কমান্ডারদের প্রভাবাধীন ছিল। তারা ইহুদিদের সাথে সরাসরি বিরোধিতায় লিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে আরব যোদ্ধাদের অগ্রযাত্রা থামানোর কাজ করেছে। এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধবিরতি করিয়ে দেওয়া হয় এবং ইহুদি দখলাদারত্ব আইনি স্বীকৃতি পেয়ে যায়। বরং আলহাজ আমিন হুসাইনিকে মিশরীয় সেনাদের চাপে পড়ে গাজা ছেড়ে দিতে হয় এবং ইখওয়ানুল মুসলিমিনের যেসকল স্বেচ্ছাসেবক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের গ্রেফতারি ও বন্দিত্বের কষ্ট সইতে হয়। আর ফিলিস্তিনি জনসাধারণকে শিকার হতে হয় বাস্তুহারা ও রক্তক্ষয়ী জুলুমের। যার মাঝে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ৯ এপ্রিল ১৯৪৮ সালের ‘দির ইয়াসিন’-এ ফিলিস্তিনিদের ওপর চালানো গণহত্যা, যেখানে দুইশ আটান্নজন ফিলিস্তিনি শহিদ হয় এবং প্রায় ৬০% ফিলিস্তিনিকে নিজের দেশ থেকে হিজরত করে সেসব অঞ্চলে আশ্রয় নিতে হয়, যেখানে ইহুদিদের রাজত্ব ছিল। এছাড়া প্রায় ত্রিশ হাজার লোক ফিলিস্তিনের অধিকৃত অঞ্চলে আশ্রয়গ্রহণ করে। ১৯৫২ সালে মিশরে জামাল আবদুন নাসেরের নেতৃত্বে বিপ্লব এরই ভিত্তিতে হয়েছিল যে, ফিলিস্তিনে আমাদের লড়াই করতে দেওয়া হয়নি; ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা আমাদের প্রথম লক্ষ্য।
মিশরের ওপর ব্রিটেন-ফ্রান্স-ইসরায়েলের হামলা
১৯৫৫ সালে সুয়েজ খাল জাতিয়করণের ফলে পশ্চিমাবিশ্ব যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে তা হলো, ব্রিটেন-ফ্রান্স-ইসরায়েল মিলে ১৯৫৬ সালে মিশর আক্রমণ করে। কিন্তু এই ত্রিদেশীয় হামলা ব্যর্থ হয়। কারণ, আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের সমর্থন করেনি। ফলে এই পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোকে ব্যর্থতার মুখে পড়তে হয় এবং ২৩ ডিসেম্বর ১৯৫৬ ব্রিটিশ ও ফরাসি সৈন্যরা মিশর ছেড়ে চলে যায়; সুয়েজ যুদ্ধ সমাপ্ত হয়ে যায়। মিশর নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করে নেয় এবং ইসরায়েলের কাছ থেকে নিজেদের অঞ্চল ফেরত নিয়ে নেয়, কিন্তু তারা ইসরায়েলকে আকাবা উপসাগরে আটকাতে পারেনি।
ব্রিটেনের অবস্থান
এই সাম্রাজ্যবাদী হামলার পর থেকে ইসরায়েলের ব্যাপারে ব্রিটেনের অবস্থান পুরোপুরিভাবে সমর্থনসূচক হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে এটি ব্রিটেনের আমেরিকা-দাসত্বেরই একটি প্রকাশ ছিল। ব্রিটেনের এই সমর্থন ১৯৬৭ পর্যন্ত বহাল ছিল, বরং ব্রিটেন ইসরায়েলকে রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে সমর্থন দিতে থাকে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিজেদের অবস্থান দুর্বল হয়ে যাওয়ার পর ফিলিস্তিনে শান্তিপ্রতিষ্ঠার (১৯৭৩-১৯৯৪) আমেরিকান ফর্মূলাকে সমর্থন দিতে থাকে।
১৯৬৭ সালে যুদ্ধ
জুন ১৯৬৭ মিশর আকাবা উপসাগরের তিরান প্রণালি বন্ধ করে দেয় এবং ইসরায়েলি জাহাজগুলোর যাতায়াতের অনুমোদন বাতিল করে। জাতিসঙ্ঘের শান্তিরক্ষাবাহিনীকে মিশর পিছু হটতে বাধ্য করে, কিন্তু ৫ জুন সকালে ইসরায়েল বিমানবাহিনী মিশর, জর্দান ও সিরিয়ার বিমানবন্দরগুলোকে মিসাইল দিয়ে উড়িয়ে দেয় এবং ছয় দিনের মধ্যে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। আরব রাষ্ট্রগুলোকে এক নতুন বিপদের মুখোমুখি হতে হয়। জায়নিস্টরা ফিলিস্তিনের অবশিষ্ট অংশ (জর্দানের পশ্চিম তীরে ৫,৮৭৮ কিলোমিটার, গাজা উপত্যকার ৩৬৩ কিলোমিটার, সিনাই মরুভূমির ৬১,১৯৮ কিলোমিটার কিলোমিটার ও সিরিয়ার গোলান মালভূমির ১,১৫০ কিলোমিটার) দখল করে নেয়।
এই যুদ্ধের ফল যা দাঁড়ায় তা হচ্ছে, তিনশ ত্রিশ হাজার অন্যান্য ফিলিস্তিনিকে দেশ ছাড়তে হয়েছে। আরব-রাষ্ট্রপ্রধানদের ওপর থেকে মানুষের আস্থা উঠে যায় এবং স্বাধীন ফিলিস্তিনের জন্য জাতীয় বিভিন্ন আন্দোলন অস্তিত্ব লাভ করে।
আরব রাষ্ট্রগুলোর ব্যর্থতা ও তার ফলাফল
আরব রাষ্ট্রগুলোর ব্যর্থতার পর ফিলিস্তিনিরা দুঃসাহসিক ও প্রাণপন তৎপড়তা শুরু করে এবং জায়নিস্টদের প্রাণনাশ ও অর্থনৈতিক ক্ষতি করতে শুরু করে, কিন্তু জর্দান ও ফিলিস্তিন বাহিনীর মধ্যকার বিরোধ ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলনগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং তাদের শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে ভেঙে দেয়। এছাড়া কিছু আরব রাষ্ট্রও ফিলিস্তিনিদের জন্য জটিলতা তৈরি করে। স্বয়ং মুসলিমদের মধ্যে হওয়া বিভিন্ন যুদ্ধ—যেমন, ১৯৮০-১৯৮৮ সালের ইরাক-ইরান যুদ্ধ—ফিলিস্তিন-ইস্যুর ওপর বড়ধরনের প্রভাব ফেলে। একইভাবে ১৯৭৭-১৯৮২ সালে মিশরকর্তৃক যুদ্ধবিরতি-চুক্তিতে শরিক হওয়ার কারণে আরববিশ্ব ও মিশরের মধ্যে লড়াই বাধার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যায়। এভাবেই ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ সংস্থাগুলো একা হয়ে যায়। আরব রাষ্ট্রগুলো তাদের কোনোধরনের সাহায্য করেনি; অথচ ইসরায়েল পরাশক্তিগুলোর পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা পাচ্ছিল।
১৯৭৩ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ
৬ অক্টোবর ১৯৭৩ আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের সূচনা হয়, যাতে জায়নিস্টদের বিরুদ্ধে মিশর বড় সাফল্য অর্জন করে। মিশর ও সিরিয়া উভয়ে তাতে শরিক ছিল এবং মিশরীয়রা সুয়েজ খালের পূর্বাংশ দখল করে নেয়; বরং সিনাই উপদ্বীপ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অক্টোবরের এই যুদ্ধকে আরবদের বিজয় মনে করা হয়, কিন্তু মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত এই যুদ্ধকে মিশরের স্বার্থে ব্যবহার করে। আর তা এভাবে যে, আনোয়ার সাদাত নভেম্বর ১৯৭৭ ইসরায়েল সফর করে এবং সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ ক্যাম্প ডেভিড চুক্তিতে সাক্ষর করে, যার মাধ্যমে মিশরের সাথে ইসরায়েলের সন্ধি হয়ে যায় এবং উভয়ের মধ্যকার সব বিভেদ মিটে যায়। মিশর সিনাই উপদ্বীপ ফেরত নিয়ে নেয়। এভাবে ফিলিস্তিনিরা স্বাধীন ফিলিস্তিনের একজন তৎপর ও শক্তিশালী স্তম্ভ মিশরকে হারিয়ে ফেলে। ফলে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে যেকোনো ধরনের সামরিক কার্যক্রমের সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়।
আফগানিস্তানের ওপর রাশিয়ার হামলা ও তার প্রভাব
আফগানিস্তানের ওপর রাশিয়ার হামলা ও দখলের (১৯৭৯) পর মুসলিমবিশ্বের প্রধান দৃষ্টি ফিলিস্তিন থেকে সরে গিয়ে আফগানিস্তানের প্রতি নিবদ্ধ হয়। এই জিহাদে পূর্ণ সাহায্য করেছে আরববিশ্বের বিভিন্ন উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলো। এরপর আরববিশ্বে একের পর এক বিপ্লব হতেই থাকে বা করানো হতে থাকে, ফলে আরব-রাষ্ট্রগুলোর মনোযোগ ফিলিস্তিন-ইস্যু থেকে সরে যায় আর ফিলিস্তিন একা হয়ে পড়ে।
আরব রাষ্ট্রগুলোর শত্রুতামূলক আচরণ
অপরদিকে আরব রাষ্ট্রগুলোতে যেসকল আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন চেতনাশীল মুসলমান ফিলিস্তিন-ইস্যুতে সাহায্য করার চেষ্টা করেছে, তাদের বিভিন্নভাবে কষ্ট দেওয়া দেয়া হয়েছে, জেলে ভরা হয়েছে, ইসলামপ্রীতির সব উপকরণ পিষে ফেলা হয়েছে। বিশেষ করে সিরিয়া, জর্দান ও মিশরে ইখওয়ানিদের—যারা ফিলিস্তিনিদের সাহায্য-সহযোগিতা করছিল—জেলের গরাদের পেছনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এসব কারণে ফিলিস্তিনিরা সবধরনের সাহায্য-সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, যেখানে ইসরায়েল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর সহায়তা ও আরবদের গোপন চুক্তির সাহায্যে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি ও ফিলিস্তিনিদের ওপর নির্যাতনের পাহাড় চাপাতে থাকে।
ইনতেফাদা আন্দোলন
৯ ডিসেম্বর ১৯৮৭ ইনতেফাদা আন্দোলন শুরু হয়, ১৯৯৩ পর্যন্ত এই আন্দোলন পূর্ণ শক্তি নিয়ে সরগরম থাকে। এই ইনতেফাদার মাধ্যমেই হামাসের আত্মপ্রকাশ হয়, যারা তাদের প্রতিষ্ঠাতা ও ইনতেফাদার প্রাণপুরুষ শায়খ আহমদ ইয়াসিন শহিদের নেতৃত্বে অনেক বেশি জনসমর্থন লাভ করে। বর্তমানে এককভাবে হামাসই ইসরায়েলি নৃশংসতার বিরোধিতা করে যাচ্ছে। আল-ফাতাহ—যা প্রতিরোধ-আন্দোলনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—বিভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে তারাও ইসরায়েলের সহযোগী হয়ে যায়। অধিকাংশ আরব রাষ্ট্রগুলোর সমর্থন তার পক্ষেই রয়েছে। গাজা অবরোধ ও ইসরায়েলি হামলা চলাকালীন এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে সামনে চলে আসে যে, মুসলিমবিশ্ব ফিলিস্তিন-ইস্যু থেকে আলাদা হয়ে গেছে। অনেকে এটিকে কেবলই আরবদের ইস্যু বানিয়ে ফেলে, ফলে ফিলিস্তিন মুসলিমবিশ্বের সমর্থন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।
১৯৮০ পরবর্তী অবস্থা
১৯৮০ সালের শেষদিকে ও ১৯৯০ সালের শুরুদিকে আরববিশ্ব ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এমন কিছু পরিবর্তন আসে, যার ফলে ফিলিস্তিন ও আরব-অবস্থানে দুর্বলতা তৈরি হয়ে যায়। বিশেষ করে ২ আগস্ট ১৯৯০ কুয়েতের ওপর ইরাকের আক্রমণে আরবদের শক্তি এলোমেলো হয়ে পড়ে, ফলে স্বয়ং আরব রাষ্ট্রগুলোতে বৈরী পরিবেশ তৈরি হয়ে যায়। ইরাকের সামরিক শক্তি, আরবদের ভাণ্ডার ও আমদানি হ্রাস পায়। ইরাকের হামলা ও তার ফলে সৃষ্ট উপসাগরীয় যুদ্ধের ফলগুলো ফিলিস্তিন-ইস্যুতে আরও বেদনাদায়ক প্রমাণিত হয় এবং কুয়েতের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।
সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন
এ সময় আমেরিকাও সোভিয়ত ইউনিয়নের পতন ও বিশেষ করে ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের পর পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শক্তিরূপে আভির্ভূত হয়। ফিলিস্তিন ভূমিতে ইহুদিদের প্রভাব-প্রতিপত্তির ফলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে থাকে। অবশেষে ১৯৯১ সালে মাদ্রিদের আরব-ইসরায়েল কনফারেন্সে আমেরিকা আরব রাষ্ট্রগুলোকে টেনে নিতে সফল হয়ে যায়, যারপর থেকে সরাসরি আরব-ইসরায়েল আলোচনার ধারার সূচনা হয়।
অসলো চুক্তি
দুই বছর পর উভয়পক্ষের মাঝে অসলো চুক্তির ঘোষণা করা হয়। ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন, ইয়াসির আরাফাত ও আইজ্যাক রবিনের উপস্থিতিতে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বাক্ষর গ্রহণ হয়। ফিলিস্তিনিদের পক্ষ থেকে মাহমুদ আব্বাস আর ইসরায়েলের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিমন পেরেজ এতে স্বাক্ষর করেন। সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করেন রাশিয়া ও আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এরপর আরও বিভিন্ন চুক্তি হয়, যেখানে মৌলিকভাবে জায়নবাদী স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। কিন্তু ফিলিস্তিন রাষ্ট্র—যা অসলো চুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল—সংবেদনশীল ইস্যুগুলোতে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত পর্যন্ত পৌঁছতে ব্যর্থ হয়।
মুসলিমবিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি
ফিলিস্তিন-ইস্যুতে ওপরিউক্ত ইতিহাসগুলোর পর্যালোচনা থেকে প্রমাণিত হয়, ইসরায়েল প্রতিষ্ঠা ও তা সুদূঢ় হওয়ার পেছনে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ, আরবদের বিভক্তি, আরব রাষ্ট্রপ্রধানদের অবহেলা ও যথাসময়ে ফিলিস্তিন রক্ষার পদক্ষেপ গ্রহণ না করা এবং ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলনগুলোকে সাহায্য ও উপকরণ সরবরাহ না করার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। মিশর ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির পর থেকে ইসরায়েলের সাথে সমঝোতার আচরণ করে যাচ্ছে এবং প্রতিরোধ আন্দোলনকারীদের বিরোধিতা, বরং তাদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি অবস্থানকে সমর্থন যুগিয়ে যাচ্ছে। যেমন, গাজা অবরোধের সময় তাদের আচরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। আরববিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলো—যারা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারত—এমনসব সমস্যায় জড়িয়ে আছে, যার ফলে তারা নিজেদের শান্তি ও নিরাপত্তা চিন্তায়ই অস্থির। আরবদের বিদ্রোহ ও উসমানি খেলাফতের পতনের পর আরবদের সাথে তুর্কিদের সম্পর্ক সবসময় অসহযোগিতামূলক ছিল, বিপরীতে ইসরায়েলের সাথে ছিল ভালো সম্পর্ক। বর্তমান ইসলামপ্রিয় সরকার আরবদের সাথে কিছুটা সহানুভূতিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, কিন্তু তারা ন্যাটোর সদস্য ও ইউরোপিয়ান কমিউনিটিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টার কারণে গুরুত্বপূর্ণ কোনো ভূমিকা রাখতে পারবে না। পাকিস্তান, ইরান, সুদান যুদ্ধাবস্থায় আছে। আর কিছু কিছু দেশের তো ইসরায়েলের সাথে গোপন সমঝোতাই আছে।
ইসরায়েলের জন্য ইউরোপিয়ানদের সাহায্য
অন্যদিকে পুরো ইউরোপ প্রকাশ্যে ইসরায়েলকে সমর্থন যুগিয়ে যাচ্ছে। যার প্রকাশ ঘটেছে ১৯১৮ সালে। এরপর ২০০৯ সালে ইসরায়েলকর্তৃক গাজা অবরোধ ও আকাশপথে আক্রমণের সময় এই সমর্থন প্রকাশ্যেই হয়েছে। এরচেয়েও আক্ষেপের বিষয় হলো, হামাসের সাহায্য করার পরিবর্তে কিছু কিছু দেশ তাদের বিরোধিতার পথ বেছে নিয়েছে এবং ইসরায়েলকে গোপনে সাহায্য করেছে। এই ইস্যুটি পুরোপুরি আরবদের ইস্যুই হতে পারেনি, মুসলিমবিশ্বের ইস্যু হওয়া তো আরও দূরের ব্যাপার।
ইউরোপিয়ানদের ইসরায়েলের সহযোগিতা ও সাহায্যের আন্দাজ করা যায় নিম্নোল্লেখিত ‘বালফুর চুক্তি’র নথি থেকে। যেখানে বলা হয়েছে, জায়নিস্টদের ব্যাপারে চারটি রাষ্ট্র নিজেদের অঙ্গীকার খুবই চমৎকারভাবে পুরা করেছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, জায়নিস্টরা—চাই সঠিক হোক বা ভুল, ভালো হোক বা খারাপ—আমাদের সভ্যতা, আমাদের বর্তমান প্রয়োজন ও ভবিষ্যত প্রত্যাশা পূরণে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তারা আরব রাষ্ট্রগুলোতে বসবাস করা ৭০০ হাজার আরবের প্রত্যাশার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি গুরুত্বের দাবিদার।
বাদশা আবদুল আজিজের এক চিঠির জবাবে—যেখানে তিনি ফিলিস্তিন-ইস্যুতে আমেরিকার অবস্থান নিয়ে নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন—আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান লেখেন, আমেরিকা তার অবস্থানের ওপর অটল রয়েছে। আর তা হলো, জনসাধারণকে তার রাজত্ব ফিরিয়ে দেওয়া হবে, আবার ফিলিস্তিনে ইহুদিদের পুনর্বাসনও জরুরি।
২৭ অক্টোবর ১৯৯৪ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন তার ইসরায়েল সফরের সময় ইসরায়েলের পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে এই বক্তব্য দিয়েছিল যে, তোমাদের পতন আমাদের পতন। আমেরিকা আজও তোমাদের সাথে আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে।
এই পরিস্থিতিতে কোনো গায়েবি সাহায্যের ব্যবস্থা হলে তবেই ফিলিস্তিন-সমস্যার সমাধান হতে পারে। وما ذلك على الله بعزيز
শুভপরিণাম হকপন্থীদেরই হয়
মুফাক্কিরে ইসলাম সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ. লেখেন, বিজয় ও শ্রেষ্ঠত্ব ইনশাআল্লাহ সে জাতিরই হবে, যে হকপন্থী ও মানবতার জন্য ব্যাপক ও স্থায়ী বার্তা নিয়ে এসেছে। যার দয়ার পরিধিতে বিশ্বমানবতার জন্য অংশ রয়েছে। যার দৃষ্টিতে সমগ্র সৃষ্টিকুল আল্লাহর পরিবারভুক্ত। যে হকের জন্য সর্বত্র বুক পেতে দেয় এবং অন্যায়ের মোকাবেলা করে সব পরিস্থিতিতে, সব সুরতে এবং সব জায়গায়; যে মানবতার সেবার জন্যই বেঁচে আছে এবং মানবতার সাথেই জুড়ে আছে। যার আঁচল বিপর্যয় ও নাশকতা থেকে পবিত্র এবং যে অহমিকা ও বিপর্যয়ের জন্য নয়, বরং হক ও ইনসাফের পতাকাবাহী।([2])
[1]. এই চুক্তিটি ফ্রান্সের প্রতিনিধি জর্জ পিকু (Georges Picot) ও ব্রিটেনের প্রতিনিধি স্যার মার্ক সাইকস (Sir Mark Sykes)-এর মধ্যে হয়েছে। এজন্যই তাকে সাইকস-পিকু চুক্তি (Sykes-Picot Agreement) বলা হয়। ইহুদিদের ফিলিস্তিনে বসতিস্থাপন ও নিয়ন্ত্রণের এটিই মূলভিত্তি। এই চুক্তিটি ১৯১৬ সালে হয়েছিল।
[2]. আলমে আরব কা আলমিয়া, পৃষ্ঠা : ১৮৩
(পুনরায় প্রকাশন থেকে প্রকাশিত “ফিলিস্তিন: সাম্রাজ্যবাদ ও মুসলিমবিশ্ব” বই থেকে সংগৃহিত)
 আহলে হক্ব বাংলা মিডিয়া সার্ভিস Ahle Haq Media
আহলে হক্ব বাংলা মিডিয়া সার্ভিস Ahle Haq Media