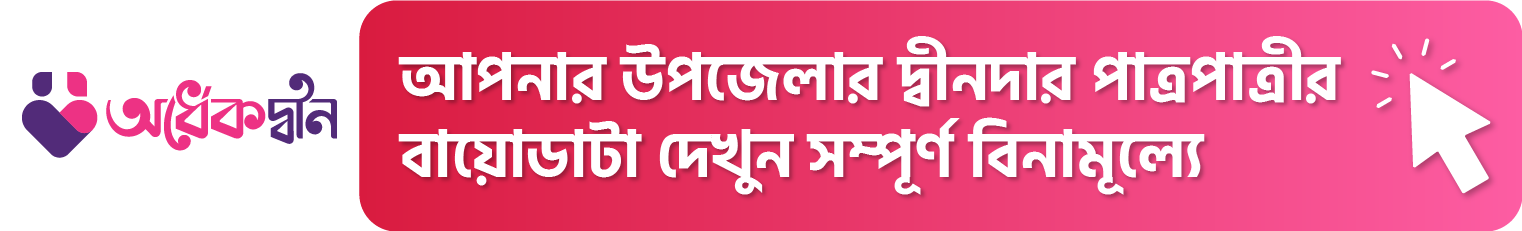আল্লামা আব্দুল মতীন দামাত বারাকাতুহু
মুযাফফর বিন মুহসিন তার ‘জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর ছালাত’ বইয়ে বিতর নামায সম্পর্কেও অনেক জালিয়তি ও ভুল তথ্য পেশ করেছেন। তিনি চেষ্টা করেছেন একথা প্রমাণ করার যে, বিতর ছালাত এক রাকাত অথবা তিন রাকাত হলে দুই সালামে কিংবা দ্বিতীয় রাকাতে বৈঠক ব্যতিত এক সালামে। এখানে সে সম্পর্কে কিছু পর্যালোচনা তুলে ধরা হল। সামনের আলোচনায় ‘গ্রন্থকার’ বলে সাধারণত মুযাফফর বিন মুহসিনকেই বুঝানো হয়েছে।
পর্যালোচনা: বিতর ছালাত অধ্যায়
গ্রন্থকার – ১
গ্রন্থকার বলেন: “একাদশ অধ্যায় বিতর ছালাত: … কিন্তু এক রাক‘আত বলে কোন ছালাতই নেই এ কথাই সমাজে বেশি প্রচলিত। উক্ত মর্মে কিছু উদ্ভট বর্ণনাও উল্লেখ করা হয়:” (পৃ.৩২৫)
পর্যালোচনা
(ক) এক রাকাত বলে কোন নামায নেই
ইমাম ইবনুছ ছালাহ (র.) বলেন, নবীজী থেকে কেবলই এক রাকাত বিতর পড়ার কথা প্রমাণিত নয়। [আত-তালখীছুল হাবীর ২/৩৯]
(খ)
গ্রন্থকার বলেন: “উক্ত মর্মে কিছু উদ্ভট বর্ণনাও উল্লেখ করা হয়”: অতঃপর গ্রন্থকার একটি মারফু ও একটি মওকুফ বর্ণনা উল্লেখ করে দুটোকেই যঈফ বলার চেষ্টা করেছেন! অভিধানে ‘উদ্ভট’ শব্দের অর্থ: আজগুবি কোন কথা যার কোনই বাস্তবতা নেই। গ্রন্থকারের উল্লিখিত দুটি বর্ণনাকে কোন মুহাদ্দিস জাল, ভিত্তিহীন বা উদ্ভট বলেছেন এমন কোন উদ্ধৃতি তিনি দিতে পারেননি। তিনি নিজেও সাহস করে বর্ণনা দুটির সাথে জাল বা উদ্ভট শব্দ যোগ করতে পারেননি। বরং তিনি শুধু ‘যঈফ’ বলেছেন। তবে কেন ‘কিছু উদ্ভট’ না বলে ‘কিছু যঈফ’ বর্ণনা বলা হল না?
আর যদি ‘যঈফ’কেই তিনি ‘উদ্ভট’ বলে থাকেন তাহলে তা চরম অন্যায়। কারণ, হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষায় ‘যঈফ’ (দুর্বল) ও ‘মউজু’ (জাল) দুটি ভিন্ন পরিভাষা। দুটোর ভিন্ন ভিন্ন বিধান রয়েছে। দুটোকে একাকার করে ফেলা একটি পরিভাষাকে নষ্ট ও বিকৃত করে ফেলা ছাড়া আর কিছুই নয়।
গ্রন্থকার – ২ (প্রথম বর্ণনা)
গ্রন্থকার ‘উদ্ভট’ বর্ণনার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে প্রথমে উল্লেখ করেন: “(ক) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল (ছা.) এক রাক‘আত বিতর পড়তে নিষেধ করেছেন। তাই কোন ব্যক্তি যেন এক রাক‘আত ছালাত আদায় করে বিজোড় না করে” (পৃ.৩২৫)
পর্যালোচনা : ভুল তরজমা
এখানে তিনি হাদীসের ভুল তরজমা করেছেন। সঠিক তরজমা হল: ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ‘বুতাইরা’ থেকে নিষেধ করেছেন: (বুতাইরা হল) যে, ব্যক্তি শুধু এক রাকাত পড়বে বিতর হিসেবে’। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যেন এক রাকাত বিতর না পড়ে। আর গ্রন্থকারের তরজমায় এসেছে: ‘কোন ব্যক্তি যেন এক রাক‘আত ছালাত আদায় করে বিজোড় না করে’। এর অর্থ দাড়ায় ইবনে মাসউদ রা. বলতে চাচ্ছেন দুই রাকাত ছালাত আদায় করে জোড় করে নিলেই হয়!
হাদীসের আরবী পাঠটি :
(أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن البتيراء أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها)
গ্রন্থকার – ৩
গ্রন্থকার আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত উপর্যুক্ত হাদীসটির মান নিয়ে আলোচনা করে বলেন:
১. “আব্দুল হক বলেন: উক্ত বর্ণনার সনদে উসমান বিন মুহাম্মদ বিন রবীআ রয়েছে”
পর্যালোচনা :
বর্ণনাকারী সম্পর্কে আব্দুল হক ইশবীলীর আপত্তি গ্রন্থকার টীকায় আরবীতে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: ‘তার হাদীসে ভুলের সংখ্যাই বেশি’।
অন্যদিকে ‘আল মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন’ গ্রন্থে (হা.২৩৪৫) উক্ত উসমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে রাবীআর একটি প্রসিদ্ধ বর্ণনা (لا ضرر ولا ضرار) উল্লেখপূর্বক হাকিম আবু আব্দিল্লাহ বলেন: হাদীসটি মুসলিম শরীফের শর্তানুযায়ী সহীহ। ইমাম যাহাবীও তার সমর্থন করে বলেন: এটি মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। উসমান ইবনে মুহাম্মদ এর হাদীসকে হাকিম ও যাহাবী সহীহ সাব্যস্ত করেছেন। তাই উসমান সম্পর্কে আব্দুল হকের সিদ্ধান্তই একক সিদ্ধান্ত নয়। সুতরাং হাকেম ও যাহাবীর বক্তব্যের আলোকে আলোচ্য বর্ণনাটি সহীহ।
আব্দুল হক ইশবীলীর মন্তব্যকে যদি সঠিক ধরেও নেয়া হয়। আর এ কারণে এ হাদীসকে যঈফ বলা হয়: তবু এর পক্ষে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে শক্তিশালী সহীহ ‘মওকুফ’ বর্ণনা রয়েছে যার বিবরণ সামনে আসছে। আর এ বিষয়ক মওকুফ বর্ণনাও সাধারণ নিয়মে ‘মারফু হুকমী’ তথা পরোক্ষ মরফু এর অন্তর্ভুক্ত, যা শাস্ত্রীয় জ্ঞান সম্পন্ন সকলেরই জানা।
গ্রন্থকার – ৪
এ হাদীস সম্পর্কে গ্রন্থকার আরো বলেন: “ইমাম নববী বলেন এক রাকাত বিতর নিষেধ মর্মে মুহাম্মদ ইবনে কা‘ব -এর হাদীছ মুরসাল ও যঈফ” (পৃ.৩২৫)
পর্যালোচনা
(ক)
এক হাদীস বিষয়ক আপত্তি অন্য হাদীসে জুড়ে দেয়া
ইমাম নববীর এ বক্তব্যটি আবু সাঈদ খুদরী (রা) এর বর্ণনার বিষয়ে নয়। বরং বরাত হিসেবে উল্লিখিত কিতাব ‘খুলাছাতুল আহকামে’ (হা.১৮৮৮) ইমাম নববী আবু সাঈদ রা. বর্ণনা উল্লেখও করেননি। এবং এ বিষয়ে কোন মন্তব্যও করেননি। তিনি যা বলেছেন: তা মুহাম্মদ ইবনে কা‘ব (তাবেঈ) থেকে ভিন্ন সনদে বর্ণিত স্বতন্ত্র আরেকটি মুরসাল বর্ণনা সম্পর্কে! যা হানাফীদের কেউ দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছেন বলে আমার জানা নেই।
আশ্চর্য! গ্রন্থকার এক হাদীসের তাহকীকের নামে অন্য হাদীস সম্পর্কিত বক্তব্য উল্লেখ করে দিলেন!
(খ)
নববী (রহ) কৃর্তৃক উদ্ধৃত বর্ণনাটি আবু সাঈদ (রা) এর বর্ণনার সমর্থক
উদ্ধৃত মুহাম্মদ ইবনে কা‘ব আল কুরাজী এর মুরসাল বর্ণানাটি কোন কিতাবে সনদসহ আছে তা নববী (রহ.)ও উল্লেখ করেননি। এবং তাকে কেন যঈফ বলেছেন: তার কারণও তিনি বলেননি। এতে কোন বর্ণনাকারী আছেন যার কারণে তাকে যঈফ বলতে হয় তাও তিনি চিহ্নিত করেননি। আবার তিনিই এ বর্ণনাটি তাঁর ‘আল-মাজমূ’ কিতাবে (৪/২২) উল্লেখ করেছেন। সেখানে এর পরবর্তী হাদীস বিষয়ে মন্তব্য করলেও এ হাদীস সম্পর্কে তিনি কিছুই বলেননি।
আর যদি এটি যঈফও হয়ে থাকে তবুও এটি পূর্ববর্তী আবু সাঈদ খুদরী (রা) এর বর্ণনার সমর্থক। এতে আবু সাঈদ (রা) এর পূর্বোল্লিখিত বর্ণনাটি আরো শক্তিশালী হয়।
রয়ে গেল বর্ণনাটি ‘মুরসাল’ হওয়ার বিষয়। তো এটি পরিত্যাগযোগ্য মুরসাল নয়। কারণ মুহাম্মদ ইবনে কা‘ব সরাসরী সাহাবী বা প্রথম স্তরের প্রবীণ তাবেঈ। ইমাম তিরমিযী রহ. কুতায়বা সূত্রে উল্লেখ করেছেন: মুহাম্মদ ইবনে কাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিবদ্দশায়ই জন্ম গ্রহণ করেছেন। [সুনানে তিরমিযী হা.২৯১০]
এজন্য অনেকেই তাঁকে সাহাবীদেরও দলভুক্ত করেছেন। বরং ইবনুস সাকানের বর্ণনায় রয়েছে, তিনি নবীজীকে পেয়েছেন এবং একটি হাদীসও শুনেছেন। [দেখুন আল-ইসতী‘আব, ২৩৪২] আর সাহাবীদের মুরসাল বর্ণনা সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য। তাবেঈদের মুরসালও অনেক ইমাম ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের নিকট শর্তসাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য।
ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর অসংখ্য অনুসারী ইমাম ও ফকীহ, ইমাম মালেক ও তাঁর অসংখ্য অনুসারী মুহাদ্দিস ও ফকীহ এবং ইমাম শাফেঈ ও তাঁর অনুসারী অসংখ্য মুহাদ্দিসও শর্ত সাপেক্ষে মুরসালকে গ্রহণ করেন। (আত-তামহীদ :এর ভূমিকা ১/৫-৬) স্বয়ং নাসীরুদ্দীন আলবানী সাহেবও মুরসালকে দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (দেখুন: ইরওয়াউল গালীল ২/৭১)
গ্রন্থকার – ৫ (দ্বিতীয় বর্ণনা)
গ্রন্থকার ‘উদ্ভট’ বর্ণনার আলোচনায় উল্লেখ করেন:
عن حصين قال : بلغ ابن مسعود أن سعدا يوتر بركعة قال : ما أجزأت ركعة قط
(খ) হুছাইন (রাঃ) বলেন, ইবনু মাসউদ (রাঃ) -এর কাছে যখন এই কথা পৌছল যে, সা‘দ এক রাকআত বিতর পড়েন। তখন তিনি বললেন, আমি এক রাকআত ছালাতকে কখনো যথেষ্ট মনে করিনি। অন্যত্র সরাসরি তার পক্ষ থেকে বর্ণনা এসেছে :(عن ابن مسعود ما أجزأت ركعة قط) ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আমি কখনো এক রাক‘আত ছালাত যথেষ্ট মনে করি না”। ( ) (পৃ.৩২৫-৩২৬)
পর্যালোচনা
(ক) হাদীসের তরজমায় সুস্পষ্ট ভুল
গ্রন্থকার (أجْزَأَتْ) শব্দের অর্থ করেছেন: ‘যথেষ্ট মনে করিনি/করিনা’ এটি ভুল। এর সঠিক অর্থ হল: ‘যথেষ্ট হয় না বা হবে না’। আসলে গ্রন্থকার শব্দটিকে পড়েছেন: (أَجْزَأْتُ) ‘আজ্যা‘তু’ যা এখানে সঠিক নয়। বিশুদ্ধ হল: (أَجْزَأَتْ) ‘আজ্যা‘আত্’। আর এ ভুলের কারণেই তিনি পরবর্তী শব্দটিকে (رَكْعَةً) ‘রাক্‘আতান্’ : তা-এ যবর দিয়ে পড়ে আরেকটি ভুলের শিকার হয়েছেন। অথচ এখানে হবে (رَكْعَةٌ)‘রাক‘আতুন্’ :তা-এ পেশ।
ব্যাকরণের পরিভাষায় (رَكْعَةٌ) ‘রাক‘আতুন’ শব্দটি (أَجْزَأَتْ) ‘আজ্যা‘আত্’ এর কর্তা। কিন্তু এখানে গ্রন্থকার কর্তা ধরেছেন ইবনে মাসউদকে। অথচ আরবী ভাষা এর সমর্থন করে না। কেননা (أَجْزَأْتُ) ‘আজ্যা‘তু’ শব্দটি নির্গত হয়েছে : (إِجْزَاء) ‘ইজ্যা’ (মূলে: ج، ز، ي জা-যা-ইয়া) থেকে। আর শব্দটি (لازم) অকর্মক ক্রিয়া (
In transitive) এর অর্থ হওয়া বুঝায়। একে (متعدي) সকর্মক ক্রিয়া (
Transitive) করতে হলে পরবর্তী শব্দে (باء) ‘বা’ বর্ণটি যোগ করতে হয়। এখানে শব্দটি (باء) ‘বা’ ব্যতীতই ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এর দ্বারা ‘যথেষ্ট মনে করা’ অর্থ নেয়া সুস্পষ্ট ভুল।
আরো আশ্চর্যের বিষয় হল, গ্রন্থকার এ হাদীসের তাহক্বীকের বরাত দিয়েছেন: (টীকা নং ১২৫৮) তাহক্বীক মুওয়াত্তা মুহাম্মদ। অর্থাৎ ড. তকীউদ্দীন নদবীর তাহক্বীক যার গ্রন্থকারের টীকা (নং ১২৫২) থেকে স্পষ্ট। আর তকীউদ্দীন নদবী তার কিতাবে (২/১৭-১৮) হাদীসটিতে হরকত দেওয়া রয়েছে এভাবে (أجزأتْ) ‘আজ্যা‘আত্’ ও(ركعةٌ) ‘রাক‘আতুন’। গ্রন্থকারের বরাত দেওয়া থেকে বুঝা যায় এ কিতাবটিও তার কাছে ছিল। কিন্তু তার পরও কেন এত বড় ভুল এর রহস্য আল্লাহ তাআলাই ভার জানেন।
গ্রন্থকার – ৬
গ্রন্থকার বর্ণনাদুটি উল্লেখপূর্বক লেখেন: “তাহক্বীক: ইমাম নববী উক্ত আছার উল্লেখ করার পর বলেন: এটি যঈফ ও মাউকুফ। ইবনু মাসউদের সাথে হুছাইনের কখনো সাক্ষাৎ হয়নি। ইবনু হাজার আসক্বালানীও তাই বলেছেন।” (পৃ.৩২৬)
পর্যালোচনা
(ক) গ্রন্থকারের তাহক্বীক!
গ্রন্থকার ইমাম নববীর বক্তব্যের কোন বরাত উল্লেখ করেননি। আমি ইমাম নববীর এবক্তব্যটি পেয়েছি: তার ‘খুলাছাতুল আহকাম’ গ্রন্থে (হা. ১৮৮৯)। কিন্তু এতে তিনি উক্ত বর্ণনাকে যঈফ বলার কোন কারণ উল্লেখ করেননি। আর এটাকেই গ্রন্থকার ‘তাহক্বীকের’ নামে চোখ বুজে মেনে নিয়েছেন।
(খ) বর্ণনাটি কি যঈফ?
বর্ণনাটি পেয়েছি: ‘আল মু‘জামুল কাবীর: তাবারানী (হা.৯৪২২), মুআত্তা মালেক: ইমাম মুহাম্মদের বর্ণনা (হা.২৬৪) কিতাবুল হুজ্জাহ আলা আহলিল মদীনা (১/১৯৭) এ তিনটি কিতাবে।
তিন কিতাবে বর্ণিত বর্ণনাটির সকল বর্ণনাকারীই বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। তাই একে যঈফ বলার সুযোগ নেই (দেখুন: তাবারানীর সনদ: ১. আলী ইবনে আব্দিল আযীয (সিয়ার) ২. আবূ নুআইম ফাযল ইবনে দুকাইন (তাহ্যীব) ৩.ক্বাসেম ইবনে মা‘ন (সিয়ার) ৪.হুছাইন ইবনে আব্দির রহমান (তাহ্যীব)। মুয়াত্তা ও কিতাবুল হুজ্জার সনদ: ১.আবু ইউসূফ ২.হুছাইন ইবনে আব্দুর রহমান ৩.ইবরাহীম আন নাখাঈ। নূরুদ্দীন হাইসামী তাবারানীর বরাত দেওয়ার পর বলেন: এর সনদ হাসান। (মাজমাউয যাওয়াইদ ২/২৪২ হা.৩৪৫৭)
অতঃপর গ্রন্থকার বলেছেন: “এটি মওকুফ”। তাতো বটেই। কিন্তু এটি মওকুফ তথা সাহাবীর কথা হলেও: এ অধ্যায়ে ‘মারফুয়ে হুকমী’ তথা পরোক্ষ মারফূ। (নছবুর রায়া: বরাতে মুয়াত্তা মুহাম্মদের টীকা: তাকী উদ্দীন নদবী ২/২২) আবার গ্রন্থকার নিজেও তার গ্রন্থের বিতর অধ্যায়েই (পৃ.৩৩২ ও ৩৩৩) একটি মওকুফ বর্ণনা ও দুটি তাবেঈর আমল দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছেন!
(গ) রয়ে গেল গ্রন্থকারের কথা :“ইবনু মাসউদের সাথে হুছাইনের কখনো সাক্ষাৎ হয়নি”
গ্রন্থকার এর দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন: বর্ণনাকারী হুছাইন হযরত ইবনে মাসউদকে পাননি। তাই এটি সূত্রবিচ্ছিন্ন। নুরুদ্দীন হাইসামী তাঁর মাজমাউয যাওয়াইদ (২/২৪২) গ্রন্থে কেবল তাবারানীর বর্ণনা সম্পর্কেই এ সূত্র বিচ্ছিন্নতার আপত্তি করেছেন।
কিন্তু মুয়াত্তা ও কিতাবুল হুজ্জার বর্ণনায় রয়েছে হুছাইন বর্ণনাটি ইবরাহীম নাখাঈ থেকে শুনেছেন। সুতরাং হুছাইন ইবনে মাসউদের সাক্ষাৎ পাওয়ার কোন প্রয়োজনই নেই। এমনকি ‘নছবুর-রায়া’ ও ‘আদ্-দিরায়া’ গ্রন্থে উদ্ধৃত তাবারানীর বর্ণনাতেও রয়েছে: হুছাইন বর্ণনা করেছেন ইবরাহীম থেকে ।
কারো প্রশ্ন হতে পারে, নুরুদ্দীন হাইসামীও এ কথা বলেছেন? তাহলে বলবো তিনি শুধু তাবারানীর বর্ণনা সম্পর্কে বলেছেন। হয়ত তাঁর কাছে সংরক্ষিত তাবারানীর কপিতে এমনই ছিল। কিন্তু ইমাম যাইলাঈ হাইসামীল আগের এবং ইবনে হাজার আসকালানী তাঁর পরের। তাদের দুজনের কপিতে ছিল এর ব্যতিক্রম। তাছাড়া হাইসামী সকল বর্ণনাকে অনির্দিষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করেননি। এবং সাথে সাথে তিনি বলেছেন: ‘এর সনদ হাসান’। গ্রন্থকার যদি হাইসামীল বক্তব্যই উদ্ধৃত করে থাকেন: তাহলে ‘এর সনদ হাসান’ :এ কথাটি বাদ দিলেন কোন উদ্দেশ্যে?
আর ইবরাহীম নাখাঈ (রহ.) হযরত ইবনে মাসউদ থেকে সরাসরি হাদীস না শুনলেও মুহাদ্দিসগণের নিকট স্বীকৃত যে, ইবনে মসউদ থেকে তাঁর সকল বর্ণনা মুরসাল হলেও গ্রহণযোগ্য ও প্রামাণ্য। ইবরাহীম নাখাঈ (রহ.) বলেন: ‘ইবনে মাসউদ থেকে যখন কোন বর্ণনা এক ব্যক্তি সূত্রে শুনি তখন তার নাম উল্লেখ করি। আর যখন একাধিক ব্যক্তি থেকে শুনি তখন তাদের নাম বাদ দিয়ে সরাসরি ইবনে মাসউদ থেকেই বর্ণনা করি’।
[দেখুন সুনানে দারা কুতনী: ৪/২২৬ হা.২৯৩৬ কিতাবুল ইলাল- তিরমিযী]তদুপরি কিতাবুল হুজ্জাহ এর পরবর্তী বর্ণনাটিতেই ইবরাহীম নাখাঈ হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে এ কথাটিই ভিন্ন শব্দে বর্ণনা করেছেন: আলকামার সূত্রে। সুতরাং বুঝা যায় পূর্বের বর্ণনাটিও ইবরাহীম আলকামাসহ অন্যদের সূত্রেই শুনেছেন। আর আলকামা হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) এর অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য শিষ্য। সুতরাং বাহ্যিকভাবেও বর্ণনাটি সূত্রবিচ্ছিন্ন রইল না। [দেখুন, মাহদী হাসান শাহজাহানপুরীর বক্তব্য: কিতাবুল হুজ্জার টীকা ১/১৯৭-১৯৮]
গ্রন্থকার বলেছেন: “ইবনু হাজার আসক্বালানীও তাই বলেছেন।” কিন্তু এর কোন বরাত তিনি উল্লেখ কনেনি। আবার ‘তাই’ বলতে গ্রন্থকার কি ‘যঈফ ও মওকুফ’ বুঝিয়েছেন, না ‘ইবনে মাসউদ (রা.) এর সাথে হুছাইন এর সাক্ষাত হয়নি’ সেকথা বুঝিয়েছেন তাও পরিস্কার করেননি। যাই হোক : ‘আদ-দিরায়া’ (১/১৯২) গ্রন্থে ইবনে হাজার (রহ.) বর্ণনাটি তাবারানী ও মুয়াত্তাসূত্রে উল্লেখ করে তাতে কোন মন্তব্যই করেননি। তাই আমি যথেষ্ট সন্দিহান ইবনে হাজার এ ধরণের কোন একটি মন্তব্য এ বর্ণনার উপর করবেন! তাছাড়া এতে ইবনে হাজার ‘তাবারানীর’ বর্ণনায়ও ‘হুছাইন ইবরাহীম থেকে’ বলেছেন। সুতারাং হুছাইনের সাক্ষাত বিষয়ে তিনি কোন আপত্তি করতেই পারেন না।
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এর এ জাতীয় একাধিক বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত বলেই ইবনু আব্দিল বার মালেকী (মৃত.৪৬৩) বলেন: (وكره ابن مسعود الوتر بركعة ليس قبلها شيء وسماها البتيراء.) ইবনে মাসউদ পূর্বে কোন নামায ব্যতিত এক রাকাতে বিতরকে অপসন্দ করেছেন এবং একে ‘বুতাইরা’ নাম দিয়েছেন। [আল ইসতিযকার ৫/২৮৫]
(ঘ) একটি ধোঁকা
বরং আমার মনে হয় “(ইবনে মাসউদের সাথে হুছাইনের কোন সাক্ষাতই হয়নি। ইবনু হাজার আসক্বালানীও তাই বলেছেন।” এ কথাটি গ্রন্থকারের একটি ধোঁকা মাত্র। কারণ তিনি এর বরাত দিয়েছেন (টীকা-১২৫৮) তাহক্বীক মুওয়াত্তা মুহাম্মদ ২/২২। এর দ্বারা তিনি ড. তকীউদ্দীন নদবীর তাহক্বীককৃত মুওয়াত্তার নসখাটিই বুঝিয়েছেন যার বরাত তিনি পূর্ববর্তী টীকা নং ১২৫২ এ উল্লেখ করেছেন। প্রথমত এখানে তিনি (১) পৃষ্ঠা নম্বর দিয়েছেন ২/২২। এটি মূলত আল-মাকতাবাতুশ শামেলার পৃষ্ঠা। মূল কিতাবে রয়েছে ২/১৭-১৮ পৃষ্ঠায়। (২) মুওয়াত্তার বর্ণনাটি হুছাইন হযরত ইবনে মাসউদ থেকে নয় বরং ইবরাহীম নাখাঈ থেকে নিয়েছেন। তাই ইবনে মাসউদের সাথে হুছাইনের সাক্ষাতের কোন প্রয়োজনই নেই। (৩) উল্লিখিত বরাতে ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর এরূপ কোন বক্তব্যই নেই। সুতরাং ইবনে হাজারের উদ্ধৃতি ও টীকার বরাত সবই একটি ধোঁকামাত্র।
গ্রন্থকার – ৭
গ্রন্থকার “এক রাক‘আত বিতর পড়ার ছহীহ হাদীছ সমূহ:” শিরোনামে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে চারটি এবং আবু আইয়্যুব আনছারী ও ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে একটি করে মোট ছ’টি হাদীস উল্লেখ করেছেন। আমি এ বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু মৌলিক কথা আলোচনা করব ইনশাল্লাহ।
গ্রন্থকার এখানে শব্দ ব্যবহার করেছেন: ‘হাদীছ সমূহ’। অথচ তার উদ্ধৃত ইবনে উমর (রা) এর চারটি বর্ণনা মূলত একই হাদীস যা গ্রন্থকারও ভালরকম জানেন বলেই মনে হল। অথবা বলা যেতে পারে এখানে দুটি বর্ণনা। আর পঞ্চম ও ষষ্ট বর্ণনা দুটি এক রাকাতের কোন দলিল হয় না।
সুতরাং ছটি বর্ণনার সবকটি মিলে হাদীস একটিই- হযরত উবনে উমর (রা.) থেকে। একেই তিনি, ‘হাদীছ সমূহ’ বলে ব্যক্ত করেছেন।
পর্যালোচনা
ইবনে উমর (রা.) এর বর্ণনার কি উদ্দেশ্য
আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বিতর বিষয়ক বর্ণনাটি: হযরত নাফে, আবু সালামা, আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার, আব্দুল্লাহ ইবনে শাক্বীক, সালেম ইবনু আব্দিল্লাহ, হুমাইদ ইবনে আব্দির রাহমান, আলী ইবনে আব্দিল্লাহ আল বারিকী, কাসেম ইবনে মুহাম্মদ, উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দিল্লাহ, আবু মিজলায, আতিয়্যা ইবনে সা‘দ, মুহাম্মদ ইবনে আব্দির রাহমান, উকবা ইবনে হুরাইস, তাউস, আনাস ইবনে সীরীন প্রমুখ (১৫ জন) তাবেয়ীগণ বর্ণনা করেছেন। (দেখুন: আলমুসনাদুল জামে’ হা.৭৪১৪-৭৪২৯ ১০/১৯৫-২০৮ কাশফুসসিত্র:আন সালাতিল বিতর:কাশমিরী পৃ.২৬)
আনাস ইবনে সীরীন ব্যতীত অবশিষ্ট চৌদ্দজনের বর্ণনা মূলত একই ঘটনার বিবরণ। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জনৈক ব্যক্তি রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি মিম্বরে থেকেই এর জবাবে হাদীসটি ইরশাদ করেন। সুতরাং হাদীসটি ‘কওলী’ তথা নবীজীর বক্তব্য। সবগুলোই মূলত একই হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা। শুধু আনাস ইবনে সীরীনের বর্ণনায় এসেছে: ইবনে উমর (রা) বলেন: নবীজী এভাবে নামায পড়তেন :যা গ্রন্থকার প্রথম নম্বরে উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বুঝা যায় হাদীসটি ‘ফে‘লী’ তথা কর্মবিষয়ক বিবরণ। এবং এটি ভিন্ন হাদীস। সুতরাং এতে বুঝা যায় ইবনে উমর থেকে এ বিষয়ের হাদীস দুটি।
ইবনে উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত:
ويوتر بركعة/ والوتر ركعة من آخر الليل/ فإذا خشي الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى/ والوتر ركعة واحدة)
এ জাতীয় শব্দগুলো মূলত একটি বর্ণনার বিভিন্ন শব্দ। তাই মুসনাদে বায্যার সংকলক বলেন: (وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ وُجُوهٍ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ أَوْ قَرِيبٌ) :এ হাদীসটি ইবনে উমর রা. থেকে বিভিন্ন সূত্রে ও বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে, তবে সবগুলি বর্ণনার অর্থ একই বা কাছাকাছি। (দেখুন, আল-বাহরুয যাখ্খার হা.৬১৫৪)।
আর এ জাতীয় শব্দ থেকে এক রাকাত বিতর এর পক্ষে স্পষ্ট দলিল হয় না। কেননা এর একটি শব্দে আছে: (ويوتر بركعة) যার অর্থ যেমন হতে পারে: ‘এক রাকাত বিতর পড়তেন’ তেমনি এও হতে পারে: ‘এক রাকাতের মাধ্যমে বিতর করতেন’ অর্থাৎ পূর্বের দুই রাকাতের সাথে এক রাকাত যোগ করে বিতর (বেজোড় তথা তিন) করে নিতেন। অন্য শব্দে আছে: (صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى) :এক রাকাত পড়ে নিবে যা পূর্বের সব নামাযকে বিতর বানিয়ে দেবে।
অর্থাৎ বিতর এক রাকাত নয় বরং এই এক রাকাত পূর্বের নামাযকেও বিতর বানিয়ে দেবে। তাই ইবনে উমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত মৌখিক বর্ণনা থেকে এক রাকাত বিতর পড়ার স্পষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।
বরং এতে বিতর তিন রাকাত দুই সালামে বা তিন রাকাত এক সালাম ও দুই বৈঠকে হওয়ারও যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা:
(ক)
ইবনে উমর (রা) থেকে একাধিক সূত্রে এসেছে: (صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى) :“এক রাকাত পড়ে নেবে যা পূর্বের আদায়কৃত নামাযকে বিতর বানিয়ে দেবে”। অর্থাৎ বিতর এক রাকাত নয় বরং পূর্বের নামাযও বিতর হয়ে গেল। দেখুন: গ্রন্থকারের উদ্ধৃত বর্ণনা (পৃ.৩২৭)
(খ)
ইবনে উমর (রা.) যখন বিতর পড়তেন তখন তিন রাকাত বিতর পড়তেন। তবে দুই সালামে। যার বিবরণ গ্রন্থকার (পৃ.৩৩৩) দিয়েছেন এভবে: “জ্ঞাতব্য: তিন রাক‘আত বিতর পড়ার ক্ষেত্রে দুই রাক‘আত পড়ে সালাম ফিরিয়ে পুনরায় এক রাক‘আত পড়া যায়। তিন রাক‘আত বিতর পড়ার এটিও একটি উত্তম পদ্ধতি। (টীকায়:বুখারী হাদীস/৯৯১ ইরওয়াউল গালীল ২/১৪৮” বর্ণনাটি হল:
]رواه مالك (১/১২৫/২০) عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة فى الوتر حتى يأمر ببعض حاجته
সুতরাং ইবনে উমর (রা.) নিজেই বর্ণনা থেকে বুঝেছেন: বিতর তিন রাকাত। সাহাবী বর্ণিত অস্পষ্ট হাদীসের জন্য সাহাবীর নিজস্ব আমলই উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা। তাই ইবনে উমরের আমলই বলে দেয়: এ হাদীসে বর্ণিত বিতর নামায তিন রাকাত।
(গ)
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে: (صلاة المغرب وتر النهار) (মুছান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হা. ৬৭৭৩) গ্রন্থকারের মতাদর্শী আলেম আব্দুল্লাহ আল-কাফি স্বরচিত ‘বিতর ছালাতে’ এ বর্ণনাকে সহীহ বলেছেন। এবং তিনি বলেছেন: “এখানে রাকাতের সংখ্যার দিক থেকে বিতরকে মাগরিবের মত বলা হয়েছে।” (পৃ.৩২-৩৩)
এ হাদীসে মূলণীতিরূপে ইবনে উমর বলেছেন: মাগরিব হল দিনের বিতর। সুতরাং রাতের বিতরকেও মাগরিবের অনুরূপ করে পড়। আলোচ্য হাদীসের বর্ণনাকারী ইবনে উমর (রা) এ বক্তব্যই প্রমাণ করে তিনি মনে করতেন বিতর নামায তিন রাকাত। আর তাই এখানে আলোচ্য হাদীসের সঠিক ব্যখ্যার ইঙ্গিত বহন করে।
(ঘ)
ইমাম শা‘বী সূত্রে একটি সহীহ বর্ণনায় ইবনে আব্বাস এর মত ইবনে উমর (রা)ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামাযের বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন: ‘তিনি তিন রাকাতে পড়তেন’। [ সুনানে ইবনে মাজা হা. ১৩৬১, আরো দ্রষ্টব্য বিতির নামায তিন রাকাত অধ্যায়]
(ঙ)
তাবেয়ী আবু-মিজ্লায্ হাদীসটি ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাস দুজন থেকেই বর্ণনা করেছেন। যা সহীহ মুসলিমের বরাতে গ্রন্থকার :(والوتر ركعة من آخر الليل) শব্দে উল্লেখ করেছেন [হা.১৭৯৩]। এতে বুঝা যায় মূল বর্ণনাটি ইবনে আব্বাস (রা.)ও শুনেছেন। তথাপি ইবনে আব্বাস রা. বিতর এক সালামে তিন রাকাতই পড়তেন এবং এক রাকাত পড়াকে অপসন্দ করতেন। [আরো দেখুন: সুনানে ইবনে মাজা হা.১২৩১ আল মু‘জামুল কাবীর: তাবারানী হা.১০৯৬৩ আননুকাতুত তারীফা পৃ. ১৮৬ কাশফুস সিতর পৃ. ৩২]
(চ)
বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী: ‘এক রাকাত পড়ে নাও’: বাক্যে এক রাকাত বিতর পড়ার বর্ণনাটি সম্পর্কে বলেন, (এতে এক রাকাত বিতর এর পক্ষে স্পষ্ট দলিল নেই বরং) ‘দুই সালামে তিন রাকাত বিতর পড়া’ (অর্থাৎ দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে আরেক রাকাতযোগে মোট তিন রাকাত বিতর) এর পক্ষে স্পষ্ট দলিল হয় না। হতে পারে এতে উদ্দেশ্য হল: ‘পূর্বের পড়া দুই রাকাতের সাথে মিলিয়ে এক সালামে মোট তিন রাকাত বিতর পড়’। অথচ তিনি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী একজন বিখ্যাত হাফেজে হাদীস। তাঁর মতে বিতর দুই সালামে তিন রাকাত। তবুও তিনি এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন।
তাঁর বক্তব্যটি নিম্নরূপ
قال الحافظ فى الفتح 2/4781: واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم صلى ركعة واحدة على ان فصل الوتر أفضل من وصله وتعقب بأنه ليس صريحا فى الفصل فيحتمل أن يريد بقوله صلى ركعة واحدة أى مضافة إلى ركعتين مما مضى
সম্ভবত এ কারণেই এক রাকাত বিতর নামাযের ইঙ্গিত বহনকারী এ ধরণের হাদীস বর্ণনা করার পরও ইমাম আবু-হানীফাসহ অনেক ইমামের মতই ‘মুয়াত্তা’ সঙ্কলক ইমাম মালেক, ‘মুসনাদ’ সঙ্কলক ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) প্রমুখ এক রাকাত বিতর পড়াকে মাকরূহ মনে করতেন। (কিতাবুল হুজ্জা আলা আহলিল মদীনা ১/১৯৩ আল-ইশরাফ ২/২৬২ ও আল-আউসাত ৮/১৬০, মাসাইলে আহমদ: ইবনে হানী পৃ. ১/৯৯ ফাতহুল বারী : ইবনে রাজাব ৬/১৯৯, এমনকি ইমাম আহমদ বলেন, বিতর ছুটে গেলে তিন রাকাতই কাযা করবে। ফাতহুল বারী :ইবনে রাজাব ৬/২২৭)
গ্রন্থকার – ৮
গ্রন্থকার পঞ্চম নম্বরে হযরত আবু-আইয়ুব আনছারী (রা.) এর নিম্নোক্ত বর্ণনাটি উল্লেখ করেন: “রাসূল (ছাঃ) বলেছেন: … সুতরাং যে পাঁচ রাক‘আত পড়তে চায় সে যেন তাই পড়ে। আর যে তিন রাক‘আত পড়তে চায় সে যেন তা পড়ে এবং যে এক রাক‘আত পড়তে চায় সে যেন তাই পড়ে”।
পর্যালোচনা
(ক) বর্ণনাটি মওকুফ তথা সাহাবীর কথা
প্রথমত বর্ণনাটিকে গ্রন্থকার ‘মারফু’ তথা নবীজীর কথারূপে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইমাম ইবনু আব্দিল বার বলেন: ইমাম নাসায়ী (রহ) বর্ণনাটি ‘মওকুফ’ তথা সাহাবীর বক্তব্য হওয়াকে বিশুদ্ধ মনে করেন (আততামহীদ ১৩/২১৯)। ইমাম দারা কুতনীও ‘মওকুফ’ হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন। [দেখুন-কিতাবুল ইলাল, দারাকুতনী হা.১০০৫ সুনানে দারাকুতনী হা.১৬৩০ মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার হা.১৩৯৪]
হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ) বলেন: ইমাম আবু-হাতেম, যুহলী, দারাকুতনী, বাইহাকী এবং আরো একাধিক ইমাম এটিকে মওকুফ বলেছেন। আর এটিই সঠিক। [আত-তালখীছুল হাবীর ২/৩৬-৩৭]
(খ) হাদীসের অংশবিশেষ গোপন করা
এ হাদীসেরই একটি অতিরিক্ত অংশ বিশুদ্ধ সনদে সুনানে নাসায়ী (হা.১৭১৩) তে রয়েছে। যার শব্দটি হল : (وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْمَأَ إِيمَاءً ،…) অর্থ: ‘…আর যার ইচ্ছা এক রাকাত পড়ে নেবে, আর যার ইচ্ছা একটি ইশারা করে নেবে’। [মুছান্নাফে আব্দির রাযযাক হা.৪৬৩৩ আস-সুনানুল কুবরা- বাইহাকী ৩/২৪ হা.৪৭৭৯-৪৭৮০ সহীহ ইবনে হিব্বান হা.২৪১১] তাহলে এ বর্ণনার আলোকে বিতর এর নামায ইশারা করে নিলেই আদায় হয়ে যাবে।
গ্রন্থকার হাদীসের শেষ অংশটি উল্লেখ করেননি। আমার যতদূর মনে হয় তিনি ইচ্ছাকরেই এ অংশটুকু এড়িয়ে গেছেন। কেননা তিনি টীকায় বরাত দিয়েছেন “ছহীহু ইবনে হিব্বান হ?২৪১১”। আর ইবনে হিব্বান এ নম্বরে হাদীসটির এ অংশটুকুসহই আছে।
গ্রন্থকার – ৯
গ্রন্থকার ছয় নম্বরে এক রাকাত বিতরের দলিল হিসেবে ইবনে মাসউদ (রা.) এর একটি বর্ণনা এভাবে পেশ করেন: “রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ বিজোড়। তিনি বিজোড়কে পসন্দ করেন। সুতরাং হে কুরআনের অনুসারীরা! তোমরা বিতর পড়”। গ্রন্থকার এখানে বলেন: “হাদীছটিতে সরাসরি আল্লাহর সাথে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ এক বিজোড় না তিন বিজোড় না পাঁচ বিজোড় তা কি বলার অপেক্ষা রাখে?” (পৃ.৩২৮)
পর্যালোচনা
(ক) ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনাও এক রাকাত বিতর এর দলিল নয়
উল্লেখযোগ্য কোন মুহাদ্দিস বা ফকীহ এ হাদীস দিয়ে এক রাকাত বিতর এর পক্ষে দলিল পেশ করেছেন বলে আমার জানা নেই।
হাদীসের বক্তব্য হল:‘আল্লাহ বেজোড়। তিনি বেজোড়কে পসন্দ করেন। (বিতর নামাযও যেহেতু বেজোড়) তাই বিতর নামায আদায় কর/ বিতরকেও বেজোড় করে পড়’। এখানে শুধু বিতর নামায আদায়ের প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়েছে। তাই ইমাম নববীসহ অনেক মুহাদ্দিসই হাদীসটিকে ‘বিতর নামাযে উৎসাহ প্রদান’ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। (খুলাছাতুল আহকাম: হা.১৮৫৪)
ইবনুল আছীর নিহায়া গ্রন্থে বলেছেন: “হাদীসে ‘বেজোড় কর’ দ্বারা উদ্দেশ্য বিতর পড়তে আদেশ করা। আর তা হল, ব্যক্তি দুই দ্ইু রাকাত নামায পড়বে। অতঃপর সবশেষে এক রাকাত পৃথক আদায় করবে অথবা পূর্বের রাকাতসমুহের সাথে মিলিয়ে আদায় করবে। এ অর্থেই অন্য হাদীসে রয়েছে : ‘ইসতিঞ্জায় ঢিলা ব্যবহার করার সময়ও তা বিতর করবে’ অর্থাৎ যে ঢিলা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে তা বেজোড় হবে। হয়ত এক বা তিন কিংবা পাঁচ। হাদীসে এ ধরণের শব্দ বারবার এসেছে”। (টীকা-১)
(খ) বর্ণনাকারী সাহাবীগণ হাদীস থেকে এক সংখ্যা বুঝেননি
এ হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, আবু হুরায়রা, হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব, হযরত আবু সাঈদ খুদরী এবং তাবেঈ মুহাম্মদ ইবনে সীরীন ও আতা ইবনে আবী রাবাহ সকলেই বুঝেছেন: ‘আল্লাহ বেজোড় তাই তিনি বেজোড়কে পসন্দ করতেন’। এর দ্বারা আল্লাহর সাথে তুলনা করে এক সংখ্যা বুঝানো হয়নি। বরং এক তিন পাঁচ সব বেজোড় সংখ্যাই আল্লাহর কাছে প্রিয়।
দেখুন:
১
ইবনে উমর থেকে এ হাদীস বর্ণনা করার পর: নাফে বলেন, ইবনে উমর সব কাজই বেজোড় করতেন। (মুসনাদে আহমদ হা.৫৮৪৬)
২
হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এ হাদীস বর্ণনা করার পর অনেকগুলো বেজোড় বস্তুর সাথে আসমানকেও বেজোড় হিসেবে গুণলেন। অতঃপর বলেন: যে, মিসওয়াক করবে, ইস্তিঞ্জায় ঢেলা ব্যবহার করবে ও যে কুলি করবে তারা যেন বেজোড় করে। (মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক হা.৯০৮৩) বলা বাহুল্য ঢেলা ব্যবহার ও কুলি করার ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে উত্তম হল তিনবার করা। একবার করা নয়।
৩-৪
উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এর উপস্থিতিতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন: আল্লাহ তা‘আলা নিজে বেজোড় এবং বেজোড়কে পসন্দ করেন। অতঃপর অনেকগুলো বেজোড় বস্তুর কথা উল্লেখ করেন। যেমন: আসমান ও যমীন সাতটি। সপ্তাহে সাত দিন। সূরা ফাতেহার আয়াত সংখ্যা সাত যাকে কুরআনে বলা হয়েছে: ‘সাবআন মিনাল মাসানী’। সাফা-মারওয়া ও কাবার তাওয়াফ সাত বার। প্রস্তর নিক্ষেপ সাত বার। সিজদা করার হুকুম করেছেন সাত অঙ্গের উপর ইত্যাদি। [দেখুন:আত-তাম্হীদ ২/২১০ হিলয়াতুল আউলিয়া- আবু নূআঈম হা.১১৫৭ জুযউ আবিল আব্বাস ইউনুস ইবনে কুদাইম আল-বাছরী]
৫
হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) লাইলাতুল কদর তালাশ করার হুকুম করে বলেন: “ তোমরা একে শেষ দশকের ‘বিতর’ তথা বেজোড় সংখ্যায় তালাশ কর। কেননা আল্লাহ ‘বিতর’ এবং তিনি ‘বিতর’ তথা বেজোড়কে পসন্দ করেন। (মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালীসী হা.১২৮০)
৬
নাফে বলেন: সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) তাওয়াফ সমাপ্ত করতেন বেজোড় সংখ্যায় আর বলতেন: ‘আল্লাহ তা‘আলা ‘বিতর’ এবং তিনি ‘বিতর’কে পসন্দ করেন। (মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক হা.৯৮০০)
৭
মুহাম্মদ ইবনে সীরীন এ হাদীসের কারণে সব কিছুকেই বেজোড় করে করতেন। এমনকি কোন কিছু খেলেও তা বেজোড় সংখ্যায় খেতেন। (মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক হা.৯৮০১)
৮
এ হাদীসের কারণেই হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহ বলেন: তিন আঙ্গুল (অর্থাৎ বেজোড় সংখ্যা) আমার কাছে চার আঙ্গুল (জোড় সংখ্যা) থেকে প্রিয়। (মুছান্নাফে আব্দির রাযযাক: হা.৯৮০৩)
(গ)
গ্রন্থকারের উল্লিখিত এ হাদীসটির বর্ণনাকারী হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)। আর তিনি এ হাদীস থেকে এক রাকাত বিতর বুঝবেন দূরের কথা তিনি এক রাকাতকে নামাযই মনে করেন না। যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।
(ঘ)
সর্বোপরি হাদীসে এ অংশ বিশেষের ব্যাখ্যা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই করেছেন। তিনি বলেন: আল্লাহর রয়েছে নিরান্নব্বইটি নাম। যে তা আয়ত্ত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর আল্লাহ ‘বিতর’ (তথা বেজোড়)। তিনি ‘বিতর’ (তথা বেজোড়কে) পসন্দ করেন। [সহীহ মুসলিম হা.২৬৭৯ বুখারী হা.৬৪১০]
(ঙ)
শুধু এক রাকাত বিতর পড়া যদি এ হাদীসের উদ্দেশ্য হত তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই করতেন। অথচ শুধু এক রাকাত বিতর পড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এক বারের জন্যও প্রমাণিত নয়, যা স্পষ্ট বলেছেন ইবনছ ছালাহ রহ.। [আত-তালখীছুল হাবীর ২/৩১] ইবনে হাজার সহীহ ইবনে হিব্বানের যে বর্ণনা দ্বারা আপত্তি করেছেন এটি মুলত একটি বর্ণনার সংক্ষিপ্তরূপ। সহীহ ইবনে হিব্বানে একই হাদীসের বিশদ বর্ণনায় পূর্ণ নামাযের বিবরণ উল্লিখিত রয়েছে। [সহীহ ইবনে হিব্বান, শায়খ শুআইব সম্পাদিত হা. ২৫৯২, ২৬২৬ ও হা. ২৪২৪ এর টীকা]
সুতরাং বিতরের যে পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অধিকাংশ সাহাবী থেকে প্রমাণিত নেই। বরং তাদের আমল এর বিপরীত। সে পদ্ধতিকেই হাদীসের উদ্দিষ্ট অর্থ সাব্যস্ত করা এবং এ দাবী করা যে, এটিই সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হিসেবে প্রমাণিত; এ যে কত সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি তা বলার অপেক্ষা রাখে না।
এক সালাম ও দুই বৈঠকে তিন রাকাতে বিতর
গ্রন্থকার – ১০
গ্রন্থকার ‘তিন রাক‘আত বিতর পড়ার সময় দুই রাক‘আতের পর তাশাহ্হুদ পড়া’ শিরোনামে বলেন: “তিন রাক‘আত বিতর একটানা পড়তে হবে। মাঝখানে কোন বৈঠক করা যাবে না। এটাই সুন্নত। (পৃ.৩৩০)
পর্যালোচনা
দুই তাশাহ্হুদ ও এক সালামে তিন রাকাত বিতর বিষয়ে নবীজী থেকে, সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে সহীহ ও সুস্পষ্ট অনেক দলিল পূর্বে সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে।
গ্রন্থকার – ১১
(এক) ইবনে মাসউদ (রা) এর মওকুফ বর্ণনা
গ্রন্থকার তিন রাকাত বিতর এর দলিল পর্যালোচনায় বলেন:“(ক) ইবনে মাসউদ বলেন, মাগরিবের ছালাতের ন্যায় বিতরের ছালাত তিন রাক‘আত।” (পৃ.৩৩০-৩৩১)
পর্যালোচনা : মিথ্যা উদ্ধৃতি দিয়ে সহীহকে যঈফ সাব্যস্ত করা
(ক)
টীকায় গ্রন্থকার শুধু আল-মুজামুল কাবীরের বরাত দিয়েছেন। অথচ হাদীসটি রয়েছে: মুছান্নাফে ইবনে আবী শাইবা (হা.৬৭৭৯) মুয়াত্তা মালেক: মুহাম্মদের বর্ণনা (হা.২৬২) শরহু মা‘আনিল আসার (হা.১৬১৩) আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকী (৩/৩০ হা.৫০০৭)।
(খ)
তাহকীকের নামে গ্রন্থকার বলেন:“ ইবনুল জাওযী বলেন, এই হাদীছ ছহীহ নয়।”। কিন্তু এ হাদীস সম্পর্কে ইবনুল জাওযীর এ বক্তব্য আমি খুঁজে পাইনি। টীকায় গ্রন্থকার এর যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন: (هذا حديث لا يصح : তানক্বীহ, পৃঃ ৪৪৭) তার রহস্য আমি খুঁজে পেলাম না। কারণ:
১
তানক্বীহ নামে ইবনুল জাওযীর কোন গ্রন্থ নেই।
২
অনেক তালাশ করে গ্রন্থকারের টীকায় উল্লিখিত ‘আপত্তিটি’ ইবনুল জাওযী (রহ.) এর ‘আল ইলালুল মুতানাহিয়া’ কিতাবে পাওয়া গেল। কিন্তু সেখানে তিনি এ মন্তব্যটি ইবনে মাসউদ এর মরফু বা মওকুফ কোন হাদীসের উপরই নয় বরং হযরত আয়শা থেকে বর্ণিত এ ধরণের ভিন্ন একটি ‘মরফু’ বর্ণনা সম্পর্কে করেছেন।
(গ) ইবনে মাসউদ (রা) এর উল্লিখিত বর্ণনাটি সহীহ:
১
নূরুদ্দীন হাইছামী (মৃত.৮০৭) বলেন: (ورجاله رجال الصحيح) :এর সকল বর্ণনাকারীগণ সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারীর মানে উত্তীর্ণ। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ হ.৩৪৫৫)
২
ইমাম বাইহাক্বী বলেন: (هذا صحيح عن عبد الله بن مسعود من قوله): আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এর বক্তব্য হিসেবে এটি সহীহ। (আস-সুনানুল কুবরা ৩/৩০) বাইহাকী (রহ.) এ বক্তব্যটি গ্রন্থকারের জানা থাকা সত্ত্বেও তিনি তার ইঙ্গিতও করেননি: যার প্রমাণ সামনে পেশ করা হবে।
৩
বিশেষত মুয়াত্তা ও ইবনে আবী শাইবার সকল বর্ণনাকারী বুখারী ও মুসলিমের রাবী। শুধু মালিক ইবনুল হারিস মুসলিমের রাবি। (দেখুন, মুয়াত্তা-ইমাম মুহাম্মদের বর্ণনা, তাহক্বীক:তাক্বী উদ্দীন নদবী হা. ২৬২)।
গ্রন্থকার – ১২
ইবনে উমরের বর্ণনা
গ্রন্থকার দুই নম্বরে বলেন: “(খ) আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, মাগরিবের ছালাত দিনের বিতর ছালাত। তাহক্বীক্ব: অনেকে উক্ত বর্ণনা উল্লেখ করে বিতর ছালাত মাগরিব ছালাতের ন্যায় প্রমাণ করতে চান। অথচ তা ত্রুটিপূর্ণ। বর্ণনাটি কখনো মারফু‘ সূত্রে এসেছে, কখনো মাওকুফ সূত্রে এসেছে। তবে এর সনদ যঈফ। মুহাদ্দিস শুআইব আরঊত বলেন, ঐ অংশটুকু ছহীহ নয়।”
পর্যালোচনা
(ক) বিভ্রান্তিপূর্ণ তাহক্বীক
এখানেও তিনি তাহকীকের নামে কি পরিমাণ গোলমাল করেছেন তা পাঠকের সামনে তুলে ধরছি:
(১)
গ্রন্থকারের বক্তব্য “অথচ তা ত্রুটিপূর্ণ” : কোন কথাটিকে তিনি ত্রুটিপূর্ণ বোঝাতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট নয়। তিনি কি বলতে চাচ্ছেন বর্ণনাটি ত্রুটিপূর্ণ? প্রকৃতপক্ষে তার বক্তব্যই ত্রুটিপূর্ণ!
(২)
তিনি বলেছেন: “বর্ণনাটি কখনো মারফু সূত্রে এসেছে, কখনো মাওকুফ সূত্রে এসেছে”
মূলত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর থেকে দুটি বর্ণনা রয়েছে:
(ক)
একটি ‘মরফু’ তথা নবীজীর বক্তব্য, আর একটি ‘মওকুফ’ তথা ইবনে উমরের বক্তব্য।
(খ)
একটি বর্ণনা করেছেন তাবেয়ী মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহ.) (মুসনাদে আহমদ ও অন্যান্য) আর অপরটি আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার (মুয়াত্তা মালেক)।
(গ)
দুটি বর্ণনার বক্তব্যেও যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।
মরফু বর্ণনা:
عَن مُحَمَّد بْن سِيرِينَ عَن ابْنِ عُمَر عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ النَّهَارِ، فَأَوْتِرُوا صَلَاةَ اللَّيْلِ .
ইবনে সীরীন রহ. বলেছেন: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: মাগরিবের নামায দিনের বিতর। সুতরাং তোমরা রাতের নামাযকেও বিতর করে পড়।
মওকুফ বর্ণনা:
عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ صَلَاةِ النَّهَارِ
আব্দুল্লাহ বিন দিনার বলেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাঃ বলতেন, মাগরিবের নামায দিনের নামাযের বিতর।
(ঘ)
বর্ণনা দুটিতে কোন বিরোধও নেই বরং আপন আপন স্থানে দুটি বর্ণনাই সঠিক।
সুতরাং দুটিকে এক বর্ণনা বানিয়ে দেয়ার কোন যুক্তি নেই। এ কারণে ইমাম ইবনু আব্দিল বার (মৃ.৪৬৩) দুটি বর্ণনাকেই উল্লেখ করে যথার্থ ব্যাখ্যা করেছেন। (আল-ইসতিযকার ৫/২৮৩)
(৩)
গ্রন্থকার চরম দুঃসাহসিকতার সাথে ‘মরফু ও ‘মওকুফ’ পার্থক্য না করেই বলেন: “তবে এর সনদ যঈফ”! ফলে বুঝা যায় মওকুফ বর্ণণাটিও যঈফ!
(খ) মওকুফ বর্ণনাটি কি যঈফ?
পূর্বেই বলেছি: এখানে দুটি বর্ণনার দুটি ভিন্ন ভিন্ন সনদ। কোন সনদটি যঈফ? কে বলেছেন যঈফ এবং কেন যঈফ? :এর কিছুই গ্রন্থকার বলেননি। এর জন্য কোন বরাতও গ্রন্থকার দেননি। তাহলে কি এটি তার ‘নিজস্ব’ ভিত্তিহীন বক্তব্য! যা অনুসরণ করতে তিনি পাঠককে বাধ্য করতে চান?! কোন ইমাম বা মুহাদ্দিস কি এ মওকুফ বর্ণনাটিকে যঈফ বলেছেন এর প্রমাণ গ্রন্থকার দিতে পারবেন?
দেখুন: গ্রন্থকার যে বর্ণনাটি উল্লেখ করে টীকায় মুয়াত্তা (হা/২৫৪) এর বরাত দিয়েছেন: এটি ইমাম মালেক তাবেয়ী আব্দুলাøহ ইবনে দীনার থেকে। আর তিনি সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। এখানে ইমাম মালেক ও সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উমর বাদ দিলে থাকে কেবল: আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার। তিনি বুখারী মুসলিমসহ ছয় কিতাবের রাবি। ইমাম আহমদ, ইবনে মাঈন, আবু-যুরআ, নাসায়ী, (ইবনে হিব্বান, ইজলী,) ইবনে সা‘দ প্রমুখ সকল ইমামই তাঁকে সিকাহ (বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য) বলেছেন। (তাহযীবুল কামাল) ইমাম যাহাবী তাঁকে ইমাম ও হুজ্জাহ উপাধী দিয়েছেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা) ইবনে হাজার আসকালানী (তাকরীবে) ও সয়ূতী (ইস‘আফে) তাঁকে সিকাহ বলেছেন। এমন বর্ণনাকারীকে ‘যয়ীফ’ বলার সাধ্য কি গ্রন্থকারের আছে?!
তাহলে এ বর্ণনায় কাকে তিনি যঈফ সাব্যস্ত করছেন: এই আব্দুল্লাহ ইবনে দীনারকে নাকি মালেক বা সাহাবী ইবনে উমরকে?
(গ) মরফু বর্ণনা
আর মারফু বর্ণনা সম্পর্কেও একই কথা, কে একে যঈফ বলেছেন এবং কেন বলেছেন?
ইমাম আহমদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন: ইয়াযীদ ইবনে হারূন-হিশাম ইবনে হাসসান-মুহাম্মদ ইবনে সীরীন সূত্রে ইবনে উমর (রা.) থেকে। এরা প্রত্যেকেই বুখারী ও মুসলিম এর বর্ণনাকারী ও নির্ভরযোগ্য। এদের কাকে গ্রন্থকার যঈফ সাব্যস্ত করতে চেয়েছেন এবং কিভাবে?
মুসনাদে আহমদে বর্ণনাটি একাধিকবার এসেছে। এবং কিতাবের মুহাক্কিক শায়খ শুআইব আরনাউত বলেছেন: এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত এবং বুখারী মুসলিমের ‘রাবী’। (দেখুন:হা.৪৮৪৭, ৪৯৯২) গ্রন্থকার শুআইব আরনাউতের যে মন্তব্য উল্লেখ করেছেন তা বিভ্রান্তিকর। এর আলোচনা সামনে আসছে ইনশাল্লাহ।
বর্ণনাটিকে যারা সহীহ বলেছেন:
১
হাফেজ আলাউদ্দীন মারদীনী (মৃত.৭৫০) বলেন: (وهذا السند على شرط الشيخين) : বর্ণনাটির সনদ বুখারী মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। (আল-জাওহারুননাকী ৩/৩১)
২
হাফেজ ইরাকী (মৃত.৮০৪) (আল-মুগনী আন হামলিল আসফার- তাখরীজুল ইহইয়া-২/৬৯)
৩
মুহাদ্দিস যুরকানী (মৃত.১১৬২) ইরাকীর বক্তব্যকে গ্রহণ করেছেন (শারহুয যুরকানী আলাল মুয়াত্তা-ছালাতুননাবী ফিল বিতরি অধ্যায়)
৪
মুহাদ্দিস আহমদ গুমারী (মৃত. ১৩৮০) বলেন: (هذا سند رجاله رجال الصحيح) : এ সনদের সকল বর্ণনাকারী সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারীদের মানোত্তীর্ণ। (আল-হিদায়া ফি তাখরীজি আহাদীসিল বিদায়া ৪/১৪২)
৫
আল্লামা আব্দুল হাই লখনবী ইরাকীর বক্তব্যকে গ্রহণ করেছেন। (আত্তা‘লিকুল মুমাজ্জাদ পৃ.১৪৭)
৬
শায়খ নাসীরুদ্দীন আলবানী (মৃ.১৪২১)। (ছহীহুল জামেইছ ছাগীর হা.১৪৫৬/৩৮৩৪, ৬৭২০)
৭
গ্রন্থকারের মতাদর্শী আহলে হাদীস আলেম আব্দুল্লাহ আল-কাফী একই উদ্দেশ্যে প্রণিত ‘ছহীহ সুন্নাহর আলোকে বিতর ছালাত’ পুস্তকে (পৃ.৩২) বর্ণনাটি উল্লেখ করেন এভাবে: ছহীহ হাদীছে বর্ণিত আছে, …।
৮
শায়খ শুআইব আরনাউত বলেন: “এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত এবং বুখারী মুসলিমের ‘রাবী’।” (দেখুন:মুসনাদে আহমদের টীকা হা.৪৮৪৭) অন্যত্র এ বর্ণনার মতন বিষয়ে শায়খের বক্তব্য সামনে আসছে।
এর সমর্থনে আরো দুটি হাদীস
১
হযরত ইবনে উমর রা. এর বর্ণনা
আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন: “আমি নবীজীর সাথে সফরে-হজরে নামায পড়েছি। …মাগরিবের নামায সফরে-হজরে সর্বদাই তিন রাকাত। সফরে-হজরে এতে (রাকাত সংখ্যায়) কোন হ্রাস পায় না। এটি হল দিনের বিতর। এর পর আরো দুই রাকাত আছে।” ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে ‘হাসান’ বলেছেন। [সুনানে তিরমিযী হা.৫৫২]
আহলে হাদীস আলেম আব্দুর রহামন মুবারকপূরী হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানীর উদ্ধৃতিতে একে গ্রহণযোগ্য ও হাসান গণ্য করে এর ব্যাখ্যা করেছেন: নবীজীর বক্তব্য : “মাগরিব দিনের বিতর” : এখানে মাগরিবের নামায সরবে কেরাত বিশিষ্ট রাতের নামায হওয়া সত্ত্বেও একে দিনের বিতর বলার কারণ এটি দিনের নিকটবর্তী নামায।
[তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৩৭৫, ৩/১২০ ফাতহুলবারী ৪/১২৬] এ বর্ণনাকে গ্রহণ করে ইবনে হাজারের আরো বক্তব্য দেখুন: [ফাতহুল বারী ২/৪৯ ৩/২১]২
হযরত আয়শা রা. এর বর্ণনা
হযরত আয়শা (রা.) বলেন: “আর মাগরিবের নামায (সফরেও তাতে কসর নেই), কেনানা তা দিনের বিতর”। (عن عائشة قالت : فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين فلما أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار) [সহীহ ইবনে হিব্বান, হা.২৭৩৮ শায়খ শুআইব আরনাউত বলেন: এর সনদ হাসান, ফাতহুলবারী ১/৪৬৪]
হাদীস দুটিতে মাগরিবকে দিনের বিতর বলা তখনি সঠিক হবে যখন একথা মেনে নেওয়া হবে যে রাতের নামাযেরও একটি বিতর আছে।
সুতরাং উভয় হাদীস থেকেই একথা বুঝা যায় যে, বিতর নামায হল রাতের বিতর।
গ্রন্থকার – ১৩
(ঘ) গ্রন্থকার শেষে বলেন: “তবে এর সনদ যঈফ। মুহাদ্দিস শুআইব আরনাঊত বলেন, ঐ অংশটুকু ছহীহ নয়।” (পৃ.৩৩০)
পর্যালোচনা
গ্রন্থকার এখানে শায়খ শুআইব -এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করতে যেয়ে তিনটি সমস্যার সৃষ্টি করেছেন:
১
“তবে এর সনদ যঈফ” কথাটি গ্রন্থকারের নিজস্ব বক্তব্য, কারো থেকে উদ্ধৃত নয়।
২
শায়খ শুআইব এর পূর্ণ বক্তব্য এখানে গ্রন্থকার উল্লেখ করেননি। কেননা পূর্ণ বক্তব্য উল্লেখ করলে আসল তথ্য ফাঁস হয়ে যেত। কারণ শায়খ শুআইব: এর আগে বলেছেন: (صحيح) : অর্থাৎ: ‘এ হাদীসটি সহীহ’। আর এর পরই বলেছেন, (… وهذا الإسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير هارون بن إبراهيم الأهوازي، فمن رجال النسائي، وهو ثقة. ) :‘… এ সনদের সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত ও বুখারী মুসলিমের ‘রাবী’। কেবল হারুন ইবনে ইবরাহীম ব্যতিত। আর তিনিও নাসায়ীর ‘রাবী’ এবং বিশ্বস্ত’। (হা.৫৫৪৯)
৩
শায়খ শুআইব এর এ বক্তব্যটি মূলত আলোচ্য হাদীসের বিষয়ে নয়। বরং ইবনে সীরীন সূত্রে ইবনে উমরের ভিন্ন আরেকটি বর্ণনা সম্পর্কে। ভিন্ন হাদীস। সম্পর্কে তোলা আপত্তিকে এ হাদীসে লাগিয়ে দিয়ে শায়খ শুআইবের তাহকীকের অপব্যবহার করেছেন।
শায়খ শুআইব -এর পূর্ণ বক্তব্য ও তার ব্যাখ্যা
গ্রন্থকারের বক্তব্য: ‘মুহাদ্দিস শুআইব আরঊত বলেন, ঐ অংশটুকু ছহীহ নয় ’ -এর মানে কি? ‘ঐ’ বলতে তিনি কি বুঝিয়েছেন বিষয়টি অস্পষ্ট?
আসলে শায়খ শুআইব বলেছেন:
صحيح دون قوله: “صلاة المغرب وتر صلاة النهار فأوتروا صلاة الليل” ، فقد سلف الحديث عنه في الرواية (৪৮৪৭) بأنه رواه عدة موقوفا، وهذا الإسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير هارون بن إبراهيم الأهوازي، فمن رجال النسائي، وهو ثقة.
অর্থ: “(হাদীসটি মরফুরূপেই) সহীহ, শুধু এ কথাটি ব্যতিত যে, ‘মাগরিবের নামায দিনের বিতর, তোমরা রাতের নামাযকেও বিতর কর’। (কারণ) পূর্বে ৪৮৪৭ নং বর্ণনায় (টীকায়) এ বিষয়ে বলা হয়েছে যে, একাধিকজন হাদীসটি মওকুফরূপে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের সনদের সকল বর্ণনাকারী সিকাহ (বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য) ও বুখারী মুসলিমের বর্ণনাকারী। কেবল হারুন বিন ইবরাহীম ব্যতিত। তিনি সুনানে নাসায়ীর রাবী ও সিকা।” (মুসনাদে আহমদ হা.৫৫৪৯)
শায়খ শুআইবের বক্তব্য স্পষ্ট যে, তিনি হাদীসটির সনদকে যঈফ বলেননি বরং সহীহ বলেছেন। বক্তব্য সম্পর্কে সহীহ নয় বলে মারফূরূপে (অর্থাৎ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যরূপে) বর্ণিত হওয়াকে সহীহ নয় বুঝিয়েছেন। মওকুফ বা সাহাবীর বক্তব্যরূপে বর্ণিত হওয়া তার দৃষ্টিতেও সহীহ।
গ্রন্থকার – ১৪
হযরত ইবনে মাসউদ এর ‘মারফূ’ বর্ণনা
গ্রন্থকার বলেন: “ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, রাত্রির তিন রাক‘আত বিতর দিনের বিতররের ন্যায় যেমন মাগরিবের ছালাত। তাহক্বীক: ইমাম দারাকুৎনী বর্ণনা করেন বলেন, ইয়াইইয়া ইবনু যাকারিয়া যাকে ইবনু আবীল হাওয়াজিব বলে, সে যঈফ। সে আ‘মাশ ছাড়া আর কারো নিকট থেকে মারফূ হাদীছ বর্ণনা করেনি। ইমাম বয়হাক্বী বলেন, ইয়াহইয়া ইবনু যাকারিয়া ইবনু হাযিব (সঠিক হল: ইবনু আবিল হাওয়াযিব!) কুফী আ‘মাশ থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেছে। কিন্তু সে যঈফ। তার বর্ণনা আ‘মাশ থেকে মারফূ অন্যান্য বর্ণনার বিরোধিতা করে। এছাড়া ইমাম দ্বারাকুৎনী উক্ত বর্ণনার পূর্বে তার বিরোধী ছহীহ হাদীছ উল্লেখ করেছেন। সেখানে মাগরিবের মত করে বিতর পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন: … ” (পৃ.৩৩০)
পর্যালোচনা
ইবনে মাসউদ রা. এর বর্ণনাটি ‘মারফূ’ ও ‘মাওকুফ’ উভয়ভাবেই বর্ণিত হয়েছে। মাওকুফ হিসেবে ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে এটি প্রমাণিত ও বিশুদ্ধ এতে কোন সন্দেহ নেই। আর দলিলের জন্য ‘মওকুফ’ বর্ণনাটিই যথেষ্ট। সাথে রয়েছে ইবনে উমর (রা.)-এর পূর্বোল্লেখিত মারফু ও মাওকুফ বর্ণনা এবং অন্যান্য দলিল।
ইবনে মাসউদ (রা.) এর মারফু বর্ণনা বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হল: এটি হাসান যা সর্বসম্মতিক্রমে দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য।
এখানে গ্রন্থকার তাহক্বীকের নামে কি ‘কীর্তি’টা আঞ্জাম দিয়েছেন তা সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ।
(ক) ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া কি যঈফ?
গ্রন্থকার দারাকুতনীর উদ্ধৃতিতে বলেছেন: ‘সে যঈফ’।
ইমাম দারাকুতনী (রা.) ‘সুনানে’ তাঁকে যঈফ বলেছেন। অনেকেই তার বিষয়ে দারাকুতনীর সঙ্গে একমত হননি। যেমন:
১
ইামাম ইবনে হিব্বান তাঁকে ‘সিকাহ’ (বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য) বর্ণনাকারীদের মধ্যে গণ্য করেছেন। (কিতাবুছছিকাত)
২
ইমাম হাকেম নিশাপুরী: তার একটি হাদীসকে সহীহুল ইসনাদ বলেছেন। (মুসতাদরাক আলাস-সহীহাইন হা.৩০৪৫)
৩
ইমাম যাহাবী রহ. হাকিমের মন্তব্যকে সমর্থন করে বলেন: এটি সহীহ। (তালখীছুল মুসতাদরাক)
(খ) মারাত্মক ভুল তরজমা
গ্রন্থকার বলেন, “ ইমাম দারাকুৎনী … সে আ‘মাশ ছাড়া আর কারো নিকট থেকে মারফূ হাদীছ বর্ণনা করেনি।”
এ তরজমায় তিনি হাস্যকর ভুল করেছেন! সহীহ তরজমা হল: (ولم يروه عن الأعمش مرفوعا غيره) ‘আ‘মাশ থেকে তিনি ছাড়া অন্য কেউ এ হাদীসটি মরফূরূপে বর্ণনা করেনি’।
(গ) তরজমায় মারাত্মক ভুল
গ্রন্থকার যে বলেছেন: “ইমাম বায়হাক্বী বলেন, … তার বর্ণনা আ‘মাশ থেকে মারফূ অন্যান্য বর্ণনার বিরোধিতা করে।”
বাইহাকী’র বক্তব্যের এটিও মারাত্মক ভুল তরজমা। আরবীতে কথাটি এমন : (وروايته تخالف رواية الجماعة عن الأعمش) : এর সঠিক তরজমা হল: ‘আ‘মাশ থেকে তাঁর বর্ণনা অন্যান্য একাধিক রাবীর বর্ণনার বিরোধী’।
(ঘ) তাহলে কি এটি ইচ্ছাকৃত করা হয়েছে?!
গ্রন্থকার এখানে বাইহাকী’র পূর্ণ বক্তব্য উল্লেখ না করে আংশিক এনেছেন। টীকায় (নং ১২৭৭) বরাত দিয়েছেন, আস-সুনানুল কুবরা (৩/৩১)। ঠিক এ পৃষ্ঠাতেই বাইহাকী (রহ.) উপরিউক্ত মন্তব্য করার পূর্বে বলেছেন, “হাদীসটি মওকুফ তথা ইবনে মাসউদ (রা.) এর বক্তব্য হিসেবে সহীহ।” সুতরাং তিনি তার এ বক্তব্যটি অবশ্যই দেখেছেন। কিন্তু গ্রন্থকার এখানে তা উল্লেখ করেননি। আর ৩৩০-৩৩১ পৃষ্ঠায় ইবনে মাসউদের মওকুফ বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন, সেখানেও এ বক্তব্য উল্লেখ করেননি। বরং অন্যায়ভাবে অন্য আরেকটি হাদীসের ক্ষেত্রে করা আপত্তি এ হাদীসের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন !
দুই রাকাতে বৈঠকের দলিল
গ্রন্থাকার – ১৫
সবশেষে তিনি মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে ও নবীজীর নামায বই দুটির উপর অন্যায় আপত্তি করে তা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বলেন: উবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী (রহ.) বলেন, “তিন রাক‘আত বিতরের দ্বিতীয় রাক‘আতে বৈঠক করার পক্ষে আমি কোন মারফূ ছহীহ দালীল পাইনি”। (পৃ.৩৩১)
পর্যালোচনা
এ বিষয়ে কয়েকটি কথা:
১
গ্রন্থকার বলেছেন, ‘মরফু ছহীহ দলিল’ পাননি। দ্বিতীয় রাকাতের বৈঠক শরঈ দলিলের আলোকেই করা হয়ে থাকে। হানাফী মাযহাবের অনুসরণ করেন না এমন অনেক বড় বড় ইমাম, হাফিজুল হাদীস ও মুহাদ্দিসই এর দলিল পেয়েছেন। যেমন ইমাম ইবনে আব্দিল বার, ইমাম ইবনুল জাওযী, ইমাম যাহাবী, ইবনে হাযম জাহেরী প্রমুখ।
২
এ বিষয়ে অনেক মরফূ সহীহ হাদীসে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যা পূর্বে বিতর নামাযের মূল আলোচনায় গত হয়েছে। এখানেও পূর্বোল্লেখিত ইবনে উমর (রা.) এর মরফু বর্ণনাটি এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ও সহীহ দলিল।
৩
‘দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে তৃতীয় রাকাত পড়বে’ এর পক্ষে কোন মরফু সহীহ ও ছরীহ (স্পষ্ট) দলিল আছে কি? গ্রন্থকারতো তার এ গ্রন্থে দেখাতে পারেননি! আর ‘দুই রাকাতে বৈঠক না করেই তিন রাকাত পড়বে’ এ বিষয়ে মরফু নয় কোন মওকুফ সহীহ বর্ণনাও তারা পেশ করতে পারবেন না।
৪
মুবারকপুরী সাহেব বলেছন: ‘মরফু’ দলিল পাননি। তার মানে মওকুফ দলিল পেয়েছেন। আর মওকুফ তথা সাহাবীদের বক্তব্যতো অনেক আছে এর পক্ষে। তাহলে কি তিনি যেখানে মরফু পাওয়া যায় না সেখানেও মুওকুফ তথা সাহাবীর বক্তব্যকে দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না? গ্রন্থকারও কি তার সাথে একমত? অথচ তিনি তার গ্রন্থের ৩৩২ ও ৩৩৩ পৃষ্ঠার টীকায় তিনটি মওকুফ বর্ণনা দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছেন! তাহলে কি নিজের বেলায় চলে কিন্তু অন্যের বেলায় না!
৫
এখানে তিনি মরফু দলিল তালাশ করেন, অথচ কুনূত পড়ার সহীহ নিয়ম শিরোনামে তিনি আলবানী সাহেবের ‘ইরওয়াউল গালীল [২/৭১] পৃষ্ঠার বরাত দিয়েছেন, যেখানে তৃতীয় শতকের মুহাদ্দিস ইসহাক ইবনে রাহুইয়াহ রহ. এর আমল বর্ণিত হয়েছে। তাহলে তৃতীয় শতকের মুহাদ্দিসের বক্তব্য বা ফতোয়াও নয়, বরং তার একটি আমল দলিল হয়ে যায়, অথচ এখানে ‘কেবল মরফু দলিল তলব করতে হয় এটা কেমন কথা!
তিন রাকাত বিতরের প্রথম পদ্ধতি: এক সালামে এক বৈঠকে তিন রাকাত?
গ্রন্থকার – ১৬
গ্রন্থকার বলেন: “এক সঙ্গে তিন রাকআত পড়ার ছহীহ দলীল:
عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن.
হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) তিন রাক‘আত বিতর পড়তেন। তিনি শেষের রাক্‘আতে ব্যতীত বসতেন না।” [টীকা:১২৮১. মুস্তাদরাক হাকেম হা/১১৪০; বায়হাক্বী হা/৪৮০৩, তয় খ-, পৃঃ৪১; সনদ ছহীহ, তা‘সীসুল আহকাম ২/২২৬ :(২/২৯৭] (পৃ. ৩৩১)
পর্যালোচনা
(ক)
গ্রন্থকার উল্লিখিত হাদীসের যে বরাত দিয়েছেন তন্মধ্যে আমি প্রথমটিতে (অর্থাৎ মুস্তাদরাক হাকেম হা/১১৪০) হাদিসটি এ শব্দে পাইনি। তিনি বলেছেন: “ لا يقْعُد (বসতেন না)” আর মুস্তাদরাকের মুদ্রিত কপিতে আছে: “ لا يُسَلم (সালাম ফিরাতেন না)”। আর (সালাম ফিরাতেন না) শব্দ দিয়ে দুই রাকাতের পর তাশাহহুদ পড়তেন না এর পক্ষে দলিল হয় না। বরং এ হাদীস থেকেত একথাই প্রমাণিত হয় যে, বিতরের দুই রাকাতে বসতে হয়, কিন্তু সালাম ফিরাতে হয় তিন রাকাত পূর্ণ করে। কেননা এর অর্থ যদি দুই রাকাতে না বসা হত, তাহলে “ لا يُسَلم (শেষ না করে সালাম ফিরাতেন না)”: এ কথার কোন অর্থই হয় না। কারণ সালামত আর দাড়ানো অবস্থায় হয় না যে, ‘সালাম ফিরাতেন না’ বলে দিতে হবে।
মোট কথা বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন সময়ে মুদ্রিত মুসতাদরাকের মোট পাঁচটি কপিতে আমি হাদীসটি (সালাম ফিরাতেন না) শব্দে এভাবেই পেয়েছি। দেখুন:
১
আল মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন, ১/৪৪৭ হা.১১৪০ তাহক্বীক: আব্দুল ক্বাদের আতা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বাইরুত, লেবানন।
২
আল মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন: ১/৪৩৭ হা.১১৪১, প্রকাশক: দারুল হারামাইন, মিশর, প্রথম প্রকাশ :১৯৯৭।
৩
আল মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন, ১/৩০৪ তাহক্বীক: ইউসুফ আব্দুর রহমান, বাইরুত, লেবানন।
৪
আল-মুসতাদরাক, হা. ১/৪১৪ দারুল ফিকর, বাইরুত, লেবানন।
৫
আল-মুসতাদরাক, ১/৩০৪ দাইরাতুল মা‘আরিফিল উসমানিয়া, হায়দারাবাদ, ভারত, প্রকাশকাল:১৩৩৪ হি.) এমনকি নাসীরুদ্দীন আলবানী সাহেবও ইরওয়াউল গালিলে (১/১৫১) এ শব্দেই উল্লেখ করেছেন।
কিন্তু গ্রন্থকার মুস্তাদরাকের কোন কপিতে “ لا يقْعُد (বসতেন না)” পেলেন তা বলেননি। পরবর্তীতে তার বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে তিনিও কোন মুদ্রিত কপিতে“ لا يقْعُد (বসতেন না)” শব্দটি পাননি। কারণ তিনি বলেছেন: “মুস্তাদরাকে হাকেমে বর্ণিত لا يقْعُد (বসতেন না) শব্দকে পরিবর্তন করে পরবর্তী ছাপাতে لا يُسَلم (সালাম ফিরাতেন না) করা হয়েছে।” আবার কোন মাখতূতা বা পা-ুলিপিতে এ শব্দটি তিনি দেখেছেন তাও বলেননি। তার কথা ‘পরবর্তী ছাপা’ দ্বারা বুঝা যায় পূর্ববর্তী ছাপাতে لا يقْعُد (বসতেন না) শব্দ ছিল। কিন্তু সেটি পূর্ববর্তী কোন ছাপা তা তিনি কিছুই বলেননি!
তবুও কেন তিনি হাদীসটি “لا يقْعُد (বসতেন না” শব্দে এনে মুস্তাদরাকের বরাত উল্লেখ করলেন আমার বুঝে আসে না? যদি তার কাছে এ শব্দটি ভুল মনে হয়ে থাকে, তাহলে তিনি কিতাবের মূল শব্দটি উল্লেখ করার পর তা ভুল প্রমাণ করে দেখাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে নিজ থেকে হাদীসের শব্দ পরিবর্তন করে দিয়েছেন। পরে জোড়াতালি দেওয়ার জন্য উপযুক্ত দলিল না দিয়ে কতগুলো অযৌক্তিক কথা বলে শাস্ত্রীয় লোকদের জন্য কিছু হাসির যোগান দিলেন।
গ্রন্থকারের সমচিন্তার লেখক আব্দুল্লাহ আল-কাফি এখানে তারচেয়েও মারাত্মক অন্যায় কাজ করেছেন। তিনি বিতর ছালাত বইয়ে (পৃ.৩১) লেখেন: “এর মধ্যে তাশাহুদের জন্যে বসতেন না”। অর্থাৎ তিনি বসতেন না শব্দের সাথে ‘তাশাহুদের জন্যে’ কথাটি নিজের থেকে জুড়ে দিলেন, যার আরবী হবে: (للتشهد)। টীকায় বলেন: “হাদীছটি বর্ণনা করেন ইমাম হাকেম, তিনি হাদীছটিকে ছহীহ বলেন।” এতে তিনি কোন খ- ও পৃষ্ঠার উল্লেখ করেননি। এ ছাড়া আর কোন বরাতও উল্লেখ করেননি। তাহলে কোথায় পেলেন তিনি এ শব্দ? এভাবেই তাহলে নবীজীর নামাযকে জাল হাদীস থেকে মুক্ত করতে গিয়ে জাল হাদীস যুক্ত করে দেওয়া হয়!
(খ) কোন শব্দটি সহীহ: “ لا يقْعُد” নাকি “ لا يُسَلم”?
এখানে কয়েকটি বিষয় পরিস্কার হওয়া দরকার:
এক
মুস্তাদরাকে হাকেমে এ হাদীসটি কোন শব্দে এসেছে?
দুই
এ হাদীসের অন্যান্য সকল সনদ বিবেচনায় কোন শব্দটি বিশুদ্ধ:“ لا يقْعُد (বসতেন না)” নাকি “ لا يُسَلم (সালাম ফিরাতেন না) ”?
তিন
“ لا يقْعُد (বসতেন না)” শব্দের অর্থের মধ্যে কি: ‘তাশাহুদের জন্য’ বসতেন না, এটি সুস্পষ্ট? নাকি ‘সালাম ফিরানোর জন্য বসতেন না, এ অর্থেরও যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে?
চার
হাদীস বর্ণনাকারী ইমাম বাইহাকী (রহ.) নিজে এ হাদীস থেকে কোন তরীকার বিতর বুঝেছেন?
পাঁচ
হাদীসটি বর্ণনাকারী ইমাম বাইহাকী (রহ.) বর্ণনাটির কি মান উল্লেখ করেছেন?
(এক) হাদীসের শব্দ “ لا يُسَلم (সালাম ফিরাতেন না)” ই সঠিক
আমার অনুসন্ধানে মনে হয়, মুসতাদরাকে হাকেমে মূলত “ لا يُسَلم (সালাম ফিরাতেন না)” শব্দটিই ছিল। অর্থাৎ হাকেম এ শব্দেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর “ لا يقْعُد (বসতেন না)” শব্দটি সঠিক নয়। হাকেম এ শব্দে বর্ণনা করেননি। কারণ:
১
আমার দেখা ‘মুসতাদরাকের’ পাঁচটি মুদ্রিত কপিতেই হাদীসটি “ لا يُسَلم (সালাম ফিরাতেন না)” শব্দে এসেছে : যা বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রকাশকদের কাছে এ কিতাবের যে কটি পা-ুলিপি ছিল তাতে হাদীসটি এ শব্দেই এসেছে।
২
কিতাবটি মুদ্রিত হয়ে আসার বহু আগে, যখন হস্তলিখিত কপি প্রচলিত ছিল তখনও বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন দেশের অনেক মুহাদ্দিস ‘মুসতাদরাক’ থেকে হাদীসটি এ শব্দে উল্লেখ করেছেন। এতে বুঝা যায় তাদের কাছে থাকা মুসতারাকের কপিগুলোতেও হাদীসটি এ শব্দেই ছিল। যেমন:
১ হাফেজ জামালুদ্দীন যাইলাঈ (মৃত.৭৬১) নছবুর রায়া গ্রন্থে
২ হাফেজ শামসুদ্দীন ইবনে আব্দিল হাদী (মৃ.৭৪৪) তানক্বীহুত তাহক্বীক গ্রন্থে (২/৪২১)
৩ হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (মৃ.৮৫২) ‘আদদিরায়া’ গ্রন্থে (১/১৯১ হা.২৪২)
৪ হাফেজ বদরুদ্দীন আইনী রহ. (মৃ.৮৫৫) উমদাতুলকারী, শরহু আবিদাউদ ও আল বিনায়া গ্রন্থে
৫ ইবনুল হুমাম (মৃ.৮৬১) ফতহুল কাদীর গ্রন্থে,
৬ হাফেজ ক্বাসেম ইবনে কুতলুবুগা (মৃ.৮৭৯) ‘আততা‘রীফ ওয়াল ইখবার ফি তাখরীজুল ইখতিয়ার’ (১/৩৭৯ হা.২১৭) গ্রন্থে
৭ মোল্লা আলী ক্বারী রহ. (মৃ.১০১৪) শরহু মুসনাদি আবিহানীফা গ্রন্থে
৮ মুরতাজা যাবীদী (মৃ.১২০৫) উকূদুল জাওয়াহিরিল মুনীফা গ্রন্থে।
৯ এমনকি গাইরে মুকাল্লিদ আলেম শাওকানী রহ. নিজেও ‘নাইলুল আওতারে’ (৩/৪২) হযরত আয়শা (রা.) এর হাদীসটিতে মুসনাদের আহমদের পাশাপাশি মুসতাদরাকের বরাতও উল্লেখ করেছেন। মুসনাদে আহমদের বর্ণনার শব্দ হল: (لا يفصل بينهن) ‘তিনি রাকাতসমূহকে (সালামের মাধ্যমে) বিভক্ত করতেন না’। এটি উল্লেখের পর শাওকানী বলেন: (أما حديث عائشة فأخرجه أيضا البيهقي والحاكم بلفظ أحمد) : “আয়শার হাদীসটি বাইহাকী ও হাকেম (মুসনাদে) আহমদের (অনুরূপ) শব্দেই উল্লেখ করেছেন”। আর আহমদের অনুরূপ শব্দ হল: “সালাম ফিরাতেন না” : অর্থাৎ সালামের মাধ্যমে বিভক্ত করতেন না।
উপরোল্লিখিত পৃথিবী বিখ্যাত হাফেজে হাদীসগণ বিভিন্ন যুগে মুসতাদরাকের বিভিন্ন হস্তলিখিত কপি থেকে হাদীসটি এ শব্দেই উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ এ নয় অঞ্চলের নয় জন হাফেজে হাদীস ও মুহাদ্দিসের কাছে মুস্তাদরাকের যে কপিগুলো ছিল, তাতে এ শব্দটিই ছিল। বলাবাহুল্য তখন মুদ্রণের যুগ ছিল না যে, একজন ভুল ছেপে দিলে সবার কাছেই ভুলটা চলে যাবে। বরং সবগুলোই ছিল হস্তলিখিত কপি। আর এতগুলো কপিতে এক সাথে ভুল শব্দ থাকবে এটা হওয়ার কথা নয়।
অবশ্য ইবনে হাজার আসকালানীর ফাতহুল বারী মুদ্রিত কপিতে, হাদীসটি “বসতেন না” শব্দে এসেছে। হতে পারে তিনি অন্য কোন কপিতে এ শব্দেই পেয়েছেন। আবার এও হতে পারে যে, এটি ফাতহুল বারী কিতাবের মুদ্রণের ভুল। কিন্তু ইবনে রজব ফাতহুল বারীতে, ইবনুল মুলাক্কিন আল বাদরুল মুনীরে এবং ইবনু আব্দিল হাদী তানকীহুত তাহকীকে (لا يقعد) শব্দে উল্লেখ করেছেন। তাই এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, হয়ত মুসতাদরাকের কোন পান্ডুলিপিতেই لا يقْعُد শব্দ রয়েছে। কিন্তু যেমনটি আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. বলেছেন:
“আমার প্রবল ধারণা (لا يسلم) শব্দটি মুসতাদরাকে হাকেমের পা-ুলিপিতেও থাকবে। কেননা যাইলাঈ কারো উদ্ধৃতি উল্লেখ করার ক্ষেত্রে এতটা (মুতাসাব্বিত) নিশ্চিত ও নির্ভুলভাবে উল্লেখ করে থাকেন যে, হাফেজ (ইবনে হাজার আসকালানী)ও অতটা করেন না। তাঁর একটি রীতি হল, তিনি যখন কারো বক্তব্য কোন মাধ্যমে পেয়ে থাকেন তখন মাধ্যম উল্লেখ করে দেন। নতুনা নিজ চোখে দেখেই সেখান থেকে হুবহু বক্তব্যটিই উল্লেখ করেন। আর এখানে (لا يسلم) বলেছেন। সুতরাং (لا يسلم) শব্দটি মুসতাদরাকের পা-ুলিপিতে অবশ্যই থাকবে।” (টীকা-১) [আরফুশ শাযী- তিরমিযীর সাথে যুক্ত পৃ. ১০৪-১০৫]
৩
বিশেষত হাকেম এ হাদীসটি উল্লেখের পূর্বে একই সনদে আরেকটি হাদীস এনেছেন (নং ১১৩৯), যার শব্দ হল: (لا يسلم في ركعتي الوتر) সালাম ফিরাতেন না”। অতঃপর বলেন: “এ হাদীসের আরো শাওয়াহেদ তথা সমর্থক হাদীস আছে”। এবং সমর্থক হিসেবেই আলোচ্য হাদীসটি (হা.১১৪০) এনেছেন। তাই দ্বিতীয় হাদীসটি প্রথম হাদীসের সমর্থক হওয়ার জন্য প্রথম হাদীসের মত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।
৪
মুসতাদরাকের এ বর্ণনার সাথেই উল্লেখ আছে, “এটিই উমর রা. এর বিতর। তাঁর কাছ থেকেই মদীনাবাসী এ পদ্ধতির বিতর শিখেছে”।
# বলাবাহুল্য ইমাম মালেক রহ. মদীনাবাসীর বিতরকে অনুসরণ করতেন, কিন্তু কোন মদীনাবাসী থেকে তিনি দুই রাকাতে বৈঠক ছাড়া তিন রাকাত বিতরের কোন বিবরণ উল্লেখ করেনও নি এবং তিনি নিজেও এভাবে বিতর পড়ার কথা বলেননি।
আবার হাফেজ ইবনুল মুলাক্কিন (মৃ.৮০৪) রহ. হাকেমের এ বিবরণ উল্লেখ করেছেন, “তাঁর কাছ থেকেই (মদীনাবাসী: এর স্থলে) ‘কুফাবাসী’ এ পদ্ধতির বিতর শিখেছে”। (আল-বাদরুল মুনীর ৪/৩০৮ দারুল হিজরাহ)। যদি ‘মদীনাবাসী’র পরিবর্তে ‘কুফাবাসী’ শব্দটি সহীহ হয় তাহলে, এ থেকে বুঝা যায় মুসতাদরাক সঙ্কলক হাকেম আবু আব্দুল্লাহ এ হাদীস থেকে দুই তাশাহহুদ ও এক সালামের বিতরই বুঝেছেন। বিশেষত হাকেমের সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, ইমাম বাইহাকী রহ.। তিনিও হাদীসটির শিরোনাম দিয়েছেন: ‘দুই তাশাহ্হুদ ও এক সালামে তিন রাকাত বিতর’।
(দুই) হাদীসের সবগুলো সূত্র সামনে রাখলে: দুই রাকাতে ‘বসতেন না’ কথার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না:
হযরত আয়শা রা. এর সূত্রে হাকেম ও বাইহাকী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এর সনদ: শাইবান ইবনে ফাররুখ আবান ইবনে ইয়াযিদ থেকে এবং আবান ইবনে ইয়াযিদ কাতাদা থেকে। অতঃপর সনদটি এরূপ: যুরারাহ-সা‘দ ইবনে হিশাম-হযরত আয়শা রা.।
কাতাদাসূত্রে হযরত আয়শা রা. এর বর্ণনাটি হাদীসের বহু কিতাবে বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে (কাশফুস সিতর পৃ.৮৯-৯০)। যেমন:
১ (يوتر بثلاث لا يسلم /لا يقعد إلا في آخرهن – رواه الحاكم والبيهقي)
২ (كان لا يسلم في ركعتي الوتر- رواه النسائي)
৩ (أوتر بثلاث لا يفصل فيهن – رواه أحمد في المسند)
৪ (الوتر بتسع أو بسبع – رواه مسلم (৭৪৬) وغيره)
নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসীনে কেরাম মনে করেন: সবগুলো মূলত একই হাদীসের বিভিন্ন শব্দ। বর্ণনাকারী বিভিন্ন সময়ে হাদীসের মূল বক্তব্য ঠিক রেখে বিভিন্ন শব্দে ব্যক্ত করেছেন। কখনো সংক্ষেপে আবার কখনো বিস্তারিত। সুতরাং এ হাদীস থেকে বিতর নামাযের পদ্ধতি বের করতে হলে, সবগুলো বর্ণনাকে সামনে রেখেই তবে করতে হবে। যে সকল মুহাদ্দিস শব্দের সামান্য ভিন্নতা সত্ত্বেও সবগুলোকে একই হাদীস বলে গণ্য করেছেন তাদের মধ্যে কয়েকজন:
১
এ হাদীসের বর্ণনাকারী হাকেম স্বয়ং: তার মুসতাদরাকে উপরোক্ত দ্বিতীয় নম্বরে উল্লিখিত শব্দের সমর্থক হিসেবে প্রথম নম্বরে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। (মুসতাদরাক হা.১১৪০, ১১৪১)
২
এ হাদীসে অপর বর্ণনাকারী বাইহাকী রহ. স্বষ্ট ভাষায় বলেছেন, সা‘দ ইবনে হিশাম সূত্রে হযরত আয়শা রা. থেকে বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত বিতর বিষয়ক হাদীস মূলত একটি হাদীসেরই বিভিন্ন চিত্র। (وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَهَّابِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ اخْتِصَارًا مِنَ الْحَدِيثِ) [আসসুনানুল কুবরা ৩/৩১] অবশ্য বাইহাকী রহ. এর মত হল, সাদ ইবনে হিশামের আলোচ্য বর্ণনায় রাকাত সংখ্যা ছিল নয়। এ কথা মারওয়াযী ও তার অনুসরণে আলবানীও বলতে চেয়েছেন। কিন্তু এ মতের পক্ষে যথাযথ কোন দলিল পাওয়া যায় না।
৩
ইমাম নববী বাইহাকীর মন্তব্যটি সমর্থনপূর্বক উল্লেখ করেন। (আল-মাজমূ:৪/১৮)
৪
হাফেজ ইবনুল মুলাক্কিন (মৃ.৮০৪)। (আল-বদরুল মুনীল ৪/৩০৮)
৫
হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.। (ইতহাফুল মাহারা বিল ফাওয়াইদিল মুবতাকারাহ ১৬/১০৮৬ হা. ২১৬৭১ )
৬
ইবনে তাইমিয়া আল-জাদ্দ ও শাওকানী রহ.। (নাইলুল আওতার ৩/৩৫)
৭
আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. (কাশফুস সিতর পৃ.৮৯-৯০)
৮
খোদ গাইরে মুকাল্লিদ আলেম আব্দুর রহমান মুবারকপুরীও স্পষ্ট ভাষায় দুটি হাদীসকে এক গণ্য করে বলেন: (قلت لا مخالفة بين قوله لا يسلم في الركعتين الأوليين من الوتر وقوله لا يقعد إلا في آخرهن) : দুই হাদীসের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। [তুহফাতুল আহওয়াযী ২/৪৫৩]
এ ছাড়াও আরো অনেকেই এ কথা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন। বিশেষত প্রথমোক্ত দুটি শব্দ হযরত কাতাদা সূত্রে একই সনদে বর্ণিত হয়েছে।
সুতরাং সবগুলো বর্ণনাকে সামনে রাখলে স্পষ্ট যে, আলোচ্য হাদীসের শব্দ অন্যগুলোর মতই : “لا يقْعُد (বসতেন না)” না হয়ে “ لا يُسَلم (সালাম ফিরাতেন না)” হওয়াটাই যক্তিযুক্ত।
আর যদি এ হাদীসে বর্ণিত শব্দগুলির মধ্যে কোনটি প্রাধান্য পাবে সেদিকে দৃষ্টিপাত করা হয় তাহলে প্রথমোক্ত মুসতাদরাকে হাকেম ও বাইহাকীর (لا يقعد / لا يسلم) শব্দ সম্বলিত বর্ণনাটিই অধিকতর দূর্বল প্রমাণিত হয়। এর তুলনায় দ্বিতীয় নাম্বারে উল্লিখিত (لا يسلم في ركعتي الوتر) : শব্দটিই প্রাধান্য পায়, যার সুস্পষ্ট অর্থ হল, বিতরের দ্বিতীয় রাকাতে বৈঠক করতেন হয়, কিন্তু সালাম ফিরাতেন না। কারণ, প্রথমোক্ত শব্দটি কাতাদা থেকে বর্ণনা করেছেন শাইবান ইবনে ফাররুখ আবান সূত্রে। আর দ্বিতীয়টি বর্ণনা করেছেন, আব্দুল ওয়াহহাব ইবনে আতা সাঈদ ইবনে আবী আরুবা সূত্রে। তন্মধ্যে শাইবান সত্যবাদী হওয়া সত্ত্বেও বর্ণনায় ভুল করতেন, ( صدوق يهم- تقريب التهذيب)। তাই কারো বর্ণনার সাথে বিরোধ লাগলে তার বর্ণনা যাচাই করা জরুরী। বিপরীতে আব্দুল ওয়াহহাব ইবনে আতা সম্পর্কে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন: (كان عبد الوهاب بن عطاء من أعلم الناس بحديث سَعِيد بن أَبي عَرُوبَة) : আব্দুল ওয়াহহাব সাঈদের হাদীস সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানেন (তাহযীবুল কামাল)। তাই সাঈদের বর্ণনায় তার ভুল হবার কথা নয়। আর ইমাম আবু হাতিম, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন ও আবু দাউদ তায়ালিসী প্রমুখ বলেন: “(كان سعيد أحفظ أصحاب قتادة/ أعلم الناس بحديث قتادة) : অর্থাৎ কাতাদার হাদীস সম্পর্কে কাতাদার শিষ্যদের মধ্যে সাঈদ সবচেয়ে বেশি জানেন।” (সিয়ারু আলামিন নুবালা) সুতরাং স্বভাবতই তার বর্ণনা শাইবানের বর্ণণার উপর অগ্রগণ্য হবে। [আরো দেখুন: নছবুর রায়াহ টীকা, তাহক্বীক শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামাহ ২/১১৮]
(তিন) “ لا يقْعُد” অর্থ ‘সালাম ফেরানোর জন্য বসতেন না’
যদি ধরে নেয়া যায় এ হাদীসে “ لا يقْعُد (বসতেন না)” শব্দটিই সঠিক। তাহলে প্রশ্ন হয়: শব্দের অর্থের মধ্যে কি ‘তাশাহুদের জন্য’ বসতেন না এটি সুস্পষ্ট; নাকি ‘সালাম ফিরানোর জন্য’ বসতেন না এ অর্থেরও যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে? এ পশ্নের উত্তর খুঁজে দেখা যায়, দুটো অর্থের সম্ভাবনা আছে বটে কিন্তু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে ‘সালাম ফিরানোর জন্য বসতেন না’ অর্থটিই এখানে যথোপযুক্ত মনে হয়। কারণ একই হাদীসের অন্য বর্ণনায়: ” لا يفصل فيهن” :“নামায বিভক্ত করতেন না”। (মুসনাদে আহমদ হা. ২৫২২৩ ) আরেক বর্ণনায় : (لا يسلم في ركعتي الوتر) “বিতরের দুই রাকাতে সালাম ফেরাতেন না” বলা হয়েছে। (সুনানে নাসায়ী হা.২৫২২৩)
যারা সা‘দ ইবনে হিশাম সূত্রে হযরত আয়শা থেকে বর্ণিত এ হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনাগুলোকে এক হাদীস গণ্য করেন তারা সকলেই হাদীসের এ ব্যাখ্যাই করে থাকবেন। এবং (لايسلم) বা (لا يقْعُد) যে শব্দই হোক তারা এ হাদীস থেকে এক সালাম ও দুই বৈঠকের তিন রাকাত বিতরই বুঝেছেন।
উদাহারণস্বরূপ বলা যায়, ইমাম ইবনুল জাওযী (মৃ.৫৯৭), ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দিল হাদী (মৃ.৭৪৪) ও ইমাম যাহাবী (মৃ.৭৪৮) প্রত্যেকেই কাতাদাসূত্রে হাদীসটি উল্লেখকরে বলেছেন: এ হাদীস থেকে এক সালামে তিন রাকাত বিতর পড়া প্রমাণিত হয়। তবে দুই রাকাতে বৈঠক অবশ্যই করতে হবে। তাঁদের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাঁরা দুই রাকাতে বৈঠক না করার সম্ভাবনাটকেও প্রত্যাখ্যান করেছেন দৃঢ়তার সাথে। তাদের তিনজনেরই ভাষ্য প্রায় কাছাকাছি এবং তিনজনের কেউই ফিকহে হানাফীর অনুসরণ করতেন না। তন্মধ্যে ইমাম যাহাবী রহ. ভাষ্য হল: (قلْنَا : يجوزُ هذا أن يوتر بسلامٍ واحدٍ لكنْ يتشهد بينهم كالمغرب) : ‘আমরা বলি, এ পদ্ধতিতে এক সালামেও (তিন রাকাত) বিতর পড়া সম্ভাবনা আছে। তবে মাগরিবের নামাযের মত মাঝে তাশাহহুদ পড়বে।’
[দেখুন:তানকীহু কিতাবিত তাহকীক, ইমাম যাহাবী ১/২১৬, আত্তাহকীক ফি মাসায়িলিল খিলাফ ১/৪৫৬ তানকীহুত তাহক্বীক, ইবনু আব্দিল হাদী ২/৪২১]বরং তারও পূর্বে ইমাম ইবনে হাযম জাহেরী (মৃ.৪৫৬) বিতর নামাযের বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনায় বলেন: (والثاني عشر: أن يصلي ثلاث ركعات، يجلس في الثانية، ثم يقوم دون تسليم ويأتي بالثالثة، ثم يجلس ويتشهد ويسلم، كصلاة المغرب وهو اخْتِيَارُ أبي حَنِيفَةَ.) : ‘দ্বাদশ পদ্ধতি: তিন রাকাত নামায পড়বে। তাতে দুই রাকাত শেষে বসে সালাম না ফিরিয়েই আবার দাড়িয়ে যাবে এবং তৃতীয় রাকাত পড়বে। অতঃপর মাগরিবের নামাযের মতই বসে তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে। আর এ মতটাই গ্রহণ করেছেন আবু হানীফা”। অতঃপর তিনি দলিল হিসেবে সা‘দ ইবনে হিশামের এ বর্ণনাটিই উল্লেখ করেছেন, (لا يسلم في ركعتي الوتر)। (আল-মুহাল্লা বিল আসার ৩/৪৭)
আলোচ্য হাদীসের এ অর্থটা খুব স্বাভাবিক। এ কারণেই গায়রে মুকাল্লিদ আলেম শাওকানী (রহ.) ও শামসুল হক আজীমাবাদী রহ. উভয়েই সাদ ইবনে হিশাম সূত্রে হযরত আয়শার এ হাদীসের একটি বর্ণনায়: “لا يقْعُد (বসতেন না)” শব্দের ঠিক একই ব্যাখ্যা করেছেন। শাওকানী রহ. নবীজী থেকে বর্ণিত হাদীস: (صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن ) ‘সাত রাকাত পূর্ণ করার আগে বসতেন না’ এর ব্যাখ্যায় বলেন:(الرواية الأولى تدل على إثبات القعود في السادسة والرواية الثانية تدل على نفيه ويمكن الجمع بحمل النفي للقعود في الرواية الثانية على القعود الذي يكون فيه التسليم) : “প্রথম বর্ণনা থেকে বুঝা যায় ষষ্ট রাকাতে ‘বসতেন’। আর দ্বিতীয় বর্ণনা থেকে বুঝা যায় ‘বসতেন না’। এ দুয়ের মাঝে এভাবে সামঞ্জস্য হবে যে, তিনি ‘বসতেন না’ দ্বারা বোঝানো হয়েছে : ‘সালাম ফেরানোর জন্য বসতেন না’।” [নাইলুল আওতার ৩/৪৭ ছালাতুল বিতরি ওয়াল কিরাআতি ওয়াল কুনূত অধ্যায়, আওনুল মা‘বুদ শারহু সুনানি আবি দাউদ ৪/২২১]
(চার) ইমাম বাইহাকী রহ. নিজেই এ হাদীস থেকে ‘এক সালাম ও দুই তাশাহুহুদে তিন রাকাত বিতর’ বুঝেছেন।
আলোচ্য বর্ণনাটি এ শব্দে বর্ণিত হয়েছে মৌলিকভাবে কেবল হাকেমের মুসতাদরাক কিতাবে। ইমাম বাইহাকী হাদীসটি হাকেমের সূত্রেই ‘আস-সুনানুল কুবরা’ ও ‘মা‘রিফাতুস সুনান’ গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণনা করেছেন। আর বর্ণনাকারী ইমাম বাইহাকী নিজেই এ হাদীস থেকে ‘এক সালাম ও দুই তাশাহহুদে তিন রাকাত বিতর’ বুঝেছেন। তিনি ‘আসসুনানুল কুবরায়’ (৩/৩১) যে অধ্যায়ে হাদীসটি উল্লেখ করে এর শিরোনাম দিয়েছেন: (باب من أوتر بثلاث موصولات بتشهدين وتسليم ) :“অধ্যায় ঃ যারা দুই তাশাহহুদ ও এক সালামে একত্রে মিলিয়ে তিন রাকাত বিতর পড়েন”। আর ‘মা‘রিফাতুসসুনান’ গ্রন্থে (৪/৭১) আরো স্পষ্ট বলেছেন: (الوتر بثلاث ركعات موصولات بتشهدين ويسلم من الثالثة) :“বিতর নামায দুই তাশাহ্হুদে একত্রে তিন রাকাত, এবং তৃতীয় রাকাত পূর্ণ করে সালাম ফেরাবে”। এখানে বাইহাকী রহ. হাদীসটি থেকে কি বুঝে আসে তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তদ্রƒপ হাকেম নিজেও এ হাদীস পূর্ববর্তী হাদীসের সমর্থক বলে দিয়েছেন। যাতে ‘বসতেন না’ কথাটি নেই।
গ্রন্থকার – ১৭
গ্রন্থকার বলেন, “বিশেষ সতর্কতা: মুস্তাদরাকে হাকেমে বর্ণিত لا يقْعُد (বসতেন না) শব্দকে পরিবর্তন করে পরবর্তী ছাপাতে لا يُسَلم (সালাম ফিরাতেন না) করা হয়েছে। কারণ পূর্ববর্তী সকল মুহাদ্দিছ لا يقْعُد দ্বারাই উল্লেখ করেছেন। টীকায় বরাত দিয়েছেন: “হাকেম হা/১১৪০ ফৎহুল বারী হা/৯৯৮ আল-আরফুশ শাযী ২/১৪” (পৃ.৩৩১)
পর্যালোচনা
এক
গ্রন্থকারের দাবি মুসতাদরাকের মুদ্রিত কপিতে হাদীসের শব্দ পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কে পরিবর্তন করেছে তিনি তা বলেননি। আর যদি কোন প্রমাণ না থাকে তাহলে অনুমান ভিত্তিক এমন অপবাদ কারো উপর দেয়া ঠিক নয়। পূর্বে বলা হয়েছে কিতাবটি ছাপার বহুকাল আগেই হাদীসটি এ শব্দে বিভিন্ন জনের কিতাবে ছিল। মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেব যে বলেছেন, পরবর্তী ছাপায় পরিবর্তন করা হয়েছে; তিনি কি দেখাতে পারবেন যে পূর্ববর্তী কোন ছাপায় তা لا يقْعُد শব্দে ছিল?
দুই.
তিনি পরিবর্তনের দলিল হিসেবে যা উল্লেখ করেছেন তা একদিকে যেমন ভিত্তিহীন অপরদিকে হাস্যকরও বটে। কেননা
ক.
তিনি বলেন: “কারণ পূর্ববর্তী সকল মুহাদ্দিছ لا يقْعُد দ্বারাই উল্লেখ করেছেন”। কিন্তু এ দাবি যে সঠিক নয় পূর্বের আলোচনায় তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। কেননা কিতাব মুদ্রণের যুগ শুরু হওয়ার বহু যুগ আগেই অনেক সংখ্যক মুহাদ্দিস বর্ণনাটি: (لا يسلم) শব্দে উল্লেখ করেছেন। যদিও কোন কোন মুহাদ্দিস বর্ণনাটি দ্বিতীয় শব্দেও উল্লেখ করেছেন তবুও অনেকগুলো পার্শ্বকারণ সামনে রাখলে (لا يسلم) শব্দটিকেই প্রাধান্য দিতে হয়। সুতরাং মুদ্রণের বহু আগে থেকেই এ শব্দ ছিল।
খ
আর “পূর্ববর্তী সকল মুহাদ্দিস” কথাটি একেবারেই ভিত্তিহীন। যা পূর্বে দেখানো হয়েছে।
তিন.
গ্রন্থকার টীকায় বরাত দিয়েছেন, “হাকেম হা/১১৪০ ফৎহুল বারী হা/৯৯৮ আল-আরফুশ শাযী ২/১৪” এখানে হাকেমের বরাত দেয়াটা হাস্যকর। কারণ, মতপার্থক্যই হল হাকেমের শব্দ নিয়ে। হাকেমের কিতাব থেকে মুহাদ্দিসগণ দুই শব্দেই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তাই এক্ষেত্রে হাকেমের বরাত দেয়াটা সত্যিই হাস্যকর। আবার হাকেমের মুদ্রিত কপিতেতো রয়েছে: (لا يسلم) শব্দ। তিনি যে হাদীস নাম্বার দিয়েছেন (হা.১১৪০) মুসতাদরাকের কোন কপিতেতো এখানে (لا يقْعُد) শব্দে হাদীসটি নেই। আর ফাতহুল বারীতে ইবনে হাজার এ শব্দে আনলেও তাঁর আদদিরায় কিতাবে তিনি (لا يسلم) শব্দে এনেছেন।
গ্রন্থকার – ১৮
অতঃপর গ্রন্থকার বলেন: “আরো দুঃখজনক হল, আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) নিজে স্বীকার করেছেন যে, আমি মুস্তাদরাক হাকেমের তিনটি কপি দেখেছি কিন্তু কোথাও لا يُسَلم (সালাম ফিরাতেন না) পাইনি। তবে হেদায়ার হাদীছের বিশ্লেষক আল্লামা যায়লাঈ উক্ত শব্দ উল্লেখ করেছেন। আর যায়লাঈর কথাই সঠিক। সুধি পাঠক! ইমাম হাকেম (৩২১-৪০৫) নিজে হাদীছটি সংকলন করেছেন আর তিনিই সঠিকটা জানেন না! বহুদিন পরে এসে যায়লাঈ (মৃত.৭৬২) সঠিকটা জানলেন? অথচ ইমাম বায়হাক্বী (৩৮৪-৪৫৮হিঃ) ও একই সনদে উক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন। সেখানে একই শব্দ আছে। অর্থাৎ لا يقْعُد (বসতেন না) আছে। একেই বলে মাযহাবী গোঁড়ামী। অন্ধ তাকলীদকে প্রাধান্য দেয়ার জন্যই হাদীছের শব্দ পরিবর্তন করা হয়েছে।”(পৃ.৩৩২)
গ্রন্থকারের বক্তব্যের খোলাসা কথা হল: ১.হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হাকেম মুসতাদরাক গ্রন্থে (لا يقْعُد) ‘বসতেন না’ শব্দে। আর যাইলাঈ কয়েকশত বছর পর এসে বলছেন হাদীসের শব্দ হল: (لا يسلم) ‘সালাম ফিরাতেন না’। ২.কাশ্মীরী রহ. মাযহাবের গোঁড়ামির কারণে বলছেন: যাইলাঈর কথাই সঠিক।
পর্যালোচনা
(ক) বক্তব্য বিকৃত করে অপবাদ আরোপ
গ্রন্থকার এখানে রীতিমত আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. এর বক্তব্যকে কেটে ছেটে বিকৃত করে তার উপরে দোষ চাপিয়ে দিলেন। দেখুন তিনি বলেন, “আর যায়লাঈর কথাই সঠিক”! অতঃপর বিস্ময়করভাবে যাইলাঈকে হাকেম ও বাইহাকীর মোকাবেলায় দাড় করালেন?!
বস্তুত গ্রন্থকারের দুটি কথাই সম্পূর্ণ অবাস্তব। দেখুন কাশ্মীরী রহ. বক্তব্য হল, “আমার প্রবল ধারণা (لا يسلم) শব্দটি মুসতাদরাকে হাকেমের পা-ুলিপিতেও থাকবে। কেননা যাইলাঈ কারো উদ্ধৃতি উল্লেখ করার সময় এতটা (মুতাসাব্বিত) নিশ্চিত ও নির্ভুলভাবে উল্লেখ করেন, হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানীও অতটা করেন না। তাঁর একটি আদত হল, তিনি যখন কারো বক্তব্য কোন মাধ্যমে পেয়ে থাকেন তখন তার বরাত উল্লেখ করে দেন। নতুবা নিজ চোখে দেখেই সেখান থেকে হুবহু বক্তব্যটিই উল্লেখ করেন। আর এখানে শব্দ পরিবর্তন করে (অর্থাৎ (لا يقْعُد) না বলে (لا يسلم) বলেছেন। (এবং এর কোন বরাতও উল্লেখ করেননি। তাই বুঝা যায় তিনি মসতাদরাকে (لا يسلم) শব্দটি নিজ চোখে দেখেই তবে উল্লেখ করেছেন।) সুতরাং (لا يسلم) শব্দটি মুসতাদরাকের পা-ুলিপিতে অবশ্যই থাকবে।
অর্থাৎ যাইলাঈ রহ. হাকেম রহ এর মুসতাদরাক গ্রন্থ থেকে হাদীসটি لا يقْعُد শব্দে নয় বরং لا يسلم শব্দেই উল্লেখ করেছেন। কাশ্মীরির কথা হল, মুসতাদরাকের কোন পা-ুলিপিতে যদি হাদীসটিلا يسلم শব্দে আমি না পাই, তবুও প্রবল ধারণা হয় যে, এটি মুসতাদরাকের কোন না কোন কপিতে থাকবেই। কারণ, যাইলাঈ নিজের চোখে না দেখে কোন বরাত দেন না। সুতরাং হাকেম মুসতাদরাক গ্রন্থে হাদীসটি কোন শব্দে বর্ণনা করেছেন, তাতো আর আমরা হাকেমকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারব না। বরং মুসতারাকের কপিতে যা পাই তাই বিশ্বাস করতে হবে। তাছাড়া যাইলাঈ ছাড়াও আরো অনেকেই মসতাদরাকের বরাতে হাদীসটি لا يسلم শব্দে উল্লেখ করেছেন। এতেও কাশ্মীরীর রহ. এর বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়।
সাধারণ পাঠকও এখান থেকে একথা বুঝবে না যে, হাকেম বলতেছেন, হাদীসের শব্দ হল: (لا يقْعُد) ‘বসতেন না’, আর যাইলাঈ এটা অস্বীকার করে বলছেন হাদীসের শব্দ : (لا يسلم) ‘সালাম ফিরাতেন না’।
বরং এখানে মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেব মুসতাদরাকের কপিতে হাদীসটি (لا يقْعُد) ‘বসতেন না’ শব্দে পেয়েছেন বলে দাবি করেছেন। যদিও কোন কপিতে পেয়েছেন তার কোন উল্লেখ তিনি করেননি। বিপরীতে যাইলাঈ মুসতাদরাকের বরাতে হাদীসটি (لا يسلم) ‘সালাম ফিরাতেন না’ শব্দে উল্লেখ করেছেন। আমরাও বহু সংখ্যক মুদ্রিত কপিতে হাদীসটি এ শব্দেই পেয়েছি। তাই একথা বলা যায়, মুসতাদরাকে হাদীসটি কোন শব্দে রয়েছে এ বিষয়ে জনাব মুযাফ্ফর সাহেব এর কথা বিশ্বাস করব, নাকি ইমাম যাইলাঈর কথা?! সাথে একথাও মনে রাখতে হবে যে মুযাফফর সাহেব কোন মুদ্রিত ও অমুদ্রিত প-ুলিপিতেই (لا يقْعُد) ‘বসতেন না’ শব্দটি দেখেছেন বলে প্রমাণ হয়নি। তবুওকি যাইলাঈর কথাকে সঠিক বললে দোষ হবে?
বরং মুযাফফর সাহেব কোন কপিতে সরাসরি না দেখে ‘সালাম ফিরাতেন না’ শব্দটি পরিবর্তন করে ‘বসতেন না’ উল্লেখ করে মহা অন্যায় করেছেন।
বিষয়টি বুঝে থাকলে এবার গ্রন্থকারের পরবর্তী কথাগুলো পড়ে হাসিও আসবে, আবার কান্নারও জোগাড় হবে যে, এমন লোক এভাবে ইমামদের ও উলামাদের উপরে অপবাদ দিয়ে যাচ্ছেন কত দুঃসাহসিকাতার সাথে! দেখুন তিনি বলেন: “সুধি পাঠক! ইমাম হাকেম (৩২১-৪০৫) নিজে হাদীছটি সংকলন করেছেন আর তিনিই সঠিকটা জানেন না! বহুদিন পরে এসে যায়লাঈ (মৃত.৭৬২) সঠিকটা জানলেন? অথচ ইমাম বায়হাক্বী (৩৮৪-৪৫৮হিঃ)ও একই সনদে উক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন। সেখানে একই শব্দ আছে। অর্থাৎ لا يقْعُد (বসতেন না) আছে।” আফসোস, গ্রন্থকার যে বোঝেন না একথাটা যদি তিনি বুঝতেন!
অথচ এমন পরিপক্ক! বুঝ নিয়েই গ্রন্থকার মুখস্ত করা গালি ছুড়ে মারলেন আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. এর মত একজন প্রাজ্ঞ হাদীস বিশারদকে বিনা অপরাধে অপরাধী ও প্রতিপক্ষ বানিয়ে, “একই বলে মাযহাবী গোঁড়ামী। অন্ধ তাকলীদকে প্রাধান্য দেয়ার জন্যই হাদীছের শব্দ পরিবর্তন করা হয়েছে।” ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন!
মোটকথা এ পদ্ধতির বিতরের সপক্ষে কোন সহীহ ও স্পষ্ট হাদীস নেই। তাই ইবনে হাযম জাহেরী রহ. বিতর বিষয়ক যত বর্ণনা পাওয়া যায় সবগুলোকেই বিতর নামাযের একেকটি তরীকা বলে মোট ১৩ পদ্ধতিতে বিতর পড়ার বৈধতা দিয়েছেন। আশ্চর্য, সেখানেও এ পদ্ধতির বিতরের কোন উল্লেখ নেই। আর তিনি ছাড়া যারাই বিতরের এমন একটি পদ্ধতির সম্ভাবনা ও বৈধতার কথা উল্লেখ করেছেন, তাদের কেউ এ ভূল বর্ণনা দিয়ে দলিল পেশ করেননি।
আরেকটি ভুল
গ্রন্থকার যাইলাঈকে বলেছেন: ‘হেদায়ার হাদীছের বিশ্লষক’। এটিও গ্রন্থকারের একটি ভুল। কারণ বিশ্লেষক বলা হয় ব্যাখ্যাকারকে। আসলে যাইলাঈ হেদায়ার হাদীসের ‘তাখরীজ’ করেছেন। ‘তাখরীজ’ মানে হাদীসের উৎস ও সূত্র উদ্ধার করা। পাশাপাশি কেউ কেউ হাদীসের মান নির্ণয়ের কাজও করে দেন। যে এ কাজ করে পরিভাষায় তাকে ‘মুর্খারিজ’ বলে। বাংলায় সূত্র উদ্ধারক বলা যেতে পারে।
(খ) একই হাদীস কি একবার সহীহ হয় আরেকবার দূর্বল
সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, গ্রন্থকার এখানে হযরত আয়শা রা. এর যে হাদীস দিয়ে বিশেষ প্রকারের বিতর প্রমাণ করতে চাচ্ছেন, যার পক্ষে এ বর্ণনাটি ছাড়া আর কোন দলিল নেই, তার বইয়ের ৩৩৩ পৃষ্ঠার টীকায় এটিকেই আবার জোর দিয়ে যঈফ ও দূর্বল সাব্যস্ত করেছেন! দেখুন: গ্রন্থকার ৩৩৩ পৃষ্ঠায় বলেন, “ তিন রকাআত বিতরের মাঝে সালাম দ্বারা পার্থক্য করা যাবে না মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ”। টীকায় লেখেন: “১২৯০. ইরওয়াউল গালীল হা.৪২১ ২/১৫০”
পর্যালোচনা
গ্রন্থকারের উল্লিখিত বরাতে (ইরওয়াউল গালীল হা.৪২১ ২/১৫০) শায়খ আলবানী রহ. বলেন, (وكأنه من أجله ضعف الإمام أحمد إسناده كما نقله المجد ابن تيمية فى المنتقى (২/২৮০ ـ بشرح الشوكانى)) : “হয়ত একারণেই ইমাম আহমদ হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন, যেমনটি ইবনে তাইমিয়া আল-জাদ্দ তার মুনতাকায় উল্লেখ করেছেন। নায়লুল আওতার ২/২৮০”। অর্থাৎ ইমাম আহমদ, ইবনে তাইমিয়া আল-জাদ্দ, শাওকানী, আলবানী প্রমুখ এ বর্ণনাটিকে যঈফ বলেছেন। কেউ তাদের এ বক্তব্য গ্রহণ নাও করতে পারেন, যদি তার কাছে দলিল থাকে। কিন্তু এক স্থানে তাদের কথা গ্রহণ করবেন, আবার একই হাদীসের বিষয়ে অন্য স্থানে গ্রহণ করবেন না, হাদীসের ক্ষেত্রে এমন দ্বিমুখী নীতি কেন? মাযহাবী গোঁড়ামী ধরতে গিয়ে এমন গোঁড়ামীর জালেই আটকা পরে গেলেন না তো আবার?
গ্রন্থকার – ১৯
এক বৈঠকে তিন রাকাতের পক্ষে গ্রন্থকারের দ্বিতীয় দলিল:
ب) عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يوتر بثلاث لا يقعد بينهن.
“(খ) ইবনু ত্বাউস তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূল (ছাঃ) তিন রাক‘আত বিতর পড়তেন। মাঝে বসতেন না। (টীকা: মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৪৬৬৯ তয় খ-, পৃ.২৭)” (পৃ.৩৩২)
পর্যালোচনা
এক. তাবেয়ীর আমলকে নবীজীর আমল বানিয়ে দিলেন
গ্রন্থকার এখানে একজন তাবেয়ীর আমলকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল বানিয়ে চরম অজ্ঞতার পরিচয় দিলেন। তিনি লিখেছেন “রসূল ছাঃ তিন রাকাত ..”। অথচ এটি হবে “তাউস তিন রাকাত …”। মূলত এ বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন উল্লেখও নেই ইঙ্গিতও নেই। বিষয়টি যে কোন হাদীসের পাঠকেরই বোধগম্য হওয়ার কথা।
দুই
আবার এখানে শব্দ এসেছে: (لا يقعد) ‘তিনি বসতেন না’; একথা বলেননি:(لا يتشهد) ‘তিনি দুই রাকাতে তাশাহহুদ পড়তেন না’। তাই এখানে (لا يقعد) এর এ অর্থ খুবই যুক্তিসঙ্গত যে তিনি ‘সালাম ফিরানোর জন্য বসতেন না’। সুতরাং এ আসারটিও দুই রাকাতে তাশাহহুদের জন্য না বসা বিষয়ে স্পষ্ট নয়।
তিন
গ্রন্থকার এর পূর্বের পৃষ্ঠায় (পৃ.৩৩১) দ্বিতীয় রাকাতে বৈঠক করার বিষয়ে ওবাইদুল্লাহ মুবারকপুরীর বক্তব্য তুলে ধরেছেন। যার অর্থ: “তিন রাকাত বিতর পড়ার সময় দ্বিতীয় রাকাতে বৈঠক করার বিষয়ে কোন মরফু-সহীহ-সরীহ তথা সহীহ ও সুস্পষ্ট নবীজীর কোন হাদীস পাইনি। (لم أجد حديثا مرفوعا صحيحا صريحا في إثبات الجلوس في الركعة الثانية عند الإيتار بالثلاث.) ”
দেখুন দুই রাকাতে বৈঠক প্রমাণ করার জন্য গ্রন্থকার দাবি করলেন: হাদীসটি হতে হবে ১. মরফু তথা নবীজীর কথা বা কাজ ২. হতে হবে সহীহ ৩. হতে হবে সরীহ তথা সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন।
আর এখানে গ্রন্থকার যে দলিল পেশ করলেন তা
১. নবীজীর কথা বা কাজতো নয়ই, সাহাবীরও নয়; বরং তাবেয়ীর কর্ম মাত্র।
২. সনদ সহীহ কি সহীহ না সে বিষয়ে গ্রন্থকার কিছুই বলেননি।
৩. আবার বর্ণনাটি সরীহ বা সুস্পষ্ট নয়। বরং এর বিপরীত অর্থের প্রবল সম্ভাবনা রাখে।
অন্যের কাছে দলিল চাওয়ার সময় যে যে বিষয়গুলোর শর্ত করলেন এর কোনওটি কি আছে এখানে তার উল্লিখিত দলিলে? যদি না থাকে তাহলে এমন দ্বিমুখী নীতি কেন? অথচ নামাযের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে সহীহ মুসলিমে শরীফের বর্ণনানুযায়ী ‘প্রতি দুই রাকাত পর তাশাহহুদ আছে’। আর এর ব্যতিক্রম কোন নামাযে পাওয়া যায় না। সুতরাং দুই রাকাতে তাশাহহুদ না পড়ার সুস্পষ্ট দলিল না পাওয়া পর্যন্ত দলিল ছাড়াই নামাযের স্বাভাবিক নিয়মেই তাশাহহুদ পড়া আবশ্যক হওয়ার কথা। তার উপর আবার শক্তিশালী দলিলও রয়েছে। তারপরও কেন দলিল ছাড়া এ নতুন নিয়মের বিতর আবিস্কার করে দলিল বিশিষ্ট সহীহ নিয়মকে ভুল আখ্যায়িত করা হচ্ছে।
চার. আমাদের আলোচনায় এসেছে যে, গ্রন্থকার একাধিক স্থানে সাহাবীর কথা বা কাজ সংক্রান্ত বর্ণনাকে মওকুফ বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। আর এখানে তিনি তার চেয়েও নিচে তথা তাবেয়ীর কথাও নয় বরং অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক আমলকে পুঁজি করে নিজের মতটাকেই একমাত্র সঠিক সাব্যস্ত করতে চাচ্ছেন।
গ্রন্থকার – ২০
গ্রন্থকারের তৃতীয় দলিল
عن قتادة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ” يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن
“(গ) ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) তিন রাক‘আত বিতর পড়তেন। শেষের রাক‘আতে ছাড়া তিনি বসতেন না।” (টীকা. মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার হা/১৪৭১ ৪/২৪০, ইরওয়াউল গালীল হা/৪১৮ এর আলোচনা)
পর্যালোচনা :
এটি মূলত কাতাদা থেকে আবান ইবনে ইয়াযিদের বর্ণিত হযরত আয়শার রা. মারফু-মুত্তাসিল হাদীসটিই, যা নিয়ে আমরা দীর্ঘ আলোচনা করে আসলাম। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হাকেম ও বাইহাকী রহ.। এটিকে ভিন্ন কোন হাদীস হিসেবে কেউই বর্ণনা করেননি। আমার জানা মতে গ্রন্থকারই এটিকে প্রথম ভিন্ন হাদীস হিসেবে রূপ দিয়েছেন। বাইহাকীর দ্ইু কিতাব থেকেই তার বক্তব্য তুলে ধরছি। যে কোন সাধারণ পাঠকই বিষয়টি সহজে বুঝতে পারবেন ইনশাল্লাহ।
বাইহাকী তাঁর ‘মারিফাতুস সুনান’ গ্রন্থে কাতাদাসূত্রে বর্ণিত হযরত আয়শার মরফু-মুত্তাসিল হাদীস সম্পর্কে আলোচনায় বলেন: (ورواه أبان بن يزيد، عن قتادة وقال فيه 🙂 :‘এ হাদীসটিই আবান বর্ণনা করেছেন কাতাদা থেকে, যাতে তিনি বলেন, …’। অর্থাৎ ইমাম বাইহাকী রহ. পূর্বের বর্ণনা থেকে এ বর্ণনাটির কেবল শব্দের পার্থক্যটাই কেবল দেখাতে চেয়েছেন। সনদে বা সূত্রে কোন পার্থক্য নেই। বরং এটিও পূর্বের সনদেই বর্ণিত। তাহলে এর সনদ হল: কাতাদা-যুরারাহ-সাদ ইবন হিশাম-আয়শা …।
অতঃপর বাইহাকী রহ. বলেন, (وهو بخلاف رواية ابن أبي عروبة ، وهشام الدستوائي ، ومعمر ، وهمام عن قتادة) :‘কাতাদা থেকে বর্ণনাকারী আবানের হাদীসের শব্দ কাতাদা থেকে অপর বর্ণনাকারী ইবনে আবী আরূবা, হিশাম, মা‘মার ও হাম্মাম সকলের বর্ণনার বিরোধী।’ অর্থাৎ সনদে কোন ভিন্নতা নেই, ভিন্নতা কেবল শব্দে। এ বিষয়টি তিনি তার ‘আস-সুনানুল কুবরায়’ আরো স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এবং সব শেষে বলেছেন: আবানের বর্ণনাটি ভুল।
গ্রন্থকার এখানে :
১
টীকায় দুটি বরাত উল্লেখ করেছেন। (এক) মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার:বাইহাকী। আর সেখানে: (ورواه أبان بن يزيد عن قتادة وقال فيه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم) :বর্ণনার এ শব্দের শুরু থেকে (ورواه أبان بن يزيد) : ‘আর এ বর্ণনাটি আবান কাতাদাসূত্রে বর্ণনা করেছেন’ কথাটি এবং মাঝখান থেকে (وقال فيه): ‘এবং তাতে তিনি (আবান) বলেছেন’ শব্দটি ইচ্ছাকৃত বাদ দিয়েছেন। দেখুন: ‘এ বর্ণনাটি’ এবং ‘তাতে’ শব্দ দুটি দ্বারা কোন বর্ণনাকে বুঝানো হয়েছে, জিজ্ঞেস করলে স্বাভাবিক উত্তর আসবে: পূর্বে উল্লিখিত বর্ণনাটি। আর পূর্বে হযরত আয়শা থেকে কাতাদাসূত্রে বর্ণিত বিতর বিষয়ক মুরফু-মুত্তাসিল বর্ণনাটি। এটি ভিন্ন কোন বর্ণনা নয় যে আবার আরেকটি নাম্বার দিয়ে তাকে উল্লেখ করতে হবে।
(দুই)
তিনি টীকায় বলেছেন বিস্তারিত ইরওয়াউল গালীলের আলোচনা দ্রষ্টব্য। আমি শায়খ আলবানীর ইরওয়াউল গালীলের পূর্ণ আলোচনায় যা পেলাম তাতে শব্দ আছে: (فأخرجه الحاكم (১/৩০৪) وعنه البيهقى (৩/২৮) من طريق شيبان بن فروخ أبى شيبة حدثنا أبان عن قتادة به بلفظ: ” كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يسلم)।
অর্থাৎ আলবানী সাহেব বলেন:‘হাদীসটি (অর্থাৎ পূর্বোক্ত হযরত আয়শার মারফু হাদীস) বর্ণনা করেছেন হাকেম এবং হাকেম থেকে বাইহাকী: শাইবান ইবনে ফাররুখসূত্রে। (শাইবান বলেন) আবান কাতাদা থেকে ‘এ সনদেই’ আমাদেরকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ‘এ শব্দে’ যে, …।’ লক্ষ করুন এখানে : (أبان عن قتادة به بلفظ:) : আবান কাতাদা থেকে ‘এ সনদেই’ ‘এ শব্দে’ বর্ণনা করেছেন …।
এখানে (به) ‘এ সনেদেই বা এ সূত্রেই’ কথার মানেই হল: পূর্ববর্তী সূত্রে। অর্থাৎ কাতাদা যুরারাহ থেকে, তিনি সাদ ইবনে হিশাম থেকে, তিনি হযরত আয়শা রা. থেকে। হাদীসের যে কোন ছাত্রই বুঝে পূর্ববর্তী কোন সূত্র উল্লেখের পর যখন অন্য আরেকটি সূত্র উল্লেখ করা হয় আর তাতে বলা হয়: (به) ‘এ সূত্রেই’, তার দ্বারা বুঝা যায় এ হাদীসটিও পূর্ববর্তী সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে।
বরং এক্ষেত্রে কখনো পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে (به) শব্দ ছেড়ে দেওয়া হয়, উদ্দেশ্য হয় যে, এটি পূর্ববর্তী সূত্রে বর্ণিত। কিন্তু হাদীসের কিতাবের রীতি ও পরিভাষা সম্পর্কে যিনি অজ্ঞ তিনি তা কি করে বুঝবেন!
মোট কথা বিষয়টি বাইহাকী ও আলবানী সাহেবের বক্তব্যে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, এটি কাতাদাসূত্রে হযরত আয়শার সেই হাদীস যা গ্রন্থকার (ক) শিরোনামে এক নাম্বারে দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছেন!
সুতরাং আমরা বলতে পারি তিনি একটি হাদীসকেই নিজ হাতে কাট ছাটের পর দুটি হাদীস বানানোর চেষ্টা করলেন!
২
হাদীসটিকে পূর্বে (ক) শিরোনামে এক নাম্বারে উল্লেখের পর আবার দ্বিতীয়বার একেই উল্লেখ করলেন সামান্য পরিবর্তন করে ভিন্ন দলিল হিসেবে দেখানোর জন্য।
৩
এভাবে তিনি একটি মুত্তাসিল বর্ণনাকে মুরসাল বানিয়ে পেশ করলেন।
গ্রন্থকার : ২১
গ্রন্থকারের চতুর্থ দলিল-
عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد ويقنت قبل الركوع فإذا فرغ قال عند فراغه سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يطيل في آخرهن.
“(ঘ) উবাই ইবনু কা‘ব হতে বর্ণিত: রাসূল (ছাঃ) তিন রাক‘আত বিতর পড়তেন। প্রথম রাক‘আতে সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ‘লা, দ্বিতীয় রাক‘আতে কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফেরূন এবং তৃতীয় রাক‘আতে কুল হুওয়াল্লাহুল আহাদ পড়তেন। এবং তিনি রুকুর পূর্বে কুনূত পড়তেন। অতঃপর যখন তিনি শেষ করতেন তখন শেষে তিনবার বলতেন সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস। শেষ বার টেনে বলতেন ”
অতঃপর বলেন: “উক্ত হাদীছও প্রমাণ করে রাসূল (ছঃ) একটানা তিন রাক‘আত পড়েছেন, মাঝে বৈঠক করননি।”
পর্যালোচনা
এ হাদীস কিভাবে প্রমাণ করে যে তিনি মাঝে বৈঠক করতেন না বিষয়টি বড়ই আশ্চর্যজনক। গ্রন্থকার হয়ত বলবেন যে, এতে তিন রাকাত নামাযের কথা এসেছে, কিন্তু মাঝে দুই রাকাত শেষে বৈঠকের কথা বলা হয়নি। এতে বুঝা যায় যে তিনি বৈঠক করেননি। কিন্তু গ্রন্থকার বলবেন কি যে, এ হাদীসে সূরা ফাতিহা, রুকু-সিজদা, শেষ বৈঠকের কথা, এমনকি সালামের কথা বলা হয়নি, তাহলে কি এ থেকে বুঝা যায় নবীজী এসবের কোনটিই করেননি?!
গ্রন্থকার – ২২
গ্রন্থকারের পঞ্চম ও শেষ দলিল
عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ ” يُوتِرُ بِثَلاثٍ لا يَجْلِسُ فِيهِنَّ، وَلا يَتَشَهَّدُ إِلا فِي آخِرِهِنَّ
“(ঙ) আত্বা (রাঃ) তিন রাক‘আত বিতর পড়তেন। কিন্তু মাঝে বসতেন না। এবং শেষ রাক‘আত ব্যতীত তাশাহহুদ পড়তেন না।” (টীকা.মুসতাদরাকে হাকেম হা/১১৪২)
পর্যালোচনা
এখানেও গ্রন্থকার খিয়ানত করেছেন:
১. বর্ণনাটি মরফু বা মওকুফও নয়; বরং একজন তাবেঈর আমল মাত্র।
২. যেখানে সাহাবীর মওকুফ বর্ণনাকেও তিনি দলিল মানতে নারাজ, সেখানে তিনি তাবেঈর আমলকে দলিল হিসেবে উল্লেখ করে যাচ্ছেন।
৩. বর্ণনাটির হুকুম তথা মান কী গ্রন্থকার বলেননি। টীকায় তিনি কেবল হাকেমের বরাত উল্লেখ করেই ক্ষ্যান্ত রয়েছেন। অথচ এর সনদে: (الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ) হাসান ইবনে ফজল রয়েছেন যিনি মুসলিম ইবনে ইবরাহীম থেকে হাদীস বর্ণনাকারী। উক্ত হাসান মাতরুক ও ‘মুত্তাহাম বিল কাযিব’ (মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত)। (আল-মুগনী ফিয-যুআফা, মীযানুল ইতিদাল ও লিসানুল মীযান)। শায়খ নাসীরুদ্দীন আলবানী সাহেব (যঈফা হা.৩৮৭০) উপরোক্ত হাসান বর্ণিত একটি বর্ণনাকে সুস্পষ্ট জাল আখ্যায়িত করেন এবং জাল হওয়ার কারণ হিসেবে তাকেই চিহ্নিত করে বলেন, (قلت : وهذا موضوع ظاهر الوضع؛ آفته البواصرائي هذا؛ واسمه الحسن بن الفضل بن السمح الزعفراني، وهو متروك الحديث؛ كما في “الأنساب” و “اللباب” وغيرهما .)
সুতরাং এ বর্ণনটি কোন ধরণের দলিলযোগ্য নয়। এমন একজন বর্ণনাকারী থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থকার এখানে কোন কিছু না বলে একে দলিল হিসেবে পেশ করে গেলেন, বিষয়টি তার আমানদারীকে মারাত্মকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করে।
গ্রন্থকার – ২৩
গ্রন্থকারের অতিরিক্ত আরেকটি দলিল
গ্রন্থকার বলেন: “এমন কি পাঁচ রাক‘আত পড়লেও রাসূল (ছাঃ) এক বৈঠকে পড়েছেন। : (عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يوتر بخمس ولا يجلس إلا في آخرهن) : পাঁচ রাক‘আত বিতর পড়তেন কিন্তু শেষ রাক‘আত ছাড়া বসতেন না। ”
পর্যালোচনা
সূত্রের সামান্য পার্থক্যে একই হাদীস এসেছে ভিন্ন শব্দে যেখানে: (لا يجلس) ‘বসতেন না’ কথাটি নেই। বরং শব্দ এসেছে: (لا يسلم) ‘সালাম ফিরাতেন না’। দেখুন বাইহাকী আস-সুনানুল কুবরার (হা.৭৮১) বর্ণনায় শব্দ এসেছে:
يُوتِرُ بِخَمْسٍ وَلا يُسَلِّمُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْخَمْسِ حَتَّى يَجْلِسَ فِي الآخِرَةِ وَيُسَلِّمَ – رواه البيهقي في الصغرى والكبرى وأبو عوانة في مستخرجه وابن المنذر في الأوسط)
গ্রন্থকার – ২৪
গ্রন্থকার বলেন:“জ্ঞাতব্য: তিন রাক‘আত বিতর পড়ার ক্ষেত্রে দুই রাক‘আত পড়ে সালাম ফিরিয়ে পুনরায় এক রাক‘আত পড়া যায়। তিন রাক‘আত বিতর পড়ার এটিও একটি উত্তম পদ্ধতি।”
পর্যালোচনা
বিতরের এ পদ্ধতি বিষয়ে গ্রন্থকার মূল বইয়ে কোন হাদীস উল্লেখ না করে টীকায় কিছু বরাত ও একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। তাই “এটিও একটি উত্তম পদ্ধতি” কথাটি যাচাই করার জন্য টীকার বরাতগুলো যাচাই ও পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।
(এক) ইবনে উমর রা. এর বর্ণনা
টীকায় গ্রন্থকার মূলত দুটি বর্ণনার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। প্রথমে যে বরাতটি উল্লেখ করেছেন তা হল: “১২৮৯. বুখারী হা/৯৯১ ১ম খ- পৃ.১৩৫ (ইফাবা হ/৯৩৭২/২২৫) সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৯৬২ সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/৪২০ এর আলোচনা দ্রঃ ২/১৪৮ পৃঃ; দেখুনঃ আলবানী, কিয়ামু রামাযান, পৃঃ২২;…”
পর্যালোচনা:
এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়:
১. সহীহ বুখারীর বর্ণনাটি এরূপ: (وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته ) : হযরত নাফে বলেন, ‘আব্দুল্লাহ ইবনে উমর বিতর সালাতে দুই রাকাত ও এক রাকাতের মধ্যে সালাম ফিরাতেন। এমনকি তার কোন প্রয়োজনের কথাও বলতেন’। (সহীহুল বুখারী হা.৯৯১)
২. সুতরাং বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, এটি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর ব্যক্তিগত আমল, যাকে পরিভাষায় ‘মওকুফ’ বলে। এটি নবীজীর কথা বা কাজ নয়। গ্রন্থকার তার বইয়ে বারবার বিভিন্ন দলিলে ‘মওকুফ’ হওয়াকে দোষ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আর এখানে মওকুফকেই প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করলেন।
৩. এ বইয়ে গ্রন্থকার একটি দলিলকেই একাধিক বানিয়ে দেখানোর উদ্দেশ্যে বারবার উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু এখানে মূল বইয়ে তার দাবীর পক্ষে কোন দলিলই উল্লেখ করেননি। তবে টীকায় একটি ‘মরফু’ বর্ণনার আরবী বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইবনে উমরের এ ‘মওকুফ’ বর্ণনাটি তার পক্ষে প্রধান দলিল হওয়া সত্ত্বেও তিনি তা মূল আলোচনা ও টীকা কোথাও উল্লেখ না করে বরং আরবী ও বাংলা বুখারীর কেবল বরাত উল্লেখ করেই ক্ষান্ত রইলেন কেন? এটা কি এ কারণে যে, উল্লেখ করলে ধরা পড়ে যাবেন: এটি মরফু নয় বরং মওকুফ? তাহলে কি বুখারীর বরাত উল্লেখ করে তিনি পাঠককে ধাঁধায় ফেলতে চেয়েছেন?
৪. গ্রন্থকার এ হাদীসের আরো দুটি বরাত দিয়েছেন (আলবানী সাহেবের ‘সিলসিলা’ (হা/২৯৬২) ও ‘ইরওয়াউল গালীল’ (২/১৪৮)। আর কিতাব দুটির বর্ণনা থেকে বাহ্যত বুঝা যায়,
(ক)
আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. এক রাকাত বিতর পড়তেন। তাই যদি হয়, তাহলে গ্রন্থকার কিতাবদুটি দেখার পরও কেন ‘তিন রাকাত বিতর এর দলিল হিসেবে’ এর বরাত উল্লেখ করলেন? আবার বর্ণনার শব্দও উল্লেখ করেননি?!
কেননা কিতাব দুটিতে বর্ণনাটির শব্দ যথাক্রমে:
এক. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর এক রাকাতে বিতর পড়তেন। আর দুই রাকাত ও এক রাকাতের মাঝে কথা বলতেন। আরবী শব্দ: (كان يوتر بركعة وكان يتكلم بين الركعتين والركعة)(সিলসিলা হা.২৯৬২)
দুই
আব্দুল্লাহ ইবনে উমর দুই রাকাত নামায পড়লেন, অতঃপর সালাম ফিরালেন। তারপর বললেন, অমুকের বাবাকে নিয়ে আস। অতঃপর দাড়ালেন এবং এক রাকাতে বিতর পড়লেন। আরবী শব্দটি: (أن ابن عمر صلى ركعتين ثم سلم، ثم قال: ادخلوا إلى بأبى فلانة، ثم قام فأوتر بركعة) (ইরওয়াউল গালীল ২/১৪৮) আলবানী সাহেব বলেন, এটি ‘আবু দাউদ’ তার ‘সুনানে’ এ শব্দে বর্ণনা করেছেন: (مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل) অর্থাৎ ‘রাতের নামায দুই দুই রাকাত, আর বিতর হল শেষ রাতের এক রাকাত’।
(খ)
যদি গ্রন্থকার উপরোক্তকিতাব দুটির বরাত থেকে তিন রাকাত বিতর পড়ার কথা বুঝে থাকেন এভাবে যে, (أوتر بركعة) অর্থ হল: ‘পূর্বের (দুই) রাকাতের সাথে এক রাকাত মিলিয়ে (তিন রাকাত) বিতর পড়েছেন’, তাহলে সবকিছু সহজ হয়ে যায়। অর্থাৎ যত বর্ণনায় (أوتر بركعة/يوتر بركعة) ‘ এক রাকাতে বিতর পড়া’ শব্দে নবীজীর বিতরের কথা এসেছে, সবগুলোতেই উদ্দেশ্য পূর্বের দুই রাকাতের সাথে মিলিয়ে তিন রাকাত বিতর পড়েছেন।
এক রাকাত বিতর পড়ার হাদীসকে আমরা যেভাবে বুঝেছি, হযরত ইবনে উমরের বর্ণনাটিকে গ্রন্থকার ঠিক সেভাবেই ব্যাখ্যা করলেন। তাই এ ধরণের হাদীস দ্বারা এক রাকাত বিতর প্রমাণ করার আর কোন সুযোগ গ্রন্থকারের বাকী থাকছে না। এখানে গ্রন্থকারকে দুটির একটি পথ অবশ্যই ধরতে হবে। কেননা, দুটি বর্ণনাকেই আলবানী সাহেবও সহীহ বলেছেন এবং গ্রন্থকার এ মত গ্রহণপূর্বক তার বরাত দিয়েছেন।
৫
সবশেষে যদি বলি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. দুই সালামে তিন রাকাত বিতর পড়তেন, তবুও নবীজীর আমল কি ছিল এর দ্বারা তা বুঝা যায় না। কারণ তাঁর চেয়েও বড় ফকীহ ও রাসূলের নিকটতম সাহাবীরা এক সালামে তিন রাকাত বিতর পড়েছেন। তাই বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত হাসান বসরীকে যখন জিজ্ঞেস করা হল: (قيل للحسن: إن ابن عمر كان يُسلم في الركعتين من الوتر؟ فقال : كان عمرُ أفقه منه – كان ينهض في الثالثة بالتكبير) :‘আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. (তিন রাকাত) বিত্রের দুই রাকাতে সালাম ফেরান? তিনি উত্তরে বললেন, উমর রা. তাঁর থেকে বেশী প্রজ্ঞাবান ছিলেন। তিনি (দ্বিতীয় রাকাতে স্বাভাবিক নিয়মে বৈঠক শেষে সালাম না ফিরিয়েই) তাকবীর বলে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন।
[বরাত সহ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে]৬
শেষে গ্রন্থকার বলেন: “দেখুনঃ আলবানী, কিয়ামু রামাযান, পৃঃ২২”; কিন্তু কিয়ামু রামাযান কিতাবের এ পৃষ্ঠায় আলবানী সাহেব কোন হাদীস উল্লেখ না করে কেবল তিন রাকাত বিতরের দুটি তরীকা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে একটি গ্রন্থকারের উল্লিখিত পন্থা। তিনি এ পদ্ধতির স্পষ্ট কোন দলিল উল্লেখ করেননি। বরং মাগরিবের নামাযের সাথে সাদৃশ্য করতে নিষেধাজ্ঞা মর্মে বর্ণিত হাদীস থেকে এটি তিনি ‘বের’ করেছেন। একেই বলে ‘ইজতিহাদ’। প্রশ্ন হয় আলবানী সাহেবের ইজতিহাদকে কি গ্রন্থকার হাদীসের মর্যাদা দিচ্ছেন? আলবানী সাহেবের ইজতিহাদ অনুসরণ করলে তাকলীদ হয় না, হয় ‘হাদীসের অনুসরণ’?
(দুই)
আয়শার রা. এর বর্ণনা
গ্রন্থকার টীকার দ্বিতীয় অংশে ইবনে আবী শাইবার বরাতে একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন এভাবে: “… মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৬৮৭১, ৬৮৭৪ : ( عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بركعة وكان يتكلم بين الركعتين والركعة.)”
পর্যালোচনা
এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়:
১. হাদীসটি হুবহু একই সনদে ইবনে আবী শাইবা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ইমাম ইবনে মাজাহ তার ‘সুনানে’ দুই স্থানে: (হা.১১৭৭ ও হা. ১৩৫৮)। তদ্রƒপ হাদীসটি একই সনদে ইবনে আবী যীব্ থেকে বর্ণিত হয়েছে: মুসনাদে আহমদ (হা.২৫১০৫) আবু দাউদ (হা.১৩৩০, ১৩৩১) সুনানে নাসায়ী (হা.১৬৪৯) সহীহ ইবনে হিব্বান (হা.২৪২২)। এবং যুহরী থেকে একই সনদে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে মুয়াত্তা মালেক (হা. ১২০) ও সহীহ মুসলিম গ্রন্থে (হা. ১৭৫২)।
অর্থাৎ এ বর্ণনাটি হদীসের প্রসিদ্ধ ৭টি কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোথাও হাদীসটি এভাবে নেই। এমনকি ইমাম ইবনে মাজা তাঁর ‘সুনানে’ খোদ ইবনে আবী শাইবা থেকেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, সেখানে বর্ণনাটি এসেছে এভাবে: (يسلم في كل ثنتين ويوتر بواحدة) অর্থাৎ ‘নবীজী প্রতি দুই রাকাতে সালাম ফেরাতেন এবং এক রাকাতে বিতর পড়তেন’।
আর শায়খ নাসীরুদ্দীন আলবানী সাহেব (রহ.) তার ‘সিলসিলাতুস সহীহায়’ ইবনে আবী শাইবার বর্ণনাটি উল্লেখ করে এর সমর্থনে এ শব্দে একটি বর্ণনাও দেখাতে পারেননি।
২
সুতরাং উল্লিখিত বর্ণনাটি শায্ ও দলবিচ্ছিন্ন। ফলে সনদ সহীহ হওয়া সত্ত্বেও এটি সহীহ নয়। কারণ এটি একই হাদীসের আরো আট-দশটি বর্ণনার বিরোধী।
৩
এটিকে সহীহ বলতে হলে এর ব্যাখ্যা করতে হবে এ হাদীসের অন্য সকল বর্ণনার আলোকে। আর তা হলে তিন রাকাত বিতরে দুই রাকাতে সালাম ফিরানোর বিষয়টি অন্তত এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় না।
৪
গ্রন্থকার নাসীরুদ্দীন আলবানী সাহেবের যে বরাত উল্লেখ করেছেন, সেখানে শায়খ আলবানী বর্ণনাটি উল্লেখ করে বলেন,
قلت : و هذا إسناد عزيز صحيح على شرط الشيخين، وأصله في ” صحيح مسلم ” (২/ ১৬৫) من طريق أخرى عن الزهري به أتم منه دون قوله : ” و كان يتكلم .. ” . و كذلك رواه ابن حبان ( ৪/৬৯/২৪২২) ، و غيره ، وهو مخرج في صلاة التراويح ( ص ১০৬ ). و روى ابن حبان ( ৪/৬৬ و ৬৭ و ৬৬৮ ) من طريق ابن أبي ذئب و غيره الطرف الأول منه . و الحديث شاهد قوي لما رواه نافع : …
অর্থাৎ, “এ সনদ বুখারী মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ, মূল বর্ণনাটি সহীহ মুসলিমে (২/১৬৫) অন্য সূত্রে যুহরী থেকে আরো বিস্তারিতভাবে এসেছে। তবে মুসলিমে ‘তিনি দুই ও এক রাকাতের মাঝে কথা বলতেন’ অংশটি নেই। তদ্রƒপ ইবনে হিব্বান প্রমুখ এটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে হিব্বান ইবনে আবী-যীব সূত্রেও হাদীসটির কেবল প্রথম অংশটি (অর্থাৎ (كان يوتر بركعة) নবীজী এক রাকাতে বিতর পড়তেন) উদ্ধৃত করেছেন। …”
অর্থাৎ মুসলিম ও ইবনে হিব্বানের কোন বর্ণনায়ই দ্বিতীয় অংশটি নেই। তবুও আলবানী সাহেব এ হাদীসের সনদকে সহীহ বলেছেন।
একই হাদীসে একদিকে ইবনে আবী শাইবায় এসেছে, ‘দুই রাকাত ও এক রাকাত (তিন রাকাত বিতরে) এর মাঝে কথা বলতেন’; আর মুসলিম, ইবনে হিব্বানসহ অন্যান্য কিতাবে এসেছে, ‘এক রাকাতে বিতর পড়তেন’। মুসলিমের যে বর্ণনার বরাত তিনি উল্লেখ করেছেন এর শব্দ হল: (إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة) ‘… প্রতি দুই রাকাতে সালাম ফিরাতেন, আর এক রাকাতে বিতর পড়তেন’ (মুসলিম হা.১৭৫২)। অর্থাৎ ইবনে আবী শাইবার বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় তিন রাকাত বিতর পড়তেন, আর মুসলিমসহ অন্যদের বর্ণনা দ্বারা স্পষ্টত বুঝা যায়, এক রাকাত বিতর পড়তেন। এক হাদীসের দুটি বর্ণনায় এমন পরস্পর বিপরীতমুখী বক্তব্য থাকার পরও দুটি একই সাথে সহীহ, নাকি দুটির একটি? বিষয়টি আলবানী সাহেব পরিস্কার করেননি।
৫
শায়খ আলবানী যদি দুটি দ্বারা একই অর্থ বুঝে থাকেন, অর্থাৎ উভয় বর্ণনায় ‘নবীজী তিন রাকাত বিতর পড়তেন’, তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই। তখন যত বর্ণনায় ‘এক রাকাত’ বিতরের কথা এসেছে সবগুলি দ্বারাই তিন রাকাত বিতর পড়া প্রমাণ হয়ে যাবে । আলবানী সাহেব হয়ত তাই বুঝেছেন। কেননা তিনি এখানে এ বর্ণনাটিকে ইবনে উমরের আমলের সমর্থক ধরেছেন। ইবনে উমরের আমল দিয়েই তিনি তার ‘কিয়ামু রামাযান’ কিতাবে দুই সালামে তিন রাকাত বিতর প্রমাণ করেছেন। কিন্তু যদি তিনি একটি দিয়ে এক রাকাত বিতর, আর অপরটি দিয়ে তিন রাকাত বিতর প্রমাণ করতে চান তাহলে আপত্তি থাকবে একই হাদীসের বিপরীতমুখী দুটি বর্ণনা এক সাথে সহীহ হয় কি করে?
৬
আলবানী সাহেব বর্ণনাটির বরাতে মুসলিম, ইবনে হিব্বান ও অন্যান্য কিতাবের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু হুবহু ইবনে আবী শাইবার সনদে তার থেকেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজাহ তার ‘সুনানে’ (হা.১১৭৭ ও হা. ১৩৫৮)। কিন্তু তিনি কুতুবে সিত্তার অংশ ইবনে মাজার বরাত উল্লেখ করেননি কেন? অথচ ইবনে মাজা এটি ইবনে আবী শাইবা থেকেই বর্ণনা করেছেন।
হাদীসটি একই সনদে ইবনে আবী শাইবায় এসেছে এক শব্দে, আর একে আলবানী সাহেব বলেছেন: এ সনদ বুখারী মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। ঠিক এ সনদটিতেই ইবনে মাজায় বর্ণনাটি এসেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন শব্দে এভাবে:“ (يسلم في كل ثنتين ويوتر بواحدة) অর্থাৎ ‘নবীজী প্রতি দুই রাকাতে সালাম ফেরাতেন এবং এক রাকাতে বিতর পড়তেন”। যেহেতু সনদ হুবহু এক, তাই এখানেও আলবানী সাহেবকে বলতে হবে: এ সনদ বুখারী মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ।
৭
এখানে আলবানী সাহেবের তাহকীক মারাত্মক ত্রুটিপূর্ণ বা একেবারেই অসম্পূর্ণ। আর এ অপূর্ণাঙ্গ বা ত্রুটিপূর্ণ তাহকীকের তাকলীদ করেই গ্রন্থকার এমন বেড়াজালে আটকা পড়েছেন। কোন বর্ণনার কি অর্থে ধরবেন, তা ঠিক করতে পারছেন না।
৮
আবার গ্রন্থকার টীকায় ইবনে আবী শাইবার দ্বিতীয় যে নম্বরটি দিয়েছেন (হা.৬৮৭৪) সেখানেও ইবনে উমর (রা.) এর নিজস্ব আমলের বিবরণ এসেছে, (ثم قام فأوتر بركعة) ‘অতঃপর ইবনে উমর দাড়ালেন এবং এক রাকাতে বিতর পড়লেন’। এতে কি তিন রাকাত বিতরের কথা আছে না এক রাকাতের কথা? গ্রন্থকারের উদ্দেশ্যের সাথে এ বর্ণনা এবং পূর্বের বর্ণনাটির কি আদৌ কোন সামঞ্জস্য আছে? এটিকি দলিলের নামে ধোঁকা নয়?
গ্রন্থকার – ২৫
গ্রন্থকার বলেন: “উল্লেখ্য যে, তিন রাক‘আত বিতরের মাঝে সালাম দ্বারা পার্থক্য করা যাবে না মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ।” টীকা. ১২৯০. ইরওয়াউল গালীল হা/৪২১, ২/১৫০ পৃঃ; আহমদ হা/২৫২৬৪”
পর্যালোচনা
এক স্থানে সহীহ বলে নিজেই আবার হাদীসটিকে যঈফ বললেন!
বর্ণনাটিকে যঈফ প্রমাণ করার জন্য গ্রন্থকার আলবানী সাহেবের ‘ইরওয়াউল্গালীলে’র বরাত দিয়েছেন। আলবানী সাহেব তার ‘ইরওয়াউলগালীল’ গ্রন্থে বলেন: ইমাম আহমদ এটিকে যঈফ বলেছেন যা ‘আল-মুনতাকা’ ও ‘নাইলুল আওতার’ গ্রন্থে এসেছে। এটি মূলত সেই হাদীস যা দিয়ে গ্রন্থকার ‘এক সালামে ও একই বৈঠকে তিন রাকাত বিতর’ প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন এবং সহীহ সাব্যস্ত করে এসেছেন (পৃ.৩৩১)। আলবানী, শাওকানী, ইবনে তাইমিয়া আল-জাদ্দ ও ইমাম আহমদের মতে দুটি একই বর্ণনা। তাই তাদের মতে দুটোই যঈফ। গ্রন্থকার এ হাদীসকেই এক স্থানে সহীহ বলে এসে এখানে আবার যঈফ সাব্যস্ত করছেন! এ কেমন বৈপরিত্য।
কুনূত পড়ার পূর্বে তাকবীর বলা ও হাত উত্তোলন করে হাত বাঁধা
গ্রন্থকার – ২৬
গ্রন্থকার বলেন: “বিতর ছালাতে কিরাআত শেষ করে তাকবীর দিয়ে পুনরায় হাত বাঁধার যে নিয়ম সমাজে চালু আছে তা ভিত্তিহীন।” (পৃ.৩৩৪)
পর্যালোচনা
তাকবীর দিয়ে পুনরায় হাত বাঁধার এ নিয়ম ভিত্তিহীন নয়, বরং সুন্নাহ সম্মত। প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থকারের কথাই বাতিল ও ভিত্তিহীন। বিষয়টি স্পষ্ট করতে আগে গ্রন্থকারের কুনূত পড়ার সহীহ নিয়ম কি ও এর দলিল কি তা পর্যালোচনা করে নেয়া দরকার।
গ্রন্থকার বলেন: “কুনূত পড়ার ছহীহ নিয়ম’: শিরোনামে লেখেন: “বিতরের কুনূত দুই নিয়মে পড়া যায়। শেষ রাক‘আত শেষ করে হাত বাঁধা অবস্থায় দু‘আয়ে কুনূত পড়া। অথবা ক্বিরাআত শেষে হাত তুলে দু‘আয়ে কুনূত পড়া।” (পৃ. ৩৩৬)
প্রথম নিয়মের দলিল
গ্রন্থকার উপরোক্তনিয়মে কুনূত পড়ার কোন দলিল উল্লেখ না করে প্রথম পদ্ধতি আলোচনার পর টীকায় কেবল একটি বরাত উল্লেখ করেছেন এভাবে: “আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ২/৭১ পৃঃ, ২/১৮১ পৃঃ”। অর্থাৎ এ বরাতেই তার দলিল রয়েছে। বরাত অনুযায়ী তালাশ করে দেখা গেল সেখানে কুনূত পড়ার নিয়ম সম্পর্কে কোন হাদীসও নেই, কোন সাহাবী, তাবেয়ীর কোন বক্তব্য বা আমলের উল্লেখও নেই। এতে কেবল ইস্হাক ইবনে রাহুয়াহ’র (জন্ম-১৬১ মৃত্যু-২৩৮) আমলের উল্লেখ রয়েছে। শায়খ আলবানীর বক্তব্য:
قد ذكر المروزى فى ” المسائل ” (ص ২২২): ” كان إسحاق يوترُ بنا… ويرفع يديه فى القنوت ويقنت قبل الركوع، ويضع يديه على ثدييه، أو تحت الثديين(
“মারওয়াযী উল্লেখ করেছেন: ইসহাক আমাদেরকে নিয়ে বিতর পড়তেন। … আর তিনি কুনূতে হাত উঠাতেন, রুকুর পর কুনূত পড়তেন এবং বুকের উপর বা বুকের নিচ বরাবর হাত রাখতেন”।
অধিকন্তু গ্রন্থকার বলেছেন, সঠিক নিয়ম ‘হাত বাঁধা অবস্থায় কুনূত পড়া’। অর্থাৎ তার আপত্তি হাত বাঁধা অবস্থায় কুনূত পড়ার উপর নয়, বরং কুনূতের শুরুতে তাকবীর বলে হাত উঠানোর উপর। কিন্তু তার উল্লিখিত বরাতে আলবানী সাহেব ইসহাক ইবনে রাহুয়ার যে আমল উল্লেখ করেছেন, তাতে রয়েছে ‘তিনি কুনূতে দুই হাত উঠাতেন’। এতে হাত উত্তোলন করাটাই প্রমাণিত হয়ে যায়, যাকে তিনি বাতিল বলে এসেছেন।
২
ইসহাক ইবনে রাহুয়ার কথাই যদি গ্রন্থকারের দলিল হয়, তাহলে দোয়ায়ে কুনূত শেষে চেহারা হাত দিয়ে মাসাহও করতে হবে। কেননা ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ্ দুআয়ে কুনূত শেষে হাত দ্বারা চেহারা মাসাহ করতেন (ইরওয়াউলগালীল ২/১৮০)। কিন্তু গ্রন্থকার তার বইয়ের ৩৩৪-৩৩৫ পৃষ্ঠায় কুনূত পড়ার পর মুখে হাত মাসাহ করা থেকে নিষেধ করেছেন। অথচ এর বিপরীত কোন হাদীসও নেই। উপরন্তু এর পক্ষে যঈফ সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।
৩
ইসহাক ইবনে রাহুয়ার আমল কুনূত পড়ার সময় হাত বেঁধে রাখা নয়। বরং দোয়ার মত হাত উঠিয়ে রাখা। বুঝা গেল এ বরাতে গ্রন্থকারের বক্তব্যের পক্ষে কোন দলিল নেই।
৪
দ্বিতীয় বরাতে (ইরওয়াউলগালীল ২/১৮১ পৃঃ) বাইহাকী ও আলবানীর দুজনের বক্তব্যেই এসেছে দোয়ার মত হাত তুলে রাখার কথা। অথচ গ্রন্থকার এ বরাতটি উল্লেখ করেছেন, তাকবীরের সময় হাত না উঠিয়ে হাত বেঁধে দোয়ায়ে কুনূত পড়ার দলিল হিসেবে। সুতরাং তার দাবির সাথে দলিলের কোন মিল নেই।
৫
আলবানী সাহেব বলেছেন, হযরত আনাস রা. সূত্রে বর্ণিত হাদীসে কুনূতে নাযেলায় (দোয়ার মত) হাত উঠানোর বিষয় প্রমাণিত। কুনূতে বিতর বিষয়ে নয়।
৬
বাইহাকী রহ. পূর্বসুরীদের থেকে কুনূতে নামাযের মত হাত উঠানোর কথা বললেও কারো বর্ণনা উল্লেখ করেননি।
৭
অতঃপর আলবানী সাহেব বলেন, (وثبت مثله عن عمر، وغيره فى قنوت الوتر) :“বিতরের কুনূত বিষয়েও অনুরূপ (দোয়ার মত করে) হাত তোলা উমর প্রমুখ থেকেও প্রমাণিত আছে।” কিন্তু আলবানী সাহেব আনাস রা. এর বর্ণনার বরাত উল্লেখ করলেও, উমরের বর্ণনাটি কোথায় রয়েছে এর কোন ইঙ্গিতও দেননি। তৎপ্রণীত ‘আসলু ছিফাতিস সালাত’ এ (পৃ.৩/৯৫৭-৯৫৯) খুলে দেখলাম সেখানে তিনি উমর রা. এর বর্ণনাটি এনেছেন, কিন্তু তা ফজরের নামাযের কুনূতে, অর্থাৎ কুনূতে নাযেলায়। সুতরাং বিতরের কুনূতে হাত উঠানোর বিষয়টি তিনি প্রমাণ করতে পারেননি।
দ্বিতীয় নিয়মেরও দলিল নেই
প্রথম নিয়মে তো দলিল উল্লেখ না করলেও অন্ততঃ একটি বরাত উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় নিয়ম উল্লেখ করার পর না তিনি কোন দলিল উল্লেখ করেছেন, আর না কোন বরাত উল্লেখ করেছেন। এমনকি এর কোন টীকাও দেননি।
তাকবীর দিয়ে হাত বাঁধার দলিল ও গ্রন্থকারের বক্তব্যের অসারতা
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বিতর নামাযের শেষ রাকাতে কুনূতের জন্য তাকবীর বলে হাত উঠাতেন। এ বিষয়ে ইবনে মাসউদ রা. থেকে বিশুদ্ধসূত্রে একাধিক বর্ণনা হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে এসেছে। (টীকা-১) ইমাম বুখারী একে সহীহ বলেছেন। [দেখুন: শরহু মুশকিলিল আসার ১১/৩৭৪, শায়খ শুআইব বলেন: এর সনদ হাসান। আলমু‘জামুল কাবীর, তাবারানী ৯/২৪৩ হা.৯১৯২, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৪/৫৩০ হা. ৭০২১, জুয্উ রাফইল ইয়াদাইন: ইমাম বুখারী পৃ.১৪৬ হা. ১৬৩]
অনুরূপ তাবেয়ী ইবরাহীম নাখাঈ থেকেও সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। (টীকা-২) [দেখুন: মুছান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৪/৫৩১ হা.৭০২৩, মুছান্নাফে আব্দুর রায্যাক হা.৫০০১, কিতাবুল আসার, মুহাম্মদ রহ. এর বর্ণনা পৃ.২০৭, আবু ইউসুফ রহ. এর বর্ণনা ৬৬, কিতাবুল হুজ্জা আলা-আহলিল মদীনা, পৃ.৫৬ শারহু মাআনিল আসার ১/৩৯১]
এ ছাড়া মারওয়াযী তাঁর ‘কিয়ামুল লায়ল’ গ্রন্থে [পৃ.২৯৪] হযরত উমর, আলী ও বারা ইবনে আযিব রা. থেকেও তাকবীরের কথা উল্লেখ করেছেন। (টীকা-৩)
হযরত সুফয়ান সাউরী রহ. তাঁর পূর্বসুরী তাবেঈ ও তাবে তাবেঈদের থেকেও কুনূতের শুরুতে তাকবীর বলে হাত উঠানোর কথা বর্ণনা করেছেন। [মুখাতাছারু কিয়ামিল লাইল, ২৯৪, ২৯৬] ইমাম আহমদ রহ. বলেন, রুকুর পূর্বে যদি কুনূত পড়া হয় তাহলে তাকবীর দিয়ে কুনূত শুরু করবে। [মুখাতাছারু কিয়ামিল লাইল, ইবনে নছর মারওয়াযী, ২৯৪]
গ্রন্থকার – ২৮
অতঃপর গ্রন্থকার ইবনে মাসউদ রা. এর হাদীসটি সম্পর্কে বন্তব্য করেছেন যে, “বর্ণনাটি ভিত্তিহীন। আলবানী (রহঃ) বলেন, لم أقف على سند عند الأثرم، لأنني لم أقف على كتابه … وغالب الظن أنه لا يصح : আছরামের সনদ সম্পর্কে অবগত নই। এমনকি তার কিতাব সম্পর্কেও অবগত নই। … আমার একান্ত ধারণা, এই বর্ণনা সঠিক নয়।” (অর্থাৎ ১. আসরাম বর্ণিত এ হাদীসের সনদ পাওয়া যায়নি কেননা কিতাবটিই তিনি পাননি ২. তিনি ধারণা করলেন এটি সহীহ নয়)
পর্যালোচনা
১
ভুল তরজমা
তিনি লেখেছেন: “এমনকি তার কিতাব সম্পর্কেও অবগত নই ” এটি আলবানী সাহেবের বক্তব্যের ভুল তরজমা। বিশুদ্ধ তরজমা হল: ‘কেননা আমি তার কিতাবের সন্ধান পাইনি’।
২
নিজের থেকে সনদবিহীন হাদীস উল্লেখ করে তাকে যঈফ সাব্যস্ত করা?
ক. নবীজীর নামায ও দলিলসহ নামাযের মাসায়েল বই দুটি গ্রন্থকারের সামনে রয়েছে। আর দুটি বইতেই হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) এর বর্ণনাটি উদ্ধৃত হয়েছে মুছান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ও শরহু মুশকিলিল আসার গ্রন্থদ্বয়ের বরাতে। এর সনদ সহীহ। কিন্তু আফসোসের কথা, গ্রন্থকার সহীহ সনদ বিশিষ্ট বর্ণনাটি না এনে আলবানী সাহেবের কিতাব থেকে আস্রামের বর্ণনা উল্লেখ করলেন: যে কিতাবটি পাওয়া যায় না। তারপর বর্ণনাটিকে সহীহ নয় বলে তার বক্তব্যকে প্রমাণ করে দিলেন!
খ
আলবানী সাহেবের ‘ইরওয়াউল গালিল’ কিতাবের যে পৃষ্ঠা থেকে (২/১৬৯) গ্রন্থকার এ তাহক্বীকটি পেশ করেছেন সেখানেই আলবানী সাহেব বলেছেন, এটি ইবনে আবী শাইবা, তাবারানী ও বাইহাকীর বর্ণনায়ও এসেছে। কিন্তু তিনি তাহক্বীক করতে যেয়ে উক্ত হাদীস গ্রন্থ সমূহ ও সেগুলির সনদের প্রতি কোন ইঙ্গিতও দেননি।
গ
গ্রন্থকার নিজেও পূর্বের টীকায় ইবনে আবী শাইবা (হা.৭০২১-৭০২৫) ও আব্দুর রাযযাকের (হা.৫০০১) বরাত উল্লেখ করেছেন। তার টীকায় হা. ৭০২১-৭০২৫ পর্যন্ত ইবনে মাসউদ রা., ইবরাহীম নাখায়ী, হাকাম, হাম্মাদ ও আবু ইসহাক থেকে মোট ছটি বর্ণনার বরাত দিয়েছেন। কিন্তু তাহক্বীকের সময় কেবল আসরামের বর্ণনা সম্পর্কিত আলবানীর বক্তব্য উল্লেখ করে ক্ষান্ত রইলেন। আর এ ছটি বর্ণনা সম্পর্কে কিছুই বললেন না। আবার তিনি ইবনে মাসউদ রা. এর বর্ণনা সম্পর্কে টীকায় দ্বিতীয় নাম্বারে আব্দুর রাযযাকের যে (হা.৫০০১) বরাত উল্লেখ করেছেন, তাতে বর্ণনা আছে ইবরাহীম নাখাঈ থেকে, ইবনে মাসউদ থেকে নয়।
ঘ
ইমাম বুখারী রহ. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর এ বর্ণনাটিকে সহীহ বলেছেন। তিনি জুয্উ রাফইল ইয়াদাইন গ্রন্থে (পৃ.১৪৬ হা. ১৬৩) এ বর্ণনাটি এবং অনুরূপ আরো কিছু বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন: (هذه الأحاديث كلها صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يخالف بعضها بعضا، وليس فيها تضاد لأنها في مواطن مختلفة،) : ‘এ সব বর্ণনাগুলোই সহীহ …’। ইমাম তাহাবী রহ. ও হাদীসটিকে সহীহ ধরে নিয়েই দলিল পেশ করেছেন তাঁর ‘শরহু মুশকিলুল আসার’ গ্রন্থে। শায়খ শ‘আইব আরনাউত বলেন: ‘হাদীসটি হাসান, কেবল হুদাইজ ইবনে মুআবিয়া ব্যতিত সকলেই বুখারী মুসলিমের বর্ণনাকারী …’। [মুশকিলিল আসার ১১/৩৭৪]
মুছান্নাফে ইবনে আবী শাইবার সনদটিও ছহীহ লিগাইরিহি বা হাসান। তাছাড়া ইবনে মাসউদ রা. এর শিষ্যদের কাছ থেকেই ইবরাহীম নাখাঈ ইলম শিখেছেন। তিনি এ তরীকাই তাদের থেকেই গ্রহণ করেছেন। সুতরাং এতে বর্ণনাটি আরো শক্তিশালি হয় বৈকি।
ঙ
আলবানী সাহেবও এ বর্ণনা বিষয়ে দুটি বড় ধরণের আপত্তিকর কাজ করেছেন। আর গ্রন্থকার এক্ষেত্রে তার অন্ধ তাকলীদ করেছেন।
(এক)
তিনি আছরামের বর্ণনা সম্পর্কে বলেছেন, এর সনদ তার জানা নেই। কিন্তুযে হাদীসের সনদ সম্পর্কে তিনি জানতে পারেননি, সে সম্পর্কে তার উচিত ছিল: মন্তব্য থেকে বিরত থাকা। অথবা মন্তব্য করলেও সম্ভাবনা ব্যক্ত করে বলা। কিন্তু তিনি বলে দিলেন: “আমার প্রবল ধারণা যে, এটি সহীহ নয়”! তিনি যখন বর্ণনাটি তিনটি কিতাবে একই সনদে পেয়েছেন তখনি তাঁর ধারণা জন্মেছে যে, হয়ত সেখানেও সেই একই সনদ হয়ে থাকবে।
আর যে সনদ পাওয়া গেছে সেটি লাইছ ইবনে আবী সুলাইম এর কারণে ‘তার দৃষ্টিতে’ যঈফ, সুতরাং তিনি বলে দিলেন সবই যঈফ! কিন্তু তিনি কি করে ভাবলেন যে, আছরামের কিতাবেও এর একই সনদ হবে? অথচ তাঁর হাতের নাগালের কিতাব ‘শরহু মুশকিলিল আসারে’ই এ বর্ণনাটি উক্ত লাইছ ইবনে আবী সুলাইম ব্যতিত ভিন্ন সনদে এসেছে যে সম্পর্কে তার খবরই নেই!
তাই এরও যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে যে, আছরামের কিতাবে বর্ণনাটি তৃতীয় কোন সনদেও থাকতে পারে। বা অন্তত মুশকিলুল আসারে যে সহীহ সনদে এসেছে তাও হতে পারে। সুতরাং এমন চোখ বুঝে একটি সনদকে যঈফ বলে দেয়া যায় কি?
দুই)
আলবানী সাহেব ইবনে আবী শাইবায় বর্ণিত হাদীসের বর্ণনাকারী ‘লাইছ ইবনে আবী সুলাইমকে’ যঈফ বলেই বর্ণনাটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু লাইছ এর কারণে হাদীসকে যঈফ বলে দেওয়া যায় না।
লাইছ সম্পর্কে হাদীসবিদগণর মতামত নিম্নরূপঃ
লাইছ ইবনে আবী সুলাইম রহ. এর বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। কারণ, ইমাম বুখারী সহীহ বুখারীর ‘তালীকাতে’ তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। ইমাম মুসলিম রহ. সহীহ মুসলিমের ভূমিকায় তাকে আতা ইবনুস সাইব এর মত দ্বিতীয় পর্যায়ের বর্ণনাকারী গণ্য করেছেন। এবং তাকে সত্যবাদিতা, দোষ মুক্ততা ও ইলমে হাদীসের সাথে ঘনিষ্টতার গুণে গুণান্বিত করেছেন। (টীকা-৪)
আবুদাউদ তিরমিযী নাসাঈ ইবনে মাজা চারটি কিতাবেই তাঁর হাদীস রয়েছে। তাঁর সম্পর্কে ইমাম বুখারী রহ. বলেন: (صدوق يهم) ‘বিস্বস্ত, কখনো ভুল করে থাকেন’। ইমাম ইবনে আদী রহ. তার বর্ণিত কিছু (মুনকার) আপত্তিকর বর্ণনা উল্লেখ করার পর বলেন: (لَهُ أَحَادِيْثُ صَالِحَةٌ غَيْرُ مَا ذَكَرتُ، وقد روى عنه شعبة والثوري وَغَيْرُهُمَا مِنَ الثِّقَاتِ، وَمَعَ الضَّعفِ الَّذِي فِيْهِ يُكْتَبُ حَدِيْثُه) : অর্থাৎ ‘এছাড়া তার কিছু ভাল হাদীসও রয়েছে। শোবা, ছাউরী প্রমুখ নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিগণ তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর মধ্যে যে দূর্বলতাটুকু রয়েছে তা সত্ত্বেও তার হাদীস লিপিবদ্ধ করা যায়’।
ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন: (وليث وإن كان ضعيف الحفظ فإنه يعتبر به ويستشهد فيعرف أن له من رواية عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أصلا، وقال أيضا: … وتابع أبا إسحاق على روايته عن عبد الرحمن المذكور ليث بن أبي سليم وحديثه يستشهد به) : ‘অর্থাৎ ‘যদিও লাইছ দূর্বল স্মৃতি শক্তির অধিকারী তবুও অন্য বর্ণনা সহায়ক ও সমর্থক হিসেবে গ্রহণযোগ্য …. ।’ অন্যত্র বলেন: ‘আব্দুর রহমান থেকে আবু ইসহাকের সমর্থন করেছেন লাইছ। আর তার বর্ণনা সমর্থক হিসেবে উল্লেখযোগ্য। [ফাতহুল বারী: ভূমিকা ৩৪৯, ১/২৫৮]
ইমাম যাহাবী রহ. বলেন: (قُلْتُ: بَعْضُ الأَئِمَّةِ يُحَسِّنُ لِلَّيْثِ، وَلاَ يَبلُغُ حَدِيْثُه مَرتَبَةَ الحَسَنِ بَلْ عِدَادُه فِي مَرتَبَةِ الضَّعِيْفِ المُقَاربِ، فَيُرْوَى فِي الشَّوَاهِدِ وَالاعْتِبَارِ، وَفِي الرَّغَائِبِ، وَالفَضَائِلِ، أَمَّا فِي الوَاجِبَاتِ، فَلاَ.) : ‘কোন কোন ইমাম লাইছের হাদীসকে হাসান গণ্য করেছেন। কিন্তু তার হাদীস হাসান পর্যায়ের নয়। বরং তা হাসানের নিকটবর্তী যঈফরূপে গণ্য। তাই তা (অন্য বর্ণনার) সহায়ক ও সমর্থকরূপে বর্ণনা করা যাবে। এবং ফযীলতের বিষয়েও বর্ণনা করা যাবে। কিন্তু ওয়াজিব বিধান সাব্যস্ত করতে তা বর্ণনা করা যাবে না’। [সিয়ারু আলামিন নুবালা ৬/১৭৯]
সুতরাং তাঁর বর্ণনা সাধারণ সকল যঈফের মত নয়, বরং হাসানের কাছাকাছি পর্যায়ের। ফযীলতের ক্ষেত্রে তাঁর বর্ণনায় নির্ভর করা যায়। অন্য বর্ণনার সমর্থন পেলেই তা হাসান স্তরে উন্নীত হয়। তখন বিধানের ক্ষেত্রেওতো প্রযোজ্য হবে। একারণে আলবানী সাহেবও ‘সিলসিলতুস্-সহীহা’ গ্রন্থে (হা.৫৮৬) লাইছের একটি বর্ণনাকে সালামা ইবনে ওয়ারদান সূত্রে বর্ণিত আরেকটি যঈফ বর্ণনার সমর্থনে হাসান বলেছেন। আলোচ্য হাদীসেও লাইছের বর্ণনার সমর্থনে রয়েছে, তাহাবীর শারহু মুশকিলিল আসারের বর্ণনা। তাই আলবানী সাহেবের যুক্তিতেই একে হাসান বলতে হবে।
লাইছ রহ. এর স্মৃতিশক্তির দূর্বলতা কখন থেকে
লাইছের যঈফ হওয়ার মূল কারণ ইঙ্গিত করে ইমাম ইবনে হিব্বান রহ. বলেন: (اخْتُلِطَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ، … كُلُّ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُ فِي اخْتِلاَطِه.) : অর্থাৎ ‘শেষ বয়সে তার ইখতিলাত: স্মৃতি শক্তির মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল’। আর এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন লাইছ থেকে দুজন নির্ভরযোগ্য রাবী।
আব্দুস সালাম ইবনে হারব ও যায়েদা ইবনে কুদামা। তন্মধ্যে যায়েদা একদিকে লাইছের এলাকার লোক এবং তার প্রবীণ শিষ্য। আবার তার স্বভাব ছিল কারো কাছ থেকে হাদীস নেয়ার সময় এবং তা বর্ণনা করার সময় ভাল রকম যাচাই-বাছাই করা। এ কারণেই ইমাম আহমদ বলেন: ‘যায়েদা ও যুহাইর থেকে কোন হাদীস শুনলে, তা আর কারো কাছ থেকে না শুনলেও কোন সমস্যা নেই। তবে আবু ইসহাকের হাদীস ব্যতিত’। তিনি আরো বলেন: ‘চারজন বর্ণনাকারী হলেন, মুতাসব্বিত [নির্ভুল বর্ণনাকারী] সুফইয়ান, শুবা যুহাইর ও যায়েদা। [সিয়ারু আলামিন নুবালা]
তিনি আরো বলেন: ‘যায়েদা কোন হাদীস বর্ণনাকালে ইত্কান তথা দৃঢ়তা ও যতেœর সাথে করত’। একবার এক উপলক্ষে সুফইয়ান যায়েদাকে বললেন: ‘নিশ্চয় আপনি সিকাহ তথা নির্ভরযোগ্য এবং সিকাহ বর্ণনাকারী থেকেই আমাদেরকে হাদীস শুনিয়ে থাকেন …’। (যায়েদা এতে মৌন সমর্থন ব্যক্ত করলেন)। [ইলাল]।
সুতরাং যায়েদা ইবনে কুদামা হলেন লাইছের যে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন তা হয়ত তার ইখতিলাত তথা স্মৃতিশক্তি দূর্বল হওয়ার আগের, অথবা পরের হলেও তা ছিল নির্ভুল। আব্দুস সালামও লাইছ থেকে একই হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এ বর্ণনায় লাইসের কোন ভুল হয়নি। সম্ভবত একারণেই ইমাম বুখারী রহ. যায়েদা সূত্রে লাইছের এ বর্ণনাটিকে স্পষ্ট ভাষায় সহীহ বলে দিয়েছেন।
চ
গ্রন্থকার আলবানী সাহেবের এমন দলিলবিহীন ও অনুমান নির্ভর হুকুমের অন্ধ তাকলীদই করেছেন। তার মাথায় এতটুকু কথাও আসেনি যে, আছরামের সনদকে তিনি কিভাবে যঈফ বলছেন অথচ তিনি তা দেখেনইনি।
গ্রন্থকার – ২৯
বাতিল কথার পুনরাবৃত্তি!
গ্রন্থকার বলেন: “আরো উল্লেখ্য যে, উক্ত বর্ণনার মধ্যে পুনরায় হাত বেঁধে কুনূত পড়ার কথা নেই। এ মর্মে কোন দলীলও নেই। অথচ এটাই সমাজে চলছে। বরং এটাকে ওয়াজিব বলা হয়েছে।”
পর্যালোচনা
এক
‘হাত বেঁধে’ কুনূত পড়াকে ওয়াজিব বলা হয়নি। বরং শুধু কুনূত পড়াকেই ওয়াজিব বলা হয়েছে। হানাফী মাযহাবের ফিকহের কিতাবে যা স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। তাই এখানে গ্রন্থকার নিজে ভুল বুঝে অন্যের উপরে দোষ চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। এটা তার অন্যায় আপত্তি।
দুই
“এ মর্মে কোন দলীলও নেই।” একথা দ্বারা গ্রন্থকার কি ধরণের দলিল চান? নবীজীর বক্তব্য বা আমল, সাহাবী বা তাবেয়ীর ফতোয়া বা আমল, না কোন ইমামের কথা বা আমল? গ্রন্থকার তার বইয়ে কুনূত পড়ার ছহীহ নিয়মের যে দলিল দিয়েছেন তাতে পাওয়া গেছে শুধু ইমাম ইসহাক ইবনে রাহুয়ার আমল বা কর্ম (দেখুন:পৃ.৩৩৬ টীকা-১৩০৪, ইরওয়াউল গালীল ২/৭১)। এ থেকে তো বুঝা যায় কোন ইমামের কথা বা আমল পাওয়া গেলেই ছহিহ দলিল হয়ে যায়।
তাই যদি হয় তাহলে হাত বেঁধে কুনূত পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে মহান ফকীহ তাবেয়ী ইবরাহীম নাখায়ী (মৃ.৯৬ হি.) থেকে। যিনি মূলত ইলম শিখেছেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর প্রধান শিষ্যদের কাছ থেকে। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে তাকবীর বলা ও হাত উঠানোর যে সহীহ বর্ণনা রয়েছে এরই বাস্তবরূপ ও সহীহ ব্যাখ্যা হল ইবরাহীম নাখাঈর কথা ও আমল। কারণ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর প্রধান ফকীহ শিষ্য হলেন আলকামা। আলকামার প্রধান ফকীহ শিষ্য হলেন ইবরাহীম নাখাঈ। [সিয়ারু আলামিন নুবালা] তাই এটি নিঃসন্দেহে গ্রন্থকারের দলিলের চেয়ে বহু গুণে শক্তিশালী। [দেখুন: কিতাবুল হুজ্জাহ আলা আহলিল মদীনা, ইমাম মুহাম্মদ পৃ. ২০০ (পৃ.৫৫ পুরাতন ছাপা) কিতাবুল আছার, ইমাম মুহাম্মদের বর্ণনা পৃ.২০৭]
তিন
গ্রন্থকারের উপরিউক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে বরং ইমাম আবু হানীফার (মৃত.১৫০ হি.) ফতোয়া ও আমলই এ বিষয়ে দলিল হওয়ার জন্য যথেষ্ট। কেননা ইসহাক ইবনে রাহুইয়া (মৃত.২৩৮ হি.):এর আমল এর চেয়ে তার আমলের গুরুত্ব অবশ্যই বেশি। আবু হানীফা রহ. ছিলেন তাবেঈ। আবার তিনি সাহাবীদের থেকে সরাসরি শিক্ষাপ্রাপ্ত বহু বড় বড় তাবেঈ থেকেই নামায শিখেছেন। যে সুযোগ ইসহাক ইবনে রাহুয়া রহ. এর হয়নি।
চার
গ্রন্থকার বলেন: “আরো উল্লেখ্য যে, উক্ত বর্ণনার মধ্যে পুনরায় হাত বেঁধে কুনূত পড়ার কথা নেই। ” আমি বলব এ বর্ণনা দ্বারা যদি এতটুকু প্রমাণিত হয় যে, কুনূতের শুরুতে তাকবীর বলবে আর হাত উঠাবে তাতেই যথেষ্ট। কেননা কুনূত পড়ার সময় হাত কিভাবে থাকবে বিষয়টি গ্রন্থকার নিজেই ‘কুনূত পড়ার ছহীহ নিয়ম’ শিরোনামে বলে দিয়েছেন। তিনি বলেন: (পৃ.৩৩৬) “শেষ রাক‘আতে হাত বাঁধা অবস্থায় দু‘আয়ে কুনূত পড়া”। ব্যস, কুনূত পড়ার আগে তাকবীর বলা ও হাত উঠানোর দলিলতো আছেই। এখন কুনূত পড়ার সময় হাত বেঁধে রাখার দলিল কি তা গ্রন্থকার বলুন! আমরাত ইবরাহীম নাখাঈর আছার উল্লেখ করেছি।
দু‘আয়ে কুনূত
গ্রন্থকার – ৩০
গ্রন্থকার বলেন: “(৫) বিতরের কুনূতে ‘আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা ও নাস্তাগফিরুকা … মর্মে ‘কুনূতে নাযেলার’ দু‘আ পাঠ করা: অধিকাংশ মুছল্লী বিতরের কুনূতে যে দু‘আ পাঠ করে থাকে, সেটা মূলতঃ কুনূতে নাযেলা। (টীকা:১৩০৯. …) রাসূল (ছাঃ) বিতর ছালাতে পড়ার জন্য হাসান (রাঃ) কে যে দু‘আ শিক্ষা দিয়েছিলেন, তা মুছল্লীরা প্রত্যাখ্যান করেছে। অতএব বিতরের কুনূত হিসাবে রাসূল (ছাঃ) – এর শিক্ষা দেওয়া দু‘আ পাঠ করতে হবে। … (তরজমা) …রাসূল (ছাঃ) আমাকে কতিপয় বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন সেগুলো আমি বিতর ছালাতে বলি। …।”
পর্যালোচনা
কোন কুনূতকে প্রত্যাখ্যান করা হয়নি
হানাফী মাযহাবের যে কোন নির্ভরযোগ্য কিতাব খুললেই দেখা যাবে যে, কুনূতের জন্য কোন একটি দুআকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি (আল-মাবসূত লি মুহাম্মদ ১/১৬৪)। বরং হাদীস ও আসারে কুনূত হিসেবে বর্ণিত সব দোয়াই যে পড়া যায় সে কথাই বলা হয়েছে। একথা সাধারণ পাঠকের জন্য লেখা ‘নবীজীর নামায’ (পৃ.২৪৩) বইয়ে এভাবে বলা হয়েছে, ‘বিতরের তৃতীয় রাকাতে রুকুর আগে দুআ কুনূত পড়া হবে। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন দুআ হাদীস শরীফে এসেছে। ..’। ‘দলিলসহ নামাযের মাসায়েল’ (প্রথম সংস্করণ) এ একথা স্পষ্ট বলা আছে। বরং হানাফী মাযহাবের বহু ফকীহ হাদীসে বর্ণিত প্রসিদ্ধ দুটি দুআই কুনূতে পড়ার কথা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন। [দেখুন, বিতর সালাত প্রথম অধ্যায় দুআয়ে কুনূতের আলোচনা]
সুতরাং তার এ দাবী বাস্তবসম্মত নয়। তবে আমাদের দেশের জন সাধারণের জন্য সহজ করণার্থে অনেকে একটি দোয়াই উল্লেখ করে থাকেন। অপর দোয়াটি প্রত্যাখ্যান করার অর্থে কখনোই নয়।
গ্রন্থকার – ৩১
গ্রন্থকার বলেন “ বিতরের কুনূতে ‘আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা ও নাস্তাগফিরুকা … অধিকাংশ মুছল্লী বিতরের কুনূতে যে দু‘আ পাঠ করে থাকে, সেটা মূলতঃ কুনূতে নাযেলা। (টীকা:১৩০৯. …)” (পৃ. ৩৩৭)
পর্যালোচনা
‘আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা …’ দুআটি বিতরের কুনূতেও পড়া যায়
গ্রন্থকার তার দাবী অর্থাৎ ‘আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতাঈনুকা…’ দুআটি কুনূতে নাযেলা হওয়ার দলিল হিসেবে টীকায় একটি বরাত দিয়েছেন। সে বরাতে রয়েছে ‘হযরত উমর রা. ফজরের নামাযের কুনূতে এ দুআটি পড়তেন’। কুনূতে নাযেলার বিষয়ে কোন কথা বলা হয়নি। আলবানী সাহেব রহ. এটিকে কুনূতে নাযেলা সাব্যস্ত করেছেন। আর গ্রন্থকার তারই অনুসরণ করেছেন। [ইরওয়াউল গালীল ২/১৭১]
আর তাই যদি হয় তাহলে হযরত উমর রা. থেকেই একাধিক বর্ণনা আছে তিনি এ দুআটি বিতরের কুনূতেও পড়তেন। [আল-আউসাত, ইবনিল মুনযির ৫/২১৪, ছালাতুল বিতর, ইবনু নছর সাথে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত আনাস, উবাই ইবনে কাব, ইবরাহীম নাখাঈ, আতা, তাউস, সাঈদ ইবনুল মাসাইয়্যিব প্রমুখ বিতরে এ দুআটি পড়তেন। হাসান বছরী রহ. তাঁর দেখা সকল সাহাবীদের থেকেই এ দুআটি পড়ার কথা বর্ণনা করেছেন। হযরত উমর রা. ফজরে পড়েছেন বলে এটি কুনূতে নাযেলা হয়েছে, তাহলে তিনি যে বিতরেও পড়েছেন তাতে এটি বিতরের কুনূত হবে না কেন?
গ্রন্থকার – ৩২
গ্রন্থকার বলেন “অতএব বিতরের কুনূত হিসাবে রাসূল (ছাঃ) – এর শিক্ষা দেওয়া দু‘আ পাঠ করতে হবে। … (তরজমা) …রাসূল (ছাঃ) আমাকে কতিপয় বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন সেগুলো আমি বিতর ছালাতে বলি। …।”
পর্যালোচনা
‘আল্লাহুম্মাহ্দিনা ফীমান হাদাইতা …’ দুআটি বিতরের মত ফজরেরও কুনূত:
যে দুআটি গ্রন্থকার শুধু বিতরের কুনূত বলে দাবী করছেন, সেটিই বরং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের কুনূত তথা কুনূতে নাযেলা হিসেবে সাহাবীদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। দেখুন ইমাম বাইহাকী রহ. বর্ণনাটি উল্লেখপূর্বক কত স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন: (فصح بهذا كله أن تعليم هذا الدعاء وقع لقنوت صلاة الصبح وقنوت الوتر) : অর্থাৎ ‘উপরোক্ত আলোচনায় বিশুদ্ধরূপে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, এ দুআটি শিক্ষা দেয়া হয়েছে ফজর ও বিতর উভয় কুনূতের জন্য’। [আস-সুনানুল কুবরা ২/২১০ হা.৩২৬৬]
সুতরাং এ দুআকে শুধু বিতরের দুআ হিসেবে নির্দিষ্ট করে ফেলা ঠিক নয়।
 আহলে হক্ব বাংলা মিডিয়া সার্ভিস Ahle Haq Media
আহলে হক্ব বাংলা মিডিয়া সার্ভিস Ahle Haq Media